কবিতার ক্ষমতা
আমাদের এই যুগটা অর্থাৎ যে-যুগে যুদ্ধ, বিপ্লব এবং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—অনেক কিছুই ঘটেছে বা এখনও অনেক কিছুই ঘটতে চলেছে, এমন একটা সময়কে কবিতার স্বর্ণযুগ বললে বোধকরি বেশি বলা হয় না। এরকম অবস্থা অনেক কবিকেই বোধহয় এর আগে দেখতে হয়নি—বর্তমানের কবিরা যা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন। পৃথিবীর সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ আজ কোনও না কোনও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন এবং সেই সকল প্রতিকূলতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে এখনকার অনেক কবিতায় আর মিছিলে।
আমি যখন আমার প্রথম কবিতার বইটি লিখেছিলাম তখন ভাবতেই পারি নি যে, রাস্তাঘাটে, কলে-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, থিয়েটারে, সভাসমিতিতে কিংবা প্রায় প্রতিটি প্রতিবাদ সভায় আমার কবিতা আমাকেই পাঠ করতে হবে—শোনাতে হবে সাধারণ মানুষজনকে। আমার দেশ চিলের সর্বত্রই ছুটে যেতে হয়েছে আমাকে—আমার দেশবাসীর কাছে আমার কবিতার বীজ ছড়াবার জন্য!
বেগা সেন্ত্রালের একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি। সান্তিয়াগোর বেগা সেন্ত্রাল্ হচ্ছে চিলের সবচেয়ে বড়ো বাজার। সারা পৃথিবীর অনেক কিছুই এই বাজারে কেনা-বেচা হয়। সব সময়েই বাজার সরগরম থাকে। বাজার-শ্রমিকদের বিরাট ইউনিয়নও আছে। বেশিরভাগ শ্রমিকই দরিদ্র। এঁদের পায়ে জুতো জোটে না বললেই চলে, অর্ধভুক্ত অবস্থার কোনও রকমে এঁদের দিন কাটে। এঁদেরই কয়েকজন একটি গাড়ি যোগাড় করে আমার কাছে এলেন, বললেন ওঁদের সঙ্গে যেতে। কোনও কৈফিয়ত বাতিরেকেই গাড়িতে উঠলাম। ‘হৃদয়ে আমার এস্পানিয়া’ কবিতার বইটি আমার পকেটেই ছিল। কিছুদূর যাবার পর সঙ্গীদের মধ্যে একজন বললেন, বেগা সেন্ত্রাল বাজার কর্মচারী সমিতিতে কবিতা পাঠ করে শোনাতে হবে।
নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ভাঙাচোরা এক বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করতেই হাড়-কাঁপানো শীতে আমার সারা শরীর আহত সিম্ফনির মতো কেঁপে উঠলো। ঘরের ভিতরের ভাঙা টেবিল এবং সেই টেবিলের চারপাশে কাঠ আর ভাঙা বেঞ্চিগুলিতে দেখলাম প্রায় জনা পঞ্চাশেক মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমার জন্য, আমার কবিতা শোনার জন্য। এঁদের কারোর গায়েই গোটা একটা জামা দেখতে পেলাম না। দেখলাম কারুর গায়ে রয়েছে আধ-ছেঁড়া পাতলা শার্ট, কেউ-বা জুলাই মাসের চিলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে দিব্যি খালি গায়ে হয়েছেন, কেউ কেউ আবার ছেঁড়া চট গায়ে জড়িয়েছেন। চিলের যা বৈশিষ্ট্য, কয়লার মতো কালো চোখ—সেই সব কালো চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবন্ধ।
আমার বুড়ো লাফের্তের কথা মনে পড়ে গেল। একবার একটি রসায়নাগারের শ্রমিক অফিসে কবিতা পড়তে গিয়ে দেখেছিলেন এমনি কয়েক শো চোখের প্রায় অপলক দৃষ্টি আমার উপরে নিবন্ধ, এমনকি তাঁদের মুখমণ্ডলের পেশিগুলি পর্যন্ত অচঞ্চল। লাফেতে সেদিন আমাকে বলেছিলেন, “দেখ, দূরে থামের পাশে ওই যে দু’জোড়া চোখ দেখা যাচ্ছে—এঁরা মুসলমান। তোমার কবিতা যেন তপ্ত মরুভূমির মতো ওঁদের মনকে স্পর্শ করতে পারে!” কিন্তু আজ! আজ এই অর্ধযুক্ত, অর্ধনগ্ন শ্রমিকদের আমি কোন কবিতা শোনাবো? আমার সংগ্রামী জীবনের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা এখানে আমি করবো? শেষ পর্যন্ত পকেটে আনা আমার কবিতার বইটি বের করে তাদের বললাম – “এই সদ্য সদ্য আমি এস্পানিয়া থেকে ফিরেছি—সেখানে অনেক যুদ্ধ আর অসংখ্য মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। এস্পানিয়ার এই ব্যথাতুর সংগ্রামী মুহূর্তের উপরে আমি যে-কবিতাগুলি লিখেছি তারই কিছু-কিছু আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।” আমার এই কবিতার বইটিতে অনেক কবিতাই আমার নিজের কাছেও দুর্বোধ্য ছিল – কারণ তীব্র ব্যথার মুহূর্তেই বেশিরভাগ কবিতা রচিত। তাই ঠিক করলাম কিছুটা অদল-বদল করে কিছু কবিতা পাঠ করে তাড়াতাড়ি বিদায় নেব।
শুরু করলাম কবিতাপাঠ। সুগম্ভীর নীরবতা ও পলকহীন চোখের দৃষ্টি আমায় যেন হঠাৎ জানিয়ে দিলো আমি ওঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পেরেছি। কবিতার পর কবিতা পড়ার সময় হঠাৎই একসময়ে আমার কবিতার শব্দগুলি আমার নিজেরই কানে আঘাত করতে শুরু করলো। সেদিন মনে হয়েছিল অদৃশ্য এক চুম্বকশক্তির প্রভাবে আমি ও আমার হতভাগ্য শ্রোতার দল কখন যেন একাত্ম হয়ে গেছি।
প্রায় এক ঘণ্টা পরে কবিতাপাঠ শেষ করে যখন বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় চটের থলি গায়ে শ্রমিকটি উঠে এসে আমায় বলেছিলেন, “ধন্যবাদ পাবলো, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কবিতার দ্বারা এমন সম্মোহিত আমরা কখনও হই নি।” বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আরও কয়েকটি কান্নার আওয়াজ আমার কানে এলো। ভেজা চোখের পাতা আর কর্কশ হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পথে নামলাম।
আগুন আর বরফের এই পরীক্ষার শেষে কোনও কবি কি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন? যখনই তিনা মোদোত্তিকে মনে করার চেষ্টা করি তখনই আমার মনে হয়, আমি যেন একআজলা কুয়াশা অতি কষ্টে কুড়িয়ে নিলাম। ও যে কী তা কখনও চিনি নি। দীর্ঘায়ত কালো দু’টি চোখ, মাথায় পশমের মতো চুলগুলি ঘাড়ের কাছে গোল করে বাঁধা। দৃষ্টিটা ছিল ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। দিয়েগো রিবেরা তাঁর এক ম্যুরালে তিনার সেই মনোমুগ্ধকর ভাবটি ফোটাতে গিয়ে উদ্ভিদ আর লতাগুলা দিয়ে তাঁর মাথার মুকুট আর ধানের শিষ দিয়ে বর্শাফলক এঁকেছিলেন।
ইতালিয়ান বিপ্লবী এই যুবতীটি কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন—সেখানকার পর্বতমালা, বন্যপ্রাণী আর পুষ্পরাজির ছবি তুলতে। কিন্তু সে-দেশের সমাজতন্ত্র, মার্ক্সীয় দর্শন, সাম্যবাদ এবং সেখানকার সমাজব্যবস্থা তাঁকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে, তিনি ক্যামেরাটি মস্কো নদীর জলে ফেলে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে সাম্যবাদ প্রচারে মেতে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় মেহিকোয়, তখন সেখানে তিনি পার্টির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একদিন রাত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমায় অত্যন্ত শোকাহত করে।
সময় ১৯৪১ সাল। কার্লোস বাহিনীর কমান্ডেন্ট বিত্তোরিও বিনালি ছিলেন। ভিনা মোদোত্তির স্বামী। তিনা মোদোত্তি রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ট্যাক্সির মধ্যেই মারা যান। তিনি অবশ্য জানতেন যে, তাঁর হৃদযন্ত্রের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়, কিন্তু পাছে এর জন্য তাঁর বিপ্লবী কাজ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয় সেই জন্য কাউকেই তিনি এই রোগের কথা বলেন নি। সব সময়েই সব রকমের কাজ করার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। এস্পানিওল্ গৃহযুদ্ধে তাঁকে আহত বিপ্লবী সেনাদের সেবা করতে দেখেছিলাম।
কুবার বিখ্যাত যুবনেতা বিপ্লবী হুলিও আন্তোনিও মেয়া-র সঙ্গে মেহিকোতে অবস্থানকালে তিনাকে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কুবাতে তখন অত্যাচারী হেরার্দো মাচাদোর শাসন চলছে। তিনি আবানা থেকে কয়েকজন ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠালেন মেহিকোতে—হুলিও আন্তোনিও মেয়াকে খুন করার জন্য। তিনা ও মেয়া এক সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে ফিরছিলেন। দু’জনে হাত ধরাধরি করে যখন হাঁটছিলেন তখন হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে মেয়ার দেহটিকে ঝাঁঝরা করে দিল। দু’জনেই উপুড় হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। তিনার কোলে মেয়ার মৃতদেহ এবং মেয়ার রক্ত তাঁর সর্বাঙ্গে। আততায়ীরা তৎক্ষণাৎ নিখোঁজ। পুলিশের তৎপরতাতেই আততায়ীরা নিরাপদে পালাতে পেরেছিল। তবে মজার কথা এই যে, পুলিশের তরফ থেকে মেয়ার মৃত্যুর জন্য তিনাকেই দায়ী করা হয়েছিল।
দীর্ঘ বারোটি বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তিনার প্রাণশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। এরই ফলস্বরূপ এক রাতে ট্যাক্সির মধ্যে তাঁর প্রাণবায়ু একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল। মেয়ার মৃত্যুর মতোই মেহিকোর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তিনার মৃত্যুকেও কলঙ্কিত করতে কসুর করে নি। সেদিন আমি ও তিনার স্বামী কমান্ডেন্ট কার্লোস তিনার মোমের মতো শরীরটা যখন কফিনে তুলে দিচ্ছিলাম তখন আমরা গভীর শোক ও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। এ সেই শোক যাকে পৃথিবীর কোনও কিছুই কলঙ্কিত করে না, যা শোকাহত মানুষের অস্ফুট চিৎকারকে সিংহনিনাদে ভরিয়ে তোলে।
পরের দিন বুর্জোয়া সব খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অনেক রকমের নোংরামি জুড়ে দিয়ে আদিরসাত্মক পরিভাষায় তিনার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছিল। সস্তা আদিরসাত্মক ভাষায় যা-কিছু লেখা যায় সে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কোনও কাগজে লিখলো : ‘মস্কোর রহস্যময়ী নারীর রহস্যজনক মৃত্যু’। কোনও কাগজে লেখা হলো : ‘মেয়েটি মরলো, কেননা মেয়েটি অনেক কিছু জানতো’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত খবর পড়ে স্থির থাকতে পারলাম না, ঠিক করলাম কার্লোসের এই দুঃসময়ে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। তাই লিখলাম একটি কবিতা—মোদোত্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে-সকল কাগজ কলঙ্ক ছড়াচ্ছে তাদের জন্য। সত্যসহ জোরালো প্রতিবাদপূর্ণ ঐ কবিতাটি কলঙ্ক লেপনকারী কাগজগুলির সম্পাদকদের কাছে পাঠালাম—যদিও জানতাম, আমার ঐ কবিতা কোনও কাগজেই ছাপা হবে না। কিন্তু আশ্চর্য, কবিতাটি পাঠানোর পরদিনই দেখলাম সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম : ‘তিনা মোদোত্তি আজ মৃত’। তিনাকে সমাহিত করার সময়েও এই কবিতা পাঠ করেছিলাম, তাঁর কফিনের ফলকে আজও লেখা রয়েছে কবিতাটি। এরপর মেহিকোর কোনও কাগজেই আর তিনার উপরে কোনও বিরূপ মন্তব্য বের হয়নি।
অনেক বছর আগে লোতায় গিয়েছিলাম সেখানকার কয়েক হাজার শ্রমিকের আমন্ত্রণে—কবিতা শোনাতে। দারিদ্র্য অবহেলা আর অত্যাচারই হচ্ছে লোতার খনি শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী। রাজনীতিকদের গালভর্তি আশ্বাস শুনে-শুনে দারিদ্র্য ও অবিচারের সঙ্গে ঐ সকল শ্রমিক এক সখ্যের সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সামনে সমুদ্র তারপরেই টানেল, সেই দেওয়ালের পাশে অন্ধকারের ভিতর নীরবে কাজ করেন ঐ সকল শ্রমিক একমুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের আশা নিয়ে। সেদিন ভরদুপুরে তাঁরা সবাই জড়ো হলেন আমার কবিতা শোনার জন্য। উঁচু পাটাতনটিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম কয়লা-কালো পোশাক আর খনির কাজের সময় ব্যবহৃত টুপি পরা হাজার কয়েক খনি-শ্রমিক আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছেন আমার কবিতা শোনার জন্য। যে-কবিতাটি পাঠ করবো তার নামটি (নতুন প্রেমগীতি : স্তালিনগ্রাদের উদ্দেশে) জানানো মাত্রই এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো—শুরু হলো অকল্পনীয় এক অনুষ্ঠানপর্ব যা ভুলবার নয়। আমার এবং আমার কবিতাটির নাম শুনেই মাথা থেকে তাঁরা টুপিগুলি খুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কবিতাপাঠ শেষে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, কবিতাটি তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে। কবিতা পাঠের তালে তালে নিঃশব্দ প্রতিজ্ঞায় তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল কয়েক হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওঠা-নামার মাঝে। আমার কবিতা নবজন্ম লাভ করলো। সংগ্রাম ও মুক্তির শপথে সেদিন আমার কবিতার ভবিষ্যৎ রচিত হয়েছিল।
আর-একদিনের আরো একটা ঘটনার কথা জানাই। অবশ্য তখন আমার বয়স অল্প, সবেমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছি এবং যে-কোনও দরিদ্র কিংবা অর্ধাহারী কবির মতোই তখন আমার চেহারা—ওজনহীন কোনও পাখির পালকের মতোই বলা চলে। অন্যান্য কবির মতোই কালো রঙের টুপি পরতাম। ক্রেপুস্কলারিও নামক আমার কবিতার বইটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সস্তা দরের এক হোটেলে গেলাম আনন্দ করতে। সেই সময়ে এই জাতীয় হোটেল বা নৈশ-আড্ডায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য ছিল খুব। এদের মধ্যে প্রায়ই গোলামাল লাগতো এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো নিরীহ মানুষ আর দরিদ্র শ্রেণীর নাচিয়ে মেয়েরা।
আমরা সবাই বসেছি। নাচ-গান শুরু হয়েছে। এমন সময় দু’টি গুণ্ডা সেখানে নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিল। ভীত আতঙ্কিত গাইয়ে নাচিয়েরা হোটেলটির পিছনে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু সহ্য হলো না আমার, উঠে গুণ্ডা দু’টির সামনে গিয়ে শারীরিক অক্ষমতাকে গলার আওয়াজে চাপা দিতে চিৎকার করে বললাম, “অসভ্য নোংরা বাঁদরের দল—এখানে মানুষ এসেছে আনন্দ করতে, তোমাদের বাঁদরামি দেখতে নয়।”
আমার চিৎকারে যে ওরা শুধু অবাক হয়েছিল তাই নয়, ওদের দেখে মনে হচ্ছিল—ওরা যেন এটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। ওদের মধ্যে বেঁটেখাটো বক্সিং জানা লোকটি আমার দিকে এগিয়ে আসতেই সজোরে একটা ঘুসি মারলাম তাকে, এর ফলে সে মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধীরা তাকে তুলে আরও কিছু উত্তমমধ্যম লাগিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।
এই ঘটনার পর অন্য সবাই খুব হৈ-চৈ করে আমাকে আর আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানালেন এবং মদ খাওয়াতে চাইলেন। হোটেল-মধ্যস্থ অন্য গুণ্ডাটি আমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে চাইল, কিন্তু তাকে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললাম। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।
আনন্দোৎসব শেষে ঘরে ফেরার পথে একটা সরু গলির মুখে এসে স্তম্ভিত হলাম আমরা। দেখলাম হোটেল থেকে বিতাড়িত দ্বিতীয় বদমাশটা তার দৈত্যের মতো চেহারা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লোকটা আমাকে বললো, “আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।” বলেই সে একটা ধাক্কা দিয়ে রাস্তার এক কোণে আমাকে নিয়ে যেতেই বন্ধুরা ভয়ে খরগোসের মতো কাঁপতে শুরু করলো। আমিও ভয়ে কাঠ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম—আঘাত করার মতো যদি কিছু একটা হাতের কাছে পাই, কিন্তু তেমন কিছুই পেলাম না। প্রতিশোধের সম্মুখীন হয়ে আমি সেদিন সব দৃঢ়তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। “আসুন একটু আলাপ করি।” লোকটা হুঙ্কার দিলো।
ভয় পেয়েছি ভাবটা দেখানো ঠিক হবে না। তাই বেশ জোরে একটা ধাক্কা মারলাম তাকে, কিন্তু সেই বিশাল দেহের বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারলাম না। মনে হলো আমার সামনে যেন ইটের প্রকাণ্ড দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সময়ে সে তার মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে আমার দিকে তাকালো, দেখলাম তার মুখ থেকে বন্যভাবটা একেবারে উবে গেছে। বেশ নম্রতার সঙ্গেই সে প্রশ্ন করলো, “আপনি কি পাবলো নেরুদা?” এরপর আমার উত্তর শুনে লজ্জায় নত হয়ে সে বললো, “ছিঃ ছিঃ, কী নীচ আমি। আমি একজন অপরাধী, আপনাকে অপমান করেছি। ক্ষমা করুন আমাকে। আপনি বিশ্বাস করুন নেরুদা — যে মেয়েটিকে আমি ভালবাসি সে আপনার ভীষণ ভক্ত। আমরা দু’জনে আপনার কবিতা পড়েই আপনাকে ভালবাসতে শিখেছি। আর আমি সেই মেয়েটির কাছে যে-ভালবাসা পেয়েছি সে কেবল আপনার কবিতার জন্যই, আপনার কবিতাই আমাদের দু’জনকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।” এই পর্যন্ত বলেই সে বুক পকেট থেকে তার প্রিয়তমার একখানি ছবি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, “আপনি এই ছবিটা একবার স্পর্শ করুন, আমি তাকে এটি দিয়ে বলবো পাবলো নেরুদার হাতের স্পর্শ আছে এই ছবিতে।”
ছবিটি স্পর্শ করে তার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি শুরু করলো :
তোমার হৃদয়ের গভীরে, নতজানু
এক বিষণ্ণ বালক
যে চেয়ে থাকে
আমাদের দিকে—
ইতিমধ্যে বন্ধুরা অকুস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই কবিতা আবৃত্তির সময়ে তাঁরা লোকজন নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসে হতবাক হলেন। এরপর আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। কিন্তু লোকটি তখনও সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আপন মনে আবৃত্তি করে চললো :
যে জীবন তার ধমনীতে
প্রবাহিত, প্রদীপ্ত
ওকে হত্যা করার আগে
আমার বাহু দুটিকে
বিচ্ছিন্ন কর
আমার শরীর থেকে—
উৎস : অনুস্মৃতি, পাবলো নেরুদা, মর্মানুবাদ ভবানীপ্রসাদ দত্ত, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮১
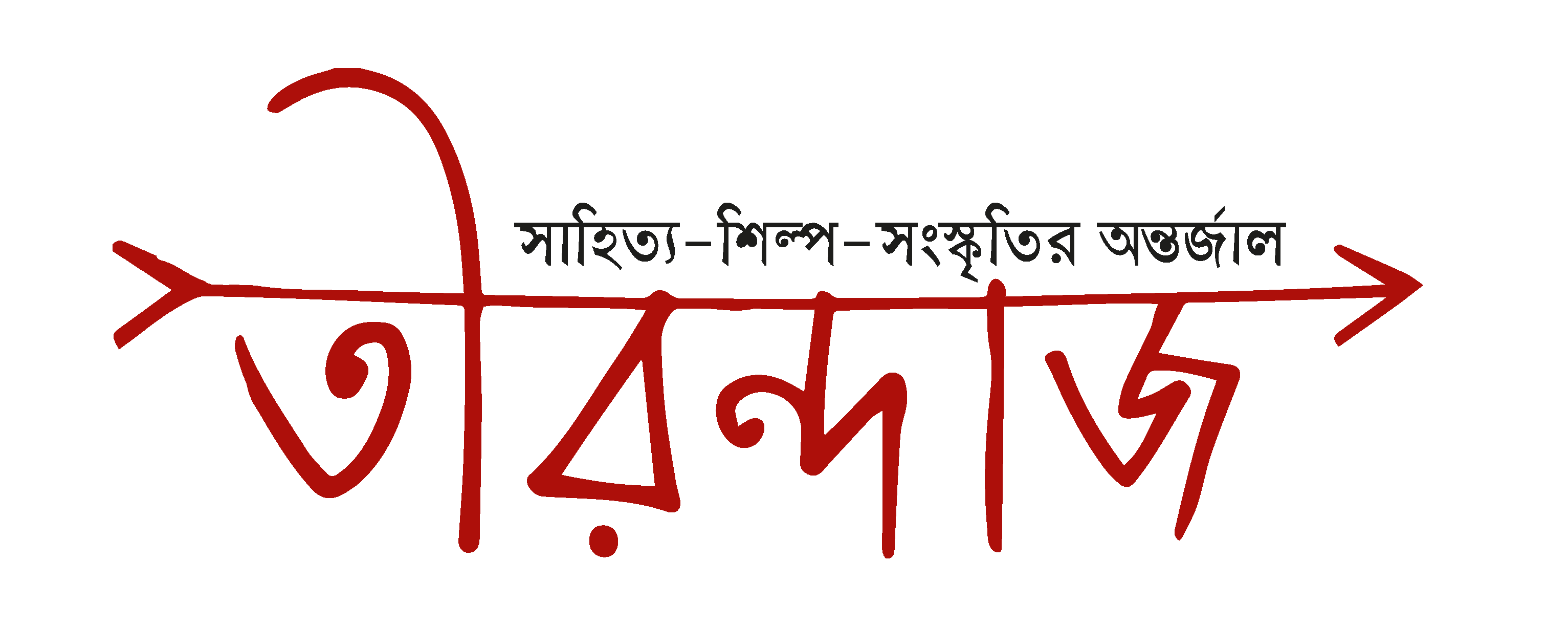






Leave feedback about this