লাল ফুলগুলো একটু নেতিয়ে পড়েছে। এই ফুলগুলোর আরও একটু পরিচর্যা করা দরকার। আসলে যতটা সময় এই বাগানটার জন্য দেওয়া উচিত ততটা সময় সুফলবাবু দিতে পারছেন না। অথচ এই বাগানটাই তো ওঁর জীবনের সবকিছু। লাল ফুলগুলোর গায়ে খুব আলতো করে আঙুল বোলাতে বোলাতে উনি বলেন, চিন্তা করিস না। তোদের আবার এক দু-দিনেই আমি তরতাজা করে দেব। হাওয়ায় মাথা দোলাবি। চিন্তা করিস না।
নীল ফুলগুলো কিন্তু দিব্যি হাসিখুশি রয়েছে। রোদের এত তেজ। তাও ওরা এতটুকুও নেতিয়ে পড়েনি। কিন্তু সুফল বাবু তো চান লাল, নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনি সব রঙের ফুলগুলোই সমানভাবে মাথা দোলাক। লাল ফুলের গাছটার যত্ন-আত্তি আরেকটু বেশিই করতে হবে। আসলে গত কয়েক দিন ধরে উনি দিনে পাঁচ ছটার বেশি মিথ্যে কথা বলতে পারছেন না। এই সংখ্যাটা ওকে বাড়াতেই হবে। অন্তত দশটা মিথ্যে কথা প্রতিদিন ওকে বলতেই হবে। না হলে লাল গাছটার এই নেতিয়ে পড়া দশা কাটবে না। যত বেশি মিথ্যে কথা বলা হবে তত বেশি কার্যকর হবে মিথ্যে। তত বেশি চনমনে হবে ফুলগুলো। আর সুফলবাবু দেখেছেন যে, গরিব মানুষদের মিথ্যে বেশি বললে চনমনে থাকে লাল ফুলগুলো। ওঁকে খুঁজে খুঁজে গরিব মানুষদের মিথ্যে বলতে হবে একটু বেশি।
একটা ট্যাক্সি জোরে হর্ন বাজাচ্ছে। ওই পাশ থেকে আসলে একটা ভ্যান কাগজ চাপিয়ে ঢুকে পড়েছে ছোটো গলিটার মধ্যে। ভ্যানটা যাতে আর না এগোয় সেজন্যই ট্যাক্সিটা হর্ন বাজাচ্ছে। সুফলবাবু জানেন ভ্যানওলা এই হর্নের পরোয়াই করবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজস্ট্রিটের এই ছোট্ট গলিটায় ভয়ংকর জ্যাম লেগে যাবে। একজন মানুষ চলাচলের পথটুকুও আর থাকবে না। এক্ষুনি ওঁকে এই গলিটা পেরিয়ে ওই পাশে চলে যেতে হবে অটো ধরবার জন্য। তাই উনি লাল ফুলগুলোর গায়ে আঙুল বোলানো বন্ধ করে টুক করে রাস্তায় নেমে এলেন। নেমেই মুখোমুখি পড়লেন সুদীপবাবুর। সুদীপবাবু ওর সহকর্মী। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো কখন বেরিয়েছেন। এতক্ষণ এখানে কী করছিলেন?
সুফলবাবু বললেন, এই একটু কাজ ছিল।
এটা মিথ্যে না। এই বাগানটার দেখভাল করা তো ওঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই সুদীপবাবুকে সত্যি কথাই বলা হল। মিথ্যে বললেও অবশ্য অসুবিধে কিছু ছিল না। কেননা কোনো মানুষের পক্ষেই ওঁকে এই বাগানটা থেকে রাস্তায় নেমে আসতে দেখা সম্ভব নয়। জনবহুল কলেজ স্ট্রিটের ভেতরে মিথ্যেফুল গাছের যে এরকম একটি বাগান আছে কেউ জানেই না। উনি জানতে দিতে চানও না। এই বাগানে যে লাল, নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনি রঙের মিথ্যেফুল ফোটে সে তো সুফল বাবুর জন্যই। ওঁরই যত্ন-আত্তিতে। সত্যি বলতে কি, মিথ্যেফুলের কথা হয়তো কেউ বিশ্বাসই করবে না। কাজেই লোকজনকে বলেই বা কী লাভ?
সুদীপবাবু বললেন, কখন বেরিয়েছেন! কী এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ?
ওঁর কথার উত্তর না-দিয়েই সুফলবাবু হাঁটতে লাগলেন। জ্যাম লাগতে শুরু করেছে। ট্যাক্সি আর ভ্যান মুখোমুখি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ কেন একটা পিঁপড়েও আর এই গলি থেকে বেরোতে পারবে না।
২
ভাস্কর কিছুতেই মিমিকে ভুলতে পারছে না। ভোলা সম্ভবও নয়। ষোলো বছরের সম্পর্ক এক মুহূর্তেই তো মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। তবে ও কিছুদিন ধরেই পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে, মিমি আর ওকে চায় না। প্রথমে ওকে না-জানিয়েই মিমি বাড়ি পালটে নিয়েছিল। তখনও অবশ্য ফোনে যোগাযোগটুকু ছিল। এখন আর সেই যোগাযোগটুকুও নেই। ফোনের সিমও পালটে নিয়েছে মিমি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে-স্কুলে মিমি পড়ায় সেই স্কুলের পাশের স্কুলটাতেই পড়ায় ভাস্করের পাড়ার বন্ধু পরিতোষ। পরিতোষকে একদিন ভাস্কর খুলে বলেছিল সব কথা। শুনে পরিতোষ চমকে উঠেছিল। বিশ্বাসই করতে চাইছিল না যে, ভাস্করের মতো একজন মুখচোরা, অন্তর্মুখী মানুষ প্রেম করতে পারে, তাও আবার ষোলো বছর ধরে এবং সেটাও মিমির মতো কোনো একজনের সঙ্গে। সেই মিমি যার জন্য নাকি ওই অঞ্চলের অবিবাহিত অন্য মাস্টারমশাই, কলেজের অধ্যাপক তো বটেই এমনকি মিমিদের স্কুলের ছাত্ররাও পাগল! রূপসি, সুন্দরী, বনেদি ঘরের মিমি ভাস্করের মতো নিতান্তই ছাপোষা একটি ছেলের সঙ্গে যে ষোলো বছর ধরে একটি সম্পর্কে ছিল সেটাই নাকি অনেক। পরিতোষ স্ট্রেট ভাস্করকে বলেছিল, শোন, বাড়ি পালটে নিয়েছে, সিম পালটে নিয়েছে, তার মানে বার্তা খুব পরিষ্কার। তোর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে চাইছে না। তুই ওকে ভুলে যা। চাকরি তো কোনোদিন পাবি বলে মনে হয় না। যে-কটা টিউশন পড়াস, সেগুলো পড়ানোতেই মন দে। বাকি সময়টুকু নাটক-ফাটক না-করে বাড়িতে থাক, মাসিমাকে সময় দে।
ঠান্ডা মাথায় ভাবলে পরিতোষ ভুল কিছু বলেনি। মিমি যে ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবে না তা ভাস্কর বেশ বুঝতে পারছে বেশ কিছুদিন ধরেই। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই মিমি আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছিল। কিন্তু, মিমির এই বদলটা ও ধরতেই পারেনি। মনে আছে যেদিন স্কুলে মিমি জয়েন করেছিল সেদিন অ্যাটেন্ডাস রেজিস্টারে সই করে সেই সইয়ের ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে ভাস্করকে পাঠিয়েছিল। সেই মিমি গত কয়েক বছরের মধ্যে কেমন বদলে গেল। গত দু-বছর মিমি ওর সঙ্গে দেখা প্রায় করতই না। সারা দিনে দশবার ফোন করলে একবার ফোন ধরত। তারপর তো একদিন ওকে হোয়াটসঅ্যাপে পরিষ্কার লিখেই পাঠিয়েছিল, তুমি কিন্তু সারাদিনে এতবার ফোন করে আমাকে বিরক্ত করছ। আমি কিন্তু ব্যবস্থা নেব।
মেসেজটা পড়ে ভাস্কর বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, মিমি এমনটা লিখতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, মিমিকে ও একটু বেশিই বিরক্ত করে ফেলছিল। এমনকি স্কুলে থাকার সময়ও ও দিনের মধ্যে দশ-বারো বার ফোন করে ফেলত মিমিকে। কাজেই মিমির রেগে যাওয়ার কারণ ছিল। তাই ওইরকম কড়া কথা মিমি লেখার পরেও ভাস্কর বুঝতে পারেনি যে, মিমি সত্যি সত্যিই ভাস্করকে ওর জীবন থেকে মুছে ফেলেছে। ওর বরং মনে হয়েছিল যে, ও তো সত্যি সত্যিই মিমিকে বেশি বিরক্ত করে ফেলছে। আসলে সকালে দু-ঘণ্টা আর সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা টিউশন পড়ানো ছাড়া তো ভাস্করের আর তেমন কোনো কাজই নেই। তাও সপ্তাহের প্রতিদিন ও পড়ায় না। আর টিউশন আছেই এখন মোটে তিনটে। সবসময় টিউশন থাকেও না। নাটকের রিহার্সালও তো আর সারা বছর হয় না। ওদের ছোটো দল। বছরে একটি নাটক নামায়। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সেই নাটক নিয়ে কিছুটা ব্যস্ততা থাকে। নানা নাট্যউৎসবে কল শো থাকে। বাকি সময়টা তো সন্ধেবেলা পড়ানোর পর ওর আর কোনো কাজই থাকে না। তাই হয়তো বাধ্য হয়ে ও মিমিকে বারবার ফোন করে ফেলত। মিমিও বিরক্ত হত। ভাস্কর ভেবেছিল এই বিরক্তি স্বাভাবিক। তাই মিমি ওই মেসেজ দেওয়ার পরে স্কুল চলাকালীন ওকে আর ফোন করত না। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করত একটা-দুটো। সেসবের কোনো উত্তর অবশ্য মিমি দিত না। একসময় ওকে হোয়াটসঅ্যাপে ব্লকই করে দিল। তখন ফোন করলে আর ফোনও ধরত না। তারপরে ও বাড়ি পালটাল। শেষে সিমও পালটাল। এখন আর কোনোই যোগাযোগ নেই।
দু-দিন আগেই পরিতোষ ওকে একটা নতুন খবর দিয়েছে। মিমি নাকি এখন যে-ফ্ল্যাটে থাকে তার উলটো দিকের ফ্ল্যাটে থাকে পরিতোষের কলিগ ভূগোলের শিক্ষক ভীষ্ম ব্যানার্জি। এই ছেলেটির সঙ্গেই নাকি মিমির সম্পর্ক হয়েছে। গোটা চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়েই নাকি ছড়িয়ে গেছে এই খবর। ছড়িয়েছে এইজন্যই আরও যে, ছেলেটার বয়স বড়জোর তিরিশ। মানে মিমির চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোটো। বয়সে ছোটো একটি ছেলের সঙ্গে একজন স্কুলশিক্ষিকা সম্পর্কে জড়ালে তা তো মুখোরোচক খবর হবেই। পরিতোষ ওকে বলেছে যে, ভীষ্মর হাবভাব দেখে ও নাকি নিশ্চিত হয়েছে যে, খবরটা সত্যি। বলেছে, তুই মিমিকে ভুলে যা।
কিন্তু ভাস্কর কিছুতেই মিমিকে ভুলতে পারছে না।
৩
সজল দত্ত সুফলবাবুকে বললেন, বাপি কাল আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল।
সুফলবাবু গৌরববাবুর কিউবিকলের বাইরে চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন। ওঁর কথা শুনে নড়েচড়ে উঠে বললেন, করবেই তো। কতদিনের পরিচয়! কেমন আছে বাপি?
সজল দত্ত বললেন, ভালো।
সজল দত্ত সুফল বাবুকে প্রথম দেখেছিলেন গত বছর বইমেলায় নক্ষত্র প্রকাশনীর স্টলে। রোগা, চিমসে চেহারা। মাথা-জোড়া টাক। মলিন, অনুজ্জ্বল জামাকাপড় পরে চারশো স্কোয়ার ফিট স্টলের একটি দিকের বইপত্র সামলাচ্ছিলেন। নক্ষত্র প্রকাশনীর নাটকের বেশ কিছু বই আছে। সেই বইগুলো কিনতেই সেদিন সজল দত্ত নক্ষত্র প্রকাশনীর স্টলে গিয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল মাত্র দু-টি বই কেনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দশটি বই কিনে স্টল ছেড়েছিলেন। সেটাও ওই সুফল বাবুর জন্যই।
সজল দত্ত আঙুল দেখিয়ে সুফল বাবুকে বলেছিলেন, আমাকে ওই অশোক মুখোপাধ্যায়ের নাটকসমগ্রটা দিন তো।
সেই বইটা ওঁর হাতে তুলে দিয়েই সুফলবাবু ওঁকে বলেছিলেন, নাটকের বই কিনছেন, বা বা! দাদা, নাটক করেন নাকি?
সজল দত্ত বলেছিলেন, হ্যাঁ ছোটো একটা নাটকের দল চালাই।
সুফল বাবু বলেছিলেন, বাহ বাহ। আমার মেজ পিসেমশাইও তো নাটকের দল চালাতেন।
সজল দত্ত বলেছিলেন, কী নাম আপনার মেজ পিসেমশাইয়ের?
এই প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে সুফল বাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি থাকেন কোথায় কলকাতায়?
সজল দত্ত বলেছিলেন, বাঁশদ্রোণীতে।
–বাঁশদ্রোণীর কোথায়?
–ব্রহ্মপুরে। কদমতলা চেনেন?
–কেন চিনব না? ওই কদম তলায় বাপি থাকে। কতবার গিয়েছি ওর বাড়িতে!
–ওহ, বাপিকে আপনি চেনেন? গেছেন ওর বাড়িতে?
–কতবার গেছি। ওই তো কদমতলা থেকে বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলেই –
–না না, বাঁ দিক নয়, ওটা ডান দিক –
–ঠিক ঠিক, ডান দিক। আসলে বুঝলেন, গুলিয়ে গেছে। এত বছর আগের ঘটনা তো! শুনে খুব ভালো লাগলো যে, আপনি কদম তলায় থাকেন।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সুফলবাবুর সঙ্গে প্রায় বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল সজল দত্তর। এত কথা বলছিলেন সুফলবাবু যে, সজল দত্ত ভুলেও গিয়েছিলেন সুফলবাবুর পিসেমশায়ের নাম জিজ্ঞেস করার কথা। কথা বলতে বলতেই আরও একাধিক বই সজল দত্তর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুফলবাবু। শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই সুফলবাবুকে নিয়ে স্টলের বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, চলুন, আপনি বাপির পাড়ার লোক, দুজনে মিলে একটু চা খাওয়া যাক।
চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সজল দত্ত চায়ের দামটা দিয়ে দিয়েছিলেন। চা হাতে নিয়ে সুফলবাবু বলেছিলেন, বিস্কুট ছাড়া কি চা খাওয়া যায় বলুন? চলুন দুটো করে বিস্কুট নিই।
বিস্কুটের দামও সজল বাবুই দিয়েছিলেন। চায়ের দাম দিলে কি আর বিস্কুটের দাম না-দিয়ে থাকা যায়?
সুফল বাবুর কারণেই সেদিনই সজল দত্তর পরিচয় হয়েছিল নক্ষত্র প্রকাশনীর কর্ণধার গৌরব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হাসিখুশি, ছোটোখাটো চেহারার গৌরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে সজল দত্তর বেশি সময় খরচ হয়নি। পেশায় সরকারি কেরানি সজল দত্তর নাটক করা আর নাটক সংক্রান্ত বই কেনা নেশা। নিজের দলের জন্য নাটক লিখেছেনও প্রায় গোটা পনেরো। গৌরব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব একটু গাঢ় হতেই সজল দত্তর মনে হয় এই নাটকগুলো নিয়ে তো ওর নিজেরও একটা বই হতে পারে। সেই প্রস্তাব সজল দিয়েছিলেন গৌরবকে। গৌরব বলেছিলেন, বই হতেই পারে। তবে আগে আপনি অন্তত কয়েকটা নাটক আমাকে পড়ান, না হলে বুঝব কী করে কেমন নাটক লেখেন আপনি? হাতে-লেখা পাঁচটা নাটকের পাণ্ডুলিপি গৌরবকে পড়িয়েছিলেন সজল দত্ত। সেগুলো পড়ে গৌরব জানান যে, বই হবে তবে এই বই ছাপানোর খরচের পুরোটাই দিতে হবে সজল দত্তকে। রাজি হয়ে যান সজল দত্ত। ডিএ-টিএ একেবারেই নেই এ রাজ্যে। ওঁর মাইনেও যে খুব একটা বেশি তা নয়। তবে রোজগারের একটা বড়ো অংশ তো চিরকাল উনি নাটকের দলের জন্যই খরচা করেছেন। এবার না হয় কিছুটা টাকা নিজের বই প্রকাশের জন্যই খরচা করলেন। বইয়ের কাজ যতই এগিয়েছে ততই গৌরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে সজল দত্তর। গৌরব এখন আর কেবল ওঁর প্রকাশক নন, বন্ধুই।
গৌরবের কাছ থেকেই সুফলবাবুর সম্পর্কে নানা কিছু ধীরে ধীরে জেনেছেন সজল দত্ত। গৌরব বলেছেন যে, সুফলবাবু এক বিচিত্র মানুষ। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উনি নাকি একজন অ্যাসেট। বিশেষ করে একজন প্রকাশকের কাছে তো বটেই। দুর্দান্ত কথা বলতে পারেন। যে কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিতে ওর এক মিনিট লাগে। গৌরব ওকে বলেছেন যে, সুফলবাবু অনবরত মিথ্যে কথা বলতে থাকেন। এই যেমন সজল দত্তকে যে বলেছিলেন কদমতলায় বাপির বাড়িতে উনি মাঝে মাঝে যেতেন সেটা সম্ভবত একেবারেই মিথ্যে কথা। যে কোনো ক্রেতাকে দ্রুত বন্ধু বানিয়ে নিতে সুফলবাবুর জুড়ি মেলা ভার। প্রায় সকলকেই তিনি বলেন যে, কোনো একটা সময় তাঁর পাড়ার কোনো একজন মানুষের বাড়ির পাশেই থাকতেন বা সেই বাড়িতে যেতেন। ওঁর চেনা পরিচিত চরিত্রগুলোর নাম দিয়ে দেন ‘বাপি’, ‘খোকা’ বা এই ধরনের একটা কিছু যা দশটা হিন্দু বাঙালি বাড়ির মধ্যে অন্তত তিন-চারটেতে পাওয়া যাবেই। এভাবেই সুফলবাবুর কাটোয়া-কালনা থেকে ঘাটশিলা-তমলুক এমনকি কোচবিহারেও মিথ্যে সব বাড়ি আছে, আত্মীয় আছে। গৌরব একথাও বলেছেন যে, সুফল বাবু যে আসলে কোথায় থাকেন তা কেউ জানে না। পেশার তাগিদেই কলকাতার বাইরেও নানা বইমেলায় অংশ নিতে গৌরববাবুকে যেতে হয়। অবধারিতভাবে গৌরববাবুর সঙ্গী হন সুফলবাবু। সেইসব জায়গা থেকে ফেরার সময় কোনো কোনো দিন ওঁকে নামানো হয় এয়ারপোর্ট গেটের সামনে, কোনো কোনো দিন লেকটাউনে, কোনো কোনো দিন আবার শ্যামবাজারে। এই সব জায়গাতেই নাকি ওঁর বাড়ি আছে। কলকাতা শহরে সুফলবাবুর আসল বাড়িটা যে কোথায় তা ওঁরা কেউ জানেন না। বইমেলার পরে এমনকি পাঁচ মাস উনি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। ফোন করলে পাওয়া যেত না। সারাক্ষণ সুইচড অফ। এর আগেও নাকি উনি এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন একবার। সেবারও ওঁর টিকিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এবার অবশ্য ছ-মাস পরে উনি ফিরে এসেছিলেন। গৌরব ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি এভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন কোথায়? সুফল বাবু বলেছিলেন, এই একটু ওই দিকে গেছিলাম আর কী। ‘ওই দিক’টা যে কোন দিক সেটা আজ পর্যন্ত গৌরববাবুকে উনি বলেননি। গৌরবের সামনেই আবার ওদের প্রকাশনীতে নিয়মিত বই কিনতে-আসা একজন ক্রেতাকে বলেছিলেন যে, উনি ছ-মাস ছিলেন না তার কারণ বউ আর শাশুড়িকে নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রের ঢেউয়ে ওর বউ নাকি ভেসে যায়। শাশুড়িকে অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে পুরী থেকে নানা জায়গা ঘুরে, চিকিৎসা করিয়ে তবে ছ-মাস পরে ফিরেছেন। গৌরব সজল দত্তকে বলেছিলেন যে, এগুলো সবই মিথ্যে কথা। উনি যে কোথায় গেছিলেন তা কেউ জানে না। গৌরব আরও বলেছিলেন যে, যেভাবে সজল দত্তর টাকায় প্রথম আলাপেই সুফলবাবু চা-বিস্কুট খেয়েছিলেন, সেভাবে নাকি প্রায় প্রতিদিনই কারও না কারও টাকায় উনি চা-বিস্কুট থেকে ডিম টোস্ট সবই খেয়ে থাকেন। পকেটে নাকি একবার মাত্র তিরিশ টাকা সম্বল করে কাশ্মীর থেকে ঘুরে এসেছিলেন। অভিনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী প্রকাশ পেয়েছিল নক্ষত্র প্রকাশনী থেকে। সেই বইয়ের প্রুফ দিতে গিয়ে উনি সুদীপবাবুকে দিয়ে ওঁর মলিনা জামা কাচিয়ে, ইস্ত্রি করিয়ে তারপর ওঁর বাড়িতে খেয়ে, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে সন্ধেবেলায় অফিসে ফিরেছিলেন। সুফলবাবু পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। গৌরব এমনটাও ইঙ্গিত করছিলেন যে, হতে পারে যে, উনি আসলে পুলিশের চর। তাই প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। শুনে চমকে উঠেছিলেন সজল দত্ত।
আজ সজল দত্ত নক্ষত্র প্রকাশনীতে এসেছেন অবশ্য নিজের জন্য নয়। এসেছেন ভাস্করের জন্য। ভাস্কর ওর নাটকের দলের একজন পুরোনো সদস্য। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়স হবে। এখনও বেকার। বাংলায় এমএ পাস করেছে কিন্তু বেচারি চাকরি জোটাতে পারেনি। বেশ কয়েকবার এসএসসি দিয়েছে কিন্তু চাকরি পায়নি। আর এখন তো বোঝাই যাচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরি কীভাবে প্রায় নিলাম করেই এ রাজ্যে বিক্রি করা হয়েছে! ভাস্করের মতো ছেলেরা চাকরি পাবে কী করে! ক-টা টিউশন সম্বল করেই ভাস্করের চলে। ওর বাবা সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মারা গেছেন অনেকদিন আগে। মা সামান্য ফ্যামিলি পেনশন পান। বাজারের যা অবস্থা তাতে ওইটুকু টাকা আর দু-তিনটে টিউশন পড়িয়ে দু-জন মানুষেরও খাবার জোগাড় করা এখন মুশকিল। নতুন নাটকের রিহার্সাল শুরু করেছেন সজল দত্ত। ক-দিন ধরেই দেখছেন রিহার্সালে এসে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে থাকছে ভাস্কর। এমনিতে অবশ্য ভাস্কর খুবই কম কথা বলে। অবশ্য রিহার্সালে খুব বেশি কথা বলার প্রয়োজনও পড়ে না ওর। ও অভিনেতা নয়। মঞ্চ বানায়। অদ্ভুত ওর নিষ্ঠা আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা। সব নাটকের দলেই এইরকম কয়েকজন ছেলেপুলে থাকে। মঞ্চের ওপর এদের দেখা যায় না। কিন্তু এরা না-থাকলে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা অসম্ভব। প্রায় পনেরো বছর ধরে ওর নাটকের দলের সঙ্গে ভাস্কর যুক্ত। কোনোদিন অভিনয় করার কথা মুখ ফুটে বলেনি। শুধু যত্ন করে স্টেজ বানিয়েই গেছে। ওই কাজেই ওর আনন্দ। তবে সজল দত্ত খেয়াল করেছেন যে, এই ক-দিন যেটুকু কথা আগে ভাস্কর বলত সেটুকুও আর বলছে না। একদিন সন্ধেবেলা ভাস্করকে তাই রিহার্সালের পরে একটু থেকে যেতে বলেন সজল দত্ত। ওকে জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে। জীবনে প্রথম ভাস্কর সজল দত্তকে জানায় যে, ওর যে কোনো ধরনের একটা কাজ দরকার। হাজার পাঁচেক টাকার মাইনের চাকরি হলেও হবে। তিনটে টিউশন করে ও তিন হাজার টাকা পায়। টিউশন পড়ায় সকালে আর সন্ধেবেলায়। বাকি সারাদিনটা ও ফাঁকা। কাজেই যে কোনো একটা কাজ পেলে ও সেই কাজ করতে পারবে। সজলকে নক্ষত্র প্রকাশনীতে একটি চাকরি দেওয়া যায় কি না সেই বিষয়ে তদবির করতেই আজ সজল দত্ত গৌরববাবুর কাছে এসেছেন। আসলে বেশ কিছুদিন ধরেই গৌরব ওকে বলছিলেন যে, ওঁর প্রকাশনী যেরকম ভাবে বাড়ছে তাতে ওঁর একজন ঠান্ডা মাথার, শান্ত ম্যানেজার চাই যিনি মোটামুটিভাবে ওঁর প্রকাশনীর অনেকখানি কাজ দেখাশোনা করতে পারবেন কেননা গৌরববাবুর পক্ষে সব কাজ দেখাশোনা করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সজল দত্তকে গৌরব বাবু বলেছেন যে, লোকটিকে হতে হবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং মাইনে আট হাজার টাকার বেশি দিতে পারবেন না। এই কাজটার জন্য সজল দত্তর মনে হয়েছে সমস্ত দিক থেকেই ভাস্কর একেবারে আদর্শ। বাংলায় এমএ পাস একটি ছেলে। পড়ার নেশা আছে। বইপত্রের খবরাখবর রাখে। বেশি কথা বলে না এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত। তাই সজল দত্ত আজ এসেছেন গৌরববাবুকে ভাস্করের কথা বলবেন বলে। ঢোকার মুখেই সুফলবাবুর সঙ্গে দেখা। সুফলবাবুর সঙ্গে এখন সজল দত্ত তালে তাল মিলিয়ে মিথ্যে কথা বলেন। যেমন ওঁদের পাড়ার বাপিকে সুফলবাবু চেনেনই না এটা বুঝে যাবার পরেও সুফল বাবুকে বললেন যে, বাপি ওর খবর নিচ্ছিল। একেবারেই মিথ্যে কথা। কিন্তু সুফল বাবুর সঙ্গে তালে তাল মেলাতে এখন সজল দত্তর ভালোই লাগে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেন একটা অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যান, যে-পৃথিবীটা নেই, কিন্তু থাকলে মন্দ হত না।
গৌরববাবুকে ভাস্করের কথা বলাতে উনি সজল দত্তকে বললেন, ঠিক আছে ছেলেটিকে একদিন নিয়ে আসুন। আমি কথা বলে দেখি। ভালো লাগলে অবশ্যই কাজে নিয়ে নেব। আমি তো একজন বিশ্বস্ত, কর্মঠ মানুষ খুঁজছি।
সজল দত্তর মনে হল যে, ভাস্করের এই চাকরিটা হয়ে যাবে। ও তো চাইছিল পাঁচ হাজার টাকার চাকরি। কিন্তু গৌরববাবু তো বলেইছেন যে, উনি আট হাজার টাকা দেবেন।
৪
কাজের জায়গাটা ভাস্করের বেশ পছন্দই হয়েছে। জীবনের প্রথম চাকরি। প্রথম যেদিন সজল দত্তর সঙ্গে ও গৌরবদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিনই ওর মনে হয়েছিল যে, এই কাজটা ওর ভালোই লাগবে। বইপত্রের সঙ্গে থাকার কাজ তো। বাড়িতেও তো ও বইপত্রের সঙ্গেই থাকে। ভাস্করের বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মারা যান। বাবার চাকরিটা ভাস্কর পায়নি। বাবা যখন মারা যায় তখন ভাস্কর গ্র্যাজুয়েশন করছে। চাকরি পাওয়ার জন্য ও অবশ্য পড়াশোনা ছেড়ে দিতেও রাজি হয়েছিল। কিন্তু তখন বাম-জমানা। এসএসসির মাধ্যমে চাকরি হত। স্কুলশিক্ষা দপ্তরে অ্যাপ্লাই করেও মৃত বাবার চাকরিটা ও পায়নি। এমনকি মায়ের ফ্যামিলি পেনশন শুরু হতেও বেশ দেরি হয়েছিল। বাবা অকালে মারা যাওয়ায় মায়ের ফ্যামিলি পেনশনটা হয়ওনি খুব বেশি। এখনও পেনশনের টাকা বিরাট কিছু নয়। বেশ কষ্ট করেই ওদের চালাতে হয়। তবুও ভাস্কর কিছু কিছু বই কেনে। আর বাবা তো প্রায় একটা লাইব্রেরিই বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বাবার কেনা সমস্ত বই আজও ওর পড়া শেষ হয়নি। বেশ কয়েকটা বই এমনকি পোকায় কেটেছে। ও মাঝে মাঝে বইগুলো বের করে রোদ্দুরে দেয় তবুও বইগুলোকে বাঁচাতে পারে না। কষ্টেসৃষ্টে ওদের কোনওরকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এবার একটা মুশকিল হয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার সময় কাঁকুড়গাছির যে-ভাড়াবাড়িতে তখন ওরা থাকত এখনও সেই বাড়িতেই থাকে। এত বছরে ভাড়াও যে খুব একটা বেড়েছে তা নয়। কিন্তু এবার ভাড়া বাড়বে। আসলে বাড়িওলা কাকু মারা গেছেন গতমাসে। কাকিমা বলেছেন, এবার বাড়িভাড়া না-বাড়ালেই আর নয়। তাই ভাস্করের এই চাকরিটা খুব দরকার ছিল।
বাড়িতে ও মূলত পুরোনো বইয়ের গন্ধের সঙ্গেই দিন কাটাত। এখানে কিন্তু ওর দিন কাটছে নতুন বইয়ের গন্ধের সঙ্গে। এ গন্ধেরও একটা মাদকতা আছে। আঠা, কাগজ এই সব কিছু মিলেমিশে একটা অদ্ভুত গন্ধ তৈরি করছে। অনেক ছোটোবেলায় নতুন স্লেটে চক দিয়ে যখন ও লিখত তখন যেরকম গন্ধ পেত ওর কেন জানি না মনে হচ্ছে নতুন বইয়ের গন্ধটাও ঠিক সেইরকম। নাকি যে কোনো নতুনের গন্ধই এইরকম? মাদকতাময়? গত তিনদিনে চারটে নতুন বই বাঁধাইখানা থেকে বাঁধাই হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝেই ও সেই বইগুলো খুলে একটু করে গন্ধ শুঁকে নিয়েছে। গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কেমন যেন ছেলেবেলায় ফিরে যাচ্ছে বলে ওর মনে হয়েছে।
ছোট্ট এই অফিসটায় ওর সহকর্মী চারজন। লেখা কম্পোজ করে মন্দিরা। বয়সে ওর চেয়ে বেশ অনেকটা ছোটো। ভগবানে খুব ভক্তি। মা কালীর একটা লকেট পরে থাকে। দিনের মধ্যে কতবার যে সেটা মাথায় ঠেকায়! শুভোদয় আবার একেবারেই অন্যরকমের। বয়সে প্রায় ওর কাছাকাছি। সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করে। কাজল পরে। কিন্তু একেবারেই ওর মতো মুখচোরা নয়। বেশ স্মার্ট। কথাবার্তায় ঝকঝকে। ভাস্করের খুব পছন্দ হয়েছে সুদীপবাবুকে। বয়স্ক মানুষ। কাজের ফাঁকে, ভাস্কর খেয়াল করেছে যে, উনি মাঝে মাঝেই বই পড়েন। কোন বই ভালো, কোন বই খারাপ তা নিয়ে মতামতও দেন। আর আশ্চর্য মানুষ হচ্ছেন সুফলবাবু। এই চেয়ারে বসে আছেন। ঝিমোচ্ছেন। এই আবার কোথায় চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক ঘণ্টা পরে। স্বভাবে ভাস্করের একেবারে উলটো সুফলবাবু। যখন উনি ঝিমোচ্ছেন না তখন কথা বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় কথা না-বলে এক সেকেন্ডও বোধহয় থাকতে পারবেন না সুফলবাবু।
ভাস্করের কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। এই তিনদিনেই ও মোটামুটি কাজটা বুঝে নিয়েছে। এখন মেলার সময় নয়। মেলা শুরু হলে যে চাপ বাড়বে সেটা ও বুঝতে পারছে। এখন ওর কাজ হচ্ছে মূলত আগামী দু-মাসে যে-বইগুলো ছাপা হবে সেই বইগুলোর কাজ কতদূর এগিয়েছে তার হিসেব রাখা। বাংলাটা ও ভালোই জানে বলে ওকে গৌরবদা ইতিমধ্যেই একটা-দুটো বইয়ের প্রুফ দেখতে দিয়েছে। দেখতে গিয়ে ভাস্করের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে। যেমন এখন ও প্রুফ দেখছে একটা উপন্যাসের। যিনি লিখেছেন সেই লেখক বেশ নামকরা। কিন্তু বাংলা বানানের ‘ব’টাও তিনি জানেন বলে ভাস্করের মনে হচ্ছে না। প্রচুর কারেকশন ওকে করতে হচ্ছে। তবে ভদ্রমহিলার লেখার হাতটি খুব ভালো। এই উপন্যাসটি একটি প্রেমের উপন্যাস। লেখাটা এমনই তরতর করে এগোচ্ছে যে, মাঝে মাঝেই প্রুফ কারেকশন করতেও ভুলে যাচ্ছে ভাস্কর। অনেকটা পড়ে নেওয়ার পর আবার দু-পাতা পিছিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রুফ কারেক্ট করতে করতে যাচ্ছে। এই উপন্যাসের নায়কের নাম অর্ক। নায়িকার নাম তিতলি। তিতলি অনেকটা ভাস্করের মতো। কম কথা বলে। বাইরের মানুষের সঙ্গে তেমন সংযোগ করতে পারে না। আর অর্ক ঠিক মিমির মতো। খুব হ্যান্ডসাম। তড়বড় করে কথা বলে। একটা আইটি কোম্পানির বড়ো পদে আছে। লেখাটার মাঝখান অবধি এসেছে ভাস্কর। ও বেশ বুঝতে পারছে যে, অর্ক আর তিতলির সম্পর্ক টিকবে না। যেমন টেকেনি ওর আর মিমির সম্পর্ক। বুঝতে পারছে যে, তিতলি একাই ভালবাসে অর্ককে। অর্ক তিতলিকে একেবারেই ভালোবাসে না। অনেক সময় হয় না হঠাৎ করেই কেউ একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তারপর আর কিছুতেই সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না – অর্কর হয়েছে তেমন দশা। এখন ভাস্কর বোঝে মিমিও হঠাৎ করেই ওর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। আসানসোল থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল মিমি। প্রথমে একটা মেসে থাকত। এমফিল করা অবধি মেসেই থাকত। পিএইচডিতে জয়েন করে একটা ছোটো এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। মানিকতলাতে। ভাস্করদের ভাড়াবাড়ি থেকে খুব দূরে সেই ফ্ল্যাট ছিল না। ভাবলে ভাস্করের আশ্চর্য লাগে যে, মিমির তখন ফ্রিজ ছিল না বলে রোজ সকালে ভাস্কর গিয়ে বাজার করে তাজা তরি-তরকারি আর মাছ কিনে দিত। মাঝে মাঝে ভাস্কর নিজেই বলত, একদিন তোমার হাতের রান্না খাব। কিন্তু ও বাজার করে দেওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন এমনকি একটু আলুভাজাও মিমি ভাস্করকে খাওয়ায়নি। বরং একদিন মা-ই মিমিকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল। মিমি মাকে বলত মাসিমণি। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে কী প্রশংসাই না মিমি করেছিল! এরপর মাঝেমাঝেই মিমি ভাস্করের মাকে ফোনও করত। জানতে চাইত একটা-দুটো রান্নার রেসিপি।
পরিতোষ ভাস্করকে বলেছে যে, মিমি প্রথম থেকেই খুব ঠান্ডা মাথায় ভাস্করকে ব্যবহার করেছে। বলেছে যে, অনেক মেয়েই এরকম হয়। ছেলেরাও। এখন পুরোনো কথা ভাবতে বসলে ভাস্করের মনে হয় পরিতোষ ভুল বলে না। ভাস্কর পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছিল না ঠিক কিন্তু প্রচুর পড়াশুনা করত। সিলেবাসের সমস্ত নাটক, উপন্যাস আগাগোড়া পড়ত। মিমি ভাস্করের এই গুণটাকেই ব্যবহার করত। প্রায়ই ওকে বলত, আমাকে তুমি একটু গল্পগুলোর জিস্ট বলে দাও না তাহলে আমাকে আর পড়তে হয় না। ভাস্কর বলে দিত। ক্লাস নোটস খুব দ্রুত লিখতে পারত ভাস্কর। স্যারদের বলা সমস্ত কথা লিখে নিতে পারত। ওর সব ক্লাস নোটস নিয়ে নিত মিমি। এইসব নিয়ে অবশ্য ভাস্করের কখনওই কোনো কিছু মনে হত না। ওর মনে হত যে, মিমি ওর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তাই মিমি যখন এমফিল পেল, পিএইচডিতে সুযোগ পেল তখন ও ভীষণ খুশি হয়েছিল। ভাস্কর নিজে এর কোনোটাই পায়নি। কিন্তু ও একদিনের জন্যও মিমিকে ঈর্ষা করতে পারেনি। কারণ ও প্রাণ দিয়ে মিমিকে ভালোবেসেছিল। আজ ও বোঝে যে, পরিতোষই ঠিক। মিমি ওকে একেবারেই ভালোবাসেনি। আসানসোল থেকে কলকাতায় এসে ভাস্করের মতো এমন একজন কলকাতা-নিবাসী, মুখচোরা, বশংবদ প্রেমিক ওর প্রয়োজন ছিল। হ্যাঁ, প্রয়োজনই ছিল। প্রয়োজন মিটতেই মিমি তাই ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।
উপন্যাসটার একটা জায়গা পড়তে পড়তে ভাস্করের বুক হু হু করতে লাগল। উপন্যাসের এই জায়গাটা কলেজ স্ট্রিট কেন্দ্রিক। তিতলি এসেছে কলেজ স্ট্রিটে। ফুটপাথে যেখানে ঢেলে পুরোনো বই বিক্রি হয়, সেই জায়গা থেকে বই কিনছে তিতলি। এই ফুটপাথগুলো ভাস্করেরও খুব প্রিয়। ওর পকেটের জোর তেমন নেই বলে প্রায়ই ও ফুটপাথ থেকে পুরোনো বই কেনে। তেমনই পুরোনো বই কিনছে তিতলি। কিনতে কিনতে হঠাৎ ও পেয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে অর্কর জন্মদিনে অর্ককে উপহার দেওয়া ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। কালির লেখা এখনও উঠে যায়নি। স্পষ্ট লেখা রয়েছে, ‘অর্কর জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা সহ তিতলি’। বিক্রি করার সময় এমনকি অর্ক এই পাতাটা ছিঁড়েও দেয়নি। ছিঁড়ে দিলেও তো পারত। তিতলি এতটা কষ্ট পেত না। কলেজস্ট্রিটে প্রচুর লোকজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনকি কাঁদতেও পারছে না তিতলি। ওর মনে হচ্ছে ও কাঁদলে সবাই ওকে দেখবে।
জায়গাটা পড়তে পড়তে সত্যিই ভাস্করের বুক হু হু করে উঠল। এত নিষ্ঠুর মানুষ হতে পারে? জন্মদিনে পাওয়া উপহার এভাবে বিক্রি করে দিয়েছে পুরোনো বইয়ের দোকানে? ভাস্করের বুক হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। মিমিকেও তো ও চিরকাল বইই উপহার দিয়েছে। সবচেয়ে কম দামে বই উপহার দেওয়া যায় বলেই। মিমি অবশ্য পড়ার বইয়ের বাইরে তেমন বই খুব একটা পড়ত না। গান শুনত না। কবীর সুমনের গান ভাস্করই মিমিকে প্রথম শুনিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের চেনা গান শোনালেও মিমি ধরতেই পারত না কার লেখা। মিমির গোটা পড়াশোনাটাই ছিল পরীক্ষাকেন্দ্রিক। তবু মিমিকে ও বইই উপহার দিত। এমনকি ভাস্কর চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতাও দিয়েছিল। ওর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল এটা ভেবে যে, পুরোনো বইয়ের ভেতর ও যদি কোনোদিন মিমিকে উপহার দেওয়া কোনো বই খুঁজে পায় তাহলে সেই ধাক্কা ও সহ্য করতে পারবে তো?
এই ভাবনাটা মাথায় আসতেই ভাস্কর সম্ভবত ছটফট করতে শুরু করেছিল। মানে ও যে ছটফট করছিল সেটা নিশ্চয়ই বুঝতেও পারছিল শুভোদয়। তাই বোধহয় শুভোদয় ওকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? এই রকম করছ কেন?
ভাস্কর বলল, না তো, শরীর খারাপ লাগছে না তো।
কিন্তু ও বুঝতে পারছিল যে, ওর ঠোঁট শুকিয়ে আসছে, গলা শুকিয়ে আসছে, কেমন যেন বমি বমি পাচ্ছে। চোখের সামনে হঠাৎ করে কতগুলো যেন কালো কালো রিং দেখতে পাচ্ছে।
জ্ঞান যখন ফিরল তখন ভাস্কর দেখল যে, ওকে অফিসের মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখে-চোখে ঠান্ডা জলের স্পর্শ পাচ্ছিল ও। চোখ খুলতেই শুভোদয় ওকে জিজ্ঞেস করল, এখন তোমার ঠিক লাগছে তো?
ও বলল, হ্যাঁ।
গৌরবদা বলল, উঠে বসতে পারবে?
ভাস্কর বলল, হ্যাঁ, পারব।
শুভোদয়, সুদীপবাবু আর সুফলবাবু তিনজনে মিলে ওকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিল। শুভোদয় ওর হাতে জলের বোতলটা ধরিয়ে দিল। ও ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা জল খেল। গৌরবদা বলল, একটু রেস্ট নিয়ে নাও। তারপর তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনব।
ডাক্তারবাবু অবশ্য বললেন যে, তেমন কিছুই হয়নি। অনেকক্ষণ খালি পেটে থাকার জন্য আর মারাত্মক অ্যাংজাইটি থেকেই ও জ্ঞান হারিয়েছিল।
এই ঘটনাটার পর ক-টা দিন ভাস্কর খুবই ভয়ে ভয়ে ছিল। খালি ওর মনে হচ্ছিল যে, ও অসুস্থ, ফিট নয় এই কারণে ওর চাকরিটা চলে যাবে না তো? আতঙ্কে একদিন ও শুভোদয়কে জিজ্ঞেসও করে ফেলল যে, ওর চাকরিটা এইভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য চলে যাবে কি না। শুভোদয় বলল, আরে, চাকরি যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। এই যে সুফলবাবুকে দেখছ না, ফি-বছর উনি মাঝে মাঝে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। চার-পাঁচ মাস অফিসেই আসেন না। কিন্তু তাও তো ওর চাকরি যায়নি। চাকরি যাওয়া নিয়ে টেনশন করো না। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা ঠিক কী সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। তুমি এত অন্যমনস্ক থাক, এভাবে সেন্সলেস হলে – এত অ্যাংজাইটি কীসের তোমার?
শুভোদয়ের গলায় এতখানি মমতা ছিল, এতখানি আন্তরিকতা ছিল যে, ভাস্কর ওকে হড়হড় করে সমস্ত কিছু বলতে লাগল। যে-ভাস্কর ভীষণ মুখচোরা, পরিতোষের বাইরে যে-ভাস্কর মিমির বিষয় নিয়ে এমনকি সজলদার সঙ্গেও কখনও কোনো কথা বলেনি, সেই ভাস্করই কেমন নির্দ্বিধায় শুভোদয়কে বলে ফেলল যে, মিমিকে ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।
৫
মিথ্যের দাম এই পৃথিবী দিতে জানে না। এই বিষয়ে তার এই তেষট্টি বছরের জীবনে সুফলবাবু নিশ্চিত হয়েছেন। অথচ সত্যিটা হল এটাই যে, এই পৃথিবী মিথ্যে ছাড়া চলতই না। কেউ কি এই কথা আদৌ অস্বীকার করতে পারবে? মিথ্যে বলা নিয়ে তাই বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই সুফল বাবুর। কখনও কখনও তিনি বরং মিথ্যে একটু কম বলা হচ্ছে বলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা অঙ্কের নিয়মেই মিথ্যে যত বেশি বলা হবে ততই মিথ্যের কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওর বাগানের ফুলগুলো দেখেই তো সুফল বাবু ঠিক বুঝতে পেরে যান যে, মিথ্যে কার্যকর হচ্ছে কি হচ্ছে না। এখন যেমন উনি খুবই চিন্তায় পড়েছেন। ক-দিন ধরেই লাল ফুলগুলো নেতিয়ে পড়েছিল। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বেগুনি ফুলগুলোও ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে। ভালো লক্ষণ নয়। পৃথিবীর জন্য এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। ওকে মিথ্যে বলার পরিমাণ দ্রুত আরও বাড়াতে হবে। যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের কম মিথ্যে বলা হলে বেগুনি ফুলগুলো শুকিয়ে যায়। অফিসে যেসব কবিরা আসছে এখন কটা দিন তাদের বেশি বেশি করে মিথ্যে বলতে হবে। না-হলে বেগুনি ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে। স্বপ্ন না-থাকলে পৃথিবীর খুব বড়ো বিপদ হতে পারে।
মিথ্যে বলা নিয়ে সুফলবাবুর কোনো গ্লানি বোধ নেই। পৃথিবীর কত কিছুই তো মিথ্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এই যে প্রকাশনা সংস্থাগুলো, এগুলোও কি মিথ্যের ওপরেই চলছে না? সুফল বাবু দেখেছেন কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা এই নক্ষত্র প্রকাশনীতে। সত্যিকারের গুণী বড়ো বড়ো মানুষ যেমন আসেন তেমনই দু-কলম ভালো করে বাংলা লিখতে পারেন না অথচ দ্রুত খ্যাতি চান এরকম মানুষও এখানে আসেন। এঁদের মধ্যে আছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধ্যাপক – কে নন! ফি-বছর শীতকালে বিদেশ থেকে চলে আসেন এনআরআইরা। ওঁদের তো অনেক অনেক টাকা। সব পাউন্ড-ডলারের ব্যাপার। দ্রুত খ্যাতি চান এঁরা। একটা কবিতার বই করার জন্য এঁদের কেউ কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত। কেউ কেউ আবার বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশনীর লোগো ব্যবহার করে বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে দেন। বিজ্ঞাপনে এক লাখ টাকা খরচ করার মতো লোকও সুফল বাবু দেখেছেন। অবশ্য নক্ষত্র প্রকাশনীতে এই ধরনের লোক তুলনায় একটু কম আসে। মানে যাঁরা বিজ্ঞাপনের জন্যই এক লক্ষ টাকা খরচ করে দেবে, সেই রকম লোক। ও শুনেছে যে, লাহা বাবুর এই ধরনের খরিদ্দার অনেক বেশি। এভাবে যে-খ্যাতি পাওয়া যায় সে তো গোটাটাই মিথ্যে! মিথ্যে নয়? এমন মিথ্যে যে-মিথ্যে ওর বাগানের গাছে কোনোদিন একটা মিথ্যেফুলও ফোটাতে পারবে না। নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালো রাখতে পারবে না। অবশ্য ছোটো ছোটো পত্রিকাগুলোও আজ প্রকাশনা খুলে এভাবেই লোক ঠকাচ্ছে। সেদিন কে যেন একটা লোক এসে বলছিল এমনকি পুরুলিয়ার ‘আটচালা’ নামে একটা কাগজ বছরে পত্রিকার একটা মাত্র সংখ্যা করে পত্রিকার নামটুকু বাঁচাতে, আর বছরে কুড়ি-তিরিশটা বই ছাপে। বই বিক্রি করে এরা নাকি লেখকদের রয়্যালটিও দেয় না। এখন তো পিওডি চলে আসার পরে সবাই প্রকাশক! চাইলে তুমি আজ কুড়িটা বই ছেপে লেখকের কাছ থেকে তিনশো বই ছাপার টাকা নিয়ে নিতে পারো। আগে এত সহজ ছিল না সবকিছু।
অফিসে চেয়ারে বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে এইসব কথাই ভাবছিলেন সুফলবাবু। বেশ একটা তন্দ্রা মতো, ঘোর-ঘোর ভাব এসে গিয়েছিল। সেই ঘোরটা কাটিয়ে দিল শুভোদয়। বলল, দেখুন ভাস্করের জন্য আমাদের কিছু একটা করা উচিত।
সুফল বাবু বললেন, ওর মূল সমস্যাটা ঠিক কী বলো তো? অজ্ঞান হয়ে গেল কেন?
শুভোদয় বলল, মিমি নামের একটা মেয়েকে ভালোবেসে বেশ জোর দাগা খেয়েছে। এটাই মূল সমস্যা। আমি যা বুঝেছি। তার ওপর রোজগারপাতি তেমন নেই। এখানে জয়েন করেছে ঠিক কিন্তু এখনও তো একমাস হয়নি। মাইনেও পায়নি। কাজেই টাকা-পয়সারও একটা সমস্যা আছে। গৌরবদাকে একমাসের মাইনে আগাম দিতে বললেও দেবে না। টাকাপয়সার ব্যাপারে ও তো চিপ্পুস। তবে টাকা ভাস্করের মূল সমস্যা নয়। আমার মনে হচ্ছে মূল সমস্যাটা আসলে মানসিক। ওর কাউন্সেলিং দরকার। ওকে মিমিকে ভুলিয়ে দিতে হবে।
সুদীপবাবু সুফলবাবুর পাশে বসে শুভোদয়ের এইসব কথা শুনছিলেন। বললেন, কাউন্সেলিং করানো কি সোজা ব্যাপার নাকি? এক-একটা সেশনের জন্য কাউন্সেলররা দেড় হাজার-দু হাজার টাকা নেয়। একটা সেশানে হয়ও না। অন্তত আট-দশটা সেশন লাগে। এইসব কাউন্সেলিং-টাউন্সেলিং গরিব লোকেদের জন্য নয়। বড়োলোকদের ব্যাপার।
শুভোদয় বলল, সেই জন্যই তো আমি চাইছি যে, সুফলবাবু ওর সঙ্গে ভালো করে একটু কথা বলুন। সুফলবাবু তো দারুণ কথা বলেন। কি সুফলবাবু, ওকে আপনি একটু বোঝাতে পারবেন না?
সুফলবাবু বললেন, আরে আমি কি আর কাউন্সেলিং করতে পারি নাকি? আমাকে দিয়ে এইসব হবে না।
সত্যিই তো। মিথ্যে কথা উনি অক্লেশে বলতে পারেন এটা ঠিক। কিন্তু কাউন্সেলিং করা কি আর ওঁর কাজ? ওরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে ভাস্করের সম্ভবত মনের রোগ হয়েছে। কেবল কাউন্সিলিং নয় ওর একজন সাইক্রিয়াটিস্টও দরকার।
শুভোদয় বলল, আরে সুফলবাবু, একটু কথা বলেই দেখুন না। আপনি তো কথা বলে মশাই দিনকে রাত করে দেন দেখেছি। ওর সঙ্গে কথা বলতে আপনার আপত্তি কি?
সুফলবাবু বললেন, এই মিমি বলে মেয়েটা কী করে?
শুভোদয় বলল, একটা স্কুলে পড়ায়। দারুণ সুন্দরী। বয়েস ভাস্করেরই মতো। ওরা দুজনে ক্লাসমেট ছিল। কিন্তু এখন মিমি ওদের চেয়ে প্রায় ছয় সাত-আট বছরের ছোট ভীষ্ম ব্যনার্জি বলে একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। আগে থাকত ভাস্করেরই ঠিক করে দেওয়া মানিকতলার একটা ফ্ল্যাটে। এখন সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে সাউথের দিকে। কোন একটা কমপ্লেক্সে চার তলায় থাকে ওই ভীষ্ম বলে ছেলেটার ফ্ল্যাটের উলটো দিকের ফ্ল্যাটে। কিন্তু কোথায় থাকে সেটা ভাস্কর জানে না। এখন আর মিমির সঙ্গে ভাস্করের কোনো যোগাযোগই নেই। মিমি ফোন নম্বর পালটে ফেলেছে। এইসব কথাই ভাস্করের পাড়ার বন্ধু পরিতোষ ওকে জানিয়েছে। পরিতোষ মিমির স্কুলের পাশের স্কুলটাতেই পড়ায়।
সুফলবাবু বললেন, এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এটা লস্ট কেস। ওই মেয়েটা ভাস্করকে আর পাত্তাই দেবে না। এইরকম কত কেসই না দেখলাম এ জীবনে! দুনিয়াটাই তো ধান্দাবাজ মানুষে ভরা। প্রয়োজন ছিল, তাই ভাস্করকে ক-দিন নাচিয়ে ছিল। এখন প্রয়োজন নেই, তাই ছেড়ে দিয়েছে। এ তো সোজা কেস। এটা বুঝছে না?
শুভোদয় বলল, আরে এ তো সোজা নয়। ওদের দু-চার দিনের সম্পর্ক নয়। ষোলো বছরের সম্পর্ক। সেজন্যই তো ভাস্কর কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছে না।
মন্দিরা সাধারণত এক মনে নিজের কাজ করে। ওদের এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে একেবারেই ঢোকে না। এইবার কিন্তু মন্দিরাও বলল, সুফলবাবু আপনি কত লোককে বুঝিয়ে-শুনিয়ে প্রতিদিন কত কী খেয়ে নেন, আর যার দরকার তাকে সত্যিই বোঝাতে পারবেন না যে, মিমিকে ও যেন ভুলে যায়? আপনি দেখুন না। আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবেন।
মন্দিরার কথা শুনে সুফলবাবু একটু দোটানায় পড়ে যান। ওর কী করা উচিত বুঝতে পারেন না। মাত্র ক-দিনই দেখেছেন এই ছেলেটিকে কিন্তু ভাস্কর তো ওর সহকর্মীই। ওকে ওঁর কি বোঝানো উচিত যে, মিমি ওকে ব্যবহার করে ছুড়ে দিয়েছে? ওর মিমিকে ভুলে যাওয়াই মঙ্গল? এটা তো একটা সত্যি কথাই। একথা ঠিক যে, ওঁর সহকর্মীদের কাউকেই উনি ওঁর আসল বাড়িটা কোথায় তা আজ অবধি বলেননি। কিন্তু মিথ্যেও তো বলেননি। সহকর্মীদের কাউকে তো উনি মিথ্যে বলেন না। সহকর্মীদের মিথ্যে বললে বাগানের মিথ্যেফুল গাছগুলোর অনেকগুলো মরে যাবে। শুভোদয়কে মিথ্যে বলেই এই রকম হয়েছিল একবার। কত কষ্ট করে তখন ওঁকে আবার মিথ্যেফুল গাছের ফুল থেকেই বীজ বানিয়ে নতুন গাছ লাগাতে হয়েছিল। সে কি কম ঝক্কি ছিল? পৃথিবীর কতজন মানুষের অবস্থা কী খারাপই না ছিল ওই ক-দিন সেটা উনি বোঝেন। আত্মীয়স্বজনদের কাউকে মিথ্যে বললেও মিথ্যেফুল গাছগুলো মরে যায়। সহকর্মীরাও তো আত্মীয়ই। তাদের মিথ্যে বললেও একই ফল হয়। এই ভয়েই উনি সহকর্মীদের মিথ্যে বলেন না। তাহলে ভাস্করের ক্ষেত্রে ওঁর কি করা উচিত? উনি কি সত্যি বলবেন নাকি মিথ্যে?
৬
মিথ্যেফুল গাছের বাগানটা এখন কলেজস্ট্রিটে আছে মানে এটা যে চিরকাল কলেজ স্ট্রিটেই থাকবে তার কোনো মানে নেই। এই বাগানটা পোর্টেবল। মানে যখন যেখানে সুফলবাবু যান এই বাগানটা সঙ্গে করে নিয়ে চলে যান। উনি যখন কাশ্মীরে গেছিলেন তখনও ফুল গাছের বাগানটা ওঁর সঙ্গেই ছিল। চার পাঁচ দিনের বেশি কোথাও গেলেই উনি সবসময় মিথ্যেফুল গাছের বাগানটাকে সঙ্গে নিয়েই যান। কয়েকদিন আগে সাত দিনের জন্য উনি বিশেষ একটা দরকারে বাঁকুড়া গিয়েছিলেন। তখনও এই বাগানটা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন। বাগানটাকে এভাবে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে সমস্যা সত্যিই ওঁর কিছু হয় না কারণ এই বাগানটা দেখভালের জন্য তো আর সত্যি সত্যিই মাটি, সার, জল এসব ওঁকে দিতে হয় না। কেবলমাত্র মিথ্যে কথা ঠিকঠাক বলতে পারলেই বাগানটা ঝলমল করে। আর বাগানটা ঠিক থাকা মানেই সুফলবাবু জানেন পৃথিবীর অনেকগুলো মানুষের জীবন ঠিক থাকবে।
মিথ্যেফুল গাছের এই বাগানটার মালিক উনি মানে এমনটা কিন্তু নয় যে, ছোটবেলা থেকেই সুফলবাবু মিথ্যে কথা বলতেন। সদা ‘সত্য কথা বলিবে’র মতো বাক্য পড়েই আরও পাঁচজন সাধারণ বাঙালি ছেলের মতোই তিনিও বড়ো হয়েছেন। ক্লাস ফাইভে ওঁদের ক্লাস টিচার ছিলেন হরিশংকরবাবু। বুড়ো মানুষ। সুফলবাবু যখন ক্লাস ফাইভে ওঠেন তখন হরিশঙ্করবাবুর রিটায়ারমেন্টের দোরগোড়ায়। স্কুলের সবাই বলাবলি করত যে, উনি নাকি গান্ধিবাদী ছিলেন। গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। হরিশংকরবাবু অবশ্য শুধু যে গান্ধিবাদী ছিলেন তাই নয়। ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও ভক্ত। ক্লাসে প্রায়ই উনি বলতেন, গান্ধি আর রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ছিলেন সত্যের পূজারী। সব সময় সত্যি কথা বলবি। গান্ধি কি বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন সত্যর জন্য সব কিছুকেই ছাড়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে ছাড়া যায় না। আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে। ছোটোবেলায় এই কথাগুলো শুনে সুফলবাবু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে বুঝেছেন যে, মহাপুরুষদের বাণী দিয়ে জীবন চলে না। বুঝেছেন যে, সাহিত্যের সঙ্গেও জীবনের যোগ খুব কম। জীবনটা কবিতা নয়। মিথ্যে না-থাকলে বেঁচে থাকা বেশ কঠিন। এই পৃথিবীর অনেক মানুষের কাছে।
মিথ্যে যে মানুষের বেঁচে থাকতে সত্যিই খুব কাজে লাগে সেকথা সুফলবাবু বুঝেছিলেন ক্লাস নাইনে। তখন ওর পনেরো বছর বয়স। জন্ম থেকেই উনি একটা ছবিকে ওঁর বাবা বলে জানতেন। ওঁদের শোবার ঘরে দরজার মাথায় ঝুলত একটা ছবি। কপালে চন্দন পরানো। বড়ো গোল টিপ। মাথার ঠিক মাঝখানে। একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের লোকের ছবি। দেখতেন লোকটা স্থির চেয়ে আছে ওঁর দিক। নাম পরেশ ঘোষ। মারা গেছে ওঁর জন্মের কয়েক মাস আগে। এই লোকটাকেই তো বাবা বলে জানতেন সুফলবাবু পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ওই ছবিটাকে প্রণাম করে যেতেন। আর একটা লোক আসত ওদের বাড়িতে। লোকটার নাম আজও উচ্চারণ করতে ওর ইচ্ছে করে না। মোটাসোটা চেহারা। খুদি খুদি চোখ। প্রায়ই সন্ধেবেলা এসে মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করত। মাঝে মাঝে ওঁর সামনেই মায়ের হাতে অনেকগুলো টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যেত। ওর যখন পনেরো বছর বয়স তখন একদিন হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে লোকটা মারা যায়। লোকটা মারা যাওয়ার পরে সুফলবাবুকে ওঁর মা বলেন যে, ওঁকে শ্মশানে যেতে হবে লোকটার মুখাগ্নি করার জন্য। লোকটার বউ ছিল, কিন্তু ছেলেপুলে ছিল না। সুফলবাবু কিছুতেই শ্মশানে যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু ওঁর মা প্রায় বাধ্য করেন ওঁকে শ্মশানে যেতে। মুখাগ্নি করতে। শ্মশান থেকে ফিরে এসে সুফলবাবু জানতে পেরেছিলেন যে, পরেশ ঘোষ ওঁর বাবা নয়। ওঁর বাবা ওই খুদি খুদি চোখের হোঁৎকা লোকটা। একটু আগে যাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছেন। ওঁর জন্মের কিছুদিন আগে এই তথ্যটা জানার পরেই পরেশ ঘোষ সুইসাইড করেছিলেন। সুফলবাবুরও মনে হচ্ছিল যে, উনি আত্মহত্যা করলেই বেঁচে যাবেন। কিছুতেই মানতে পারছিলেন না যে-লোকটাকে উনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘেন্না করতেন সেই লোকটাই ওঁর বাবা। সেই দিনই উনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, মহাপুরুষদের জীবন আর সাধারণ মানুষের জীবন এক নয়। বুঝতে পেরেছিলেন যে, কবিতা আর জীবন এক নয়। সত্যকে কখনও কখনও সহজ করে নেওয়া যায় না। বরং মিথ্যেই মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
সে বছরই সুফলবাবু এই মিথ্যেফুলের বাগানটা করতে শুরু করেন। ওঁদের বাড়ির ছাদে। ছোটো একতলা বাড়ির ছাদে মাত্র তিনটে গাছ নিয়েই উনি এই বাগানটা শুরু করেছিলেন। আজ বাগানটায় কতগুলো গাছ! এ তো এমনি এমনি হয়নি। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওঁকে। অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যেতে হয়েছে। তবেই বাগানটা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। লাল, নীল, হলুদ, কমলা, বেগুনি কত রং এর ফুল ফোটে। কেবল যে ওঁর চোখকেই আরাম দেয় ফুলগুলো তা তো নয়। সুফল বাবু জানেন যে, যত বেশি ফুল ফোটে তত বেশি মানুষ এই পৃথিবীতে আশ্রয় পায় মিথ্যের কাছে। যত ধরনের, যত রঙের ফুল ততগুলি ধর্মের, শ্রেণির, রঙের মানুষ আশ্রয় পাবে মিথ্যের কাছে। সুফল বাবু নিশ্চিত এ বিষয়। শুধু আত্মীয়-স্বজনদের আর সহকর্মীদের বলা মিথ্যে কথায় উলটো ফল হয়। গাছগুলো ঝিমিয়ে পড়ে। ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ে। শেষে মারাও যায়। মায়ের যখন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল তখন সুফলবাবু ওঁকে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, বায়োপ্সি টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ। টিউমারটা ম্যালিগন্যান্ট নয়। এরপর ভয়ংকর একটা জিনিস হয়েছিল। দশটা গাছ মরে গিয়েছিল। সহকর্মীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। একবার শুভোদয়ের সঙ্গে বইমেলার পরে ওঁর বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। গাড়ি থেকে কে কত বই নামাবে এই নিয়ে ঝামেলা। এইসব ঝামেলা বইপাড়ায় মাঝে মাঝেই হয়। সুফলবাবু শুভোদয়কে বলেছিলেন, তুমি তো ছোকরা হে, তোমার কি উচিত নয় আর একটু বেশি বেশি বই নামানো? এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। এরপর কিছুদিন শুভোদয় ওঁর সঙ্গে কথা-বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। এইসব দেখে গৌরববাবু ওঁদের বলেছিলেন যে, দেখ, আমরা কিন্তু একটা পরিবার। সহকর্মীরা আসলে আত্মীয়। সহকর্মীদের আত্মীয় ভাবতে না-পারলে কোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্ভব নয়। এই কথাটা ভীষণ ভাবিয়েছিল সুফলবাবুকে। সহকর্মীরা কি সত্যিই আত্মীয়? পরখ করে দেখার জন্য উনি সুদীপবাবুকে একটা নিরীহ মিথ্যে কথা বলেছিলেন তাতেই কিন্তু দুটো গাছ মরে গিয়েছিল। সেই থেকে সুফল বাবু আর কিছুতেই সহকর্মীদেরও মিথ্যে বলেন না। উনি জানেন এর ফল হবে মারাত্মক। সত্যি বলতে যখন পারেন না তখন উত্তর দেন না বা ‘হু, হ্যাঁ’ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেন কিন্তু মিথ্যে বলেন না। তাই উনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে, ভাস্করকে মিথ্যে কথা বলা ঠিক হবে কি না।
৭
বেশ কিছুদিন ধরেই ভাস্কর মনমরা হয়ে থাকছিল এ কথা ঠিক। মাঝে নাকি অফিসে একদিন সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল, রিহার্সালে এসে একদিন হড়হড় করে বমিও করল। কিন্তু ওর যে কর্কট রোগের মতো এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি শরীরে বাসা বেঁধেছে সে কথা সজল দত্ত ভাবতেও পারেননি। গৌরববাবু যে-ডাক্তারকে ভাস্করকে দেখিয়েছিল তিনি বলেছিলেন যে, এটা আসলে অ্যাংজাইটি থেকে হচ্ছে। প্রথম দিকে এটাই ভাস্কর বিশ্বাস করেছিল। বাকিরাও। কিন্তু যখন কিছুতেই বমি কমছে না তখন আরেকজন ডাক্তারকে দেখাবার সিদ্ধান্ত নেন সজল দত্ত। তিনি প্রথমেই একটা ইউএসজি করতে বলেন। ইউএসজি থেকেই দেখা যায় যে, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে প্যানক্রিয়াসের জায়গাটায়। তারপর সিটি স্ক্যান, এমআরআই। ধরা পড়ে যে, প্যানক্রিয়াসের ওপরে একটা টিউমার রয়েছে। সেটাকে অনেকখানি পেঁচিয়ে ফেলেছে এমনকি ক্ষুদ্রান্তের কিছুটা অংশও। ছোটো ছোটো গ্রোথ দেখা গেছে লিভারেও। ডাক্তাররা বলেছেন এটা নাকি মেটাথিসিস শুরু হওয়ার লক্ষণ। ক্যান্সার ধরাই পড়েছে অনেক দেরিতে। এটা প্রায় শেষ অবস্থা। খুব বেশি দিন ভাস্কর এই পৃথিবীতে আর নেই। এই কথাটা ভাস্করকে সরাসরি এখনও পর্যন্ত বলা যায়নি। ভাস্করের মাকেও না। সজল দত্ত জানেন। জেনেছে নাটকের দলের ছেলেরা আর জেনেছেন গৌরববাবু। গৌরববাবুকে না-জানিয়ে উপায় ছিল না। কেননা ভাস্করের পক্ষে এই শারীরিক অবস্থায় চাকরিটা করা অসম্ভব। ছ-মাস চাকরি করেই ছেলেটা চাকরির সুখটুকুও আর পেল না। ওই ছ-মাসের মাইনে থেকে সামান্য কিছু টাকা জমিয়েছিল ভাস্কর। তবে সেই টাকাতে কি আর এত বড়ো চিকিৎসা হয়? নাটকের দলের ছেলেরা অবশ্য প্রচুর সাহায্য করেছে সজল দত্তকে। সাউথের দিকের আরও কয়েকটা ছোটো ছোটো দলও আর্থিক সাহায্য করেছে। তা না-হলে ইতিমধ্যেই যে-পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে সেই টাকা সজল দত্তের একার পক্ষে খরচ করা সম্ভব হত না। ভাস্কর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সজল দত্ত দেখলেন যে, বিপদে আজও মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।
রোজ সন্ধেবেলা এখন অফিস থেকে ফিরে সজল দত্তর নিয়ম করে ভাস্করকে দেখতে যান। প্রায়ই ওর সঙ্গে ভাস্করদের বাড়িতে ভাস্করের বন্ধু পরিতোষের দেখা হয়। পরিতোষের কাছ থেকে আরেকটা নতুন বিষয় জেনেছেন সজল দত্ত। মিমি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি সেই কলেজবেলা থেকে সম্পর্ক ছিল ভাস্করের। সে এখন ভাস্করকে ধোঁকা দিয়ে ভীষ্ম ব্যানার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে লিভ-ইন জাতীয় কিছু করছে। এই বিষয়টা নিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ভাস্কর। সজল দত্তর সামনেই বেশ কয়েকবার ভাস্কর পরিতোষকে জিজ্ঞেস করেছে ভীষ্ম ব্যানার্জির ব্যাপারে। জানতে চেয়েছে ভীষ্ম ব্যানার্জির ফ্ল্যাটের অ্যাড্রেসটা পরিতোষ খুঁজে পেয়েছে কি না। সম্ভবত সজল দত্ত আছেন বলেই এর বেশি স্পষ্ট করে আর কিছুই ভাস্কর বলেনি। সজল দত্তকে অদ্ভুত শ্রদ্ধা করে ভাস্কর। পরিতোষ সত্যিই জানে না ভীষ্ম ব্যানার্জি কোথায় থাকে। সজল দত্ত একবার পরিতোষকে বলেছিলেন যে, ভীষ্ম ব্যানার্জি বলে এই ছেলেটি কোথায় থাকে সেটা খোঁজ নেওয়া কি সত্যিই সম্ভব নয়? পরিতোষ বলেছিল, খোঁজ নিয়ে কী হবে বলুন তো দাদা? আমি অনেক করে ভাস্করকে বুঝিয়েছি যে, মিমিকে ভুলে যেতে হবে। কিন্তু এটা একটা অবসেশনের মতো হয়ে গেছে ওর কাছে। ওর ঠিকানাটা ভাস্করের চাই। এই একই কথা আজ কতদিন ধরে আমাকে বলে চলেছে। ও নিজেও বুঝতে পারছে যে, মিমি ওকে ব্যবহার করে নিয়েছে কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। কিছু কিছু সত্য তো জীবনে মেনে নিতে হয় সজলদা, তাই না? আমি যদি খবর এনেও দিই যে, কোথায় থাকে ভীষ্ম ব্যানার্জি আর মিমি, ভাস্করকে কি সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে? শরীরের এই অবস্থায়? নিয়ে গিয়ে লাভই বা কী হবে? গিয়ে যদি ভাস্কর দেখে যে, ওরা সত্যিই লিভ-ইন করছে, তখন সেই সত্যকে আদৌ মেনে নিতে পারবে তো ভাস্কর?
এই কথাটা শুনেই সজল দত্তর মাথায় একটা ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সত্যিই তো আর ক-টা দিনই বা বাঁচবে ভাস্কর! ওকে জীবনের শেষ ক-টা দিন একটু শান্তি দেওয়া যায় না? সেই শান্তি যদি আসে মিথ্যে বলেই তাতেই বা ক্ষতি কি? এই ভাবনাটা মাথায় আসতেই ওঁর মনে পড়েছে সুফলবাবুর কথা। সুফলবাবু তো এখন ভাস্করের সহকর্মী। ওঁকে বললে কিছুদিন উনি বেশ গুছিয়ে কিছু মিথ্যে কথা ভাস্করকে বলতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। বললে সেটা কি অন্যায় কাজ করা হবে আদৌ? একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ যদি কয়েকটা মিথ্যে কথা বলায় একটু ভালো থাকেন, তাহলে সেটা কি খুবই অনৈতিক কাজ হবে? এই যে ওরা নাটক করেন এর মধ্যেও তো অনেকখানি মিথ্যেই থাকে। যে-চরিত্র ওঁরা সেজে ওঠেন মুখে রং মেখে, আসল জীবনে সেই চরিত্র তো ওঁরা কখনওই নন। ভাস্করও তো মঞ্চের ওপর যে-কাজটা করত তা এক ধরনের মিথ্যেই। কখনও মঞ্চটাকে ও বানিয়েছে বড়োলোকের বৈঠকখানা, কখনও পার্ক, কখনও বা ষোড়শ শতাব্দীর দিল্লি। এসব কি মিথ্যে নয়? এই মিথ্যে তো আসলে ব্যবহার করা হয় মানুষকে আনন্দ দিতেই। তাহলে মৃত্যু পথযাত্রী ভাস্করকে জীবনের শেষ কটা দিন মিথ্যে বলে সামান্য আনন্দ দিলে ক্ষতি কি? পরিতোষের সঙ্গে এ নিয়ে বেশি কথা বলে লাভ নেই। সজল দত্ত ঠিক করলেন যে, সুফলবাবুকে উনি নিজেই বলবেন ভাস্করকে উনি যেন বলেন যে, মিমি এখন কোথায় আছে উনি সেটা জানেন। যেন বলেন যে, ভীষ্ম ব্যানার্জির বিষয়টা সম্পূর্ণ মিথ্যে। রটনা মাত্র।
৮
সুফলবাবু বললেন, যাই বলো, মিমিকে কিন্তু দুর্দান্ত দেখতে। একেবারে সরস্বতী ঠাকুরের মতো।
শুনে শিশুর মতো হেসে উঠল ভাস্কর৷ লাজুক হাসি। ও যখন প্রথম অনার্সের ক্লাসে দেখেছিল মিমিকে ওরও মনে হয়েছিল যে, মিমি সত্যিই সরস্বতী ঠাকুরের মতো দেখতে।
ওকে মুচকি হাসতে দেখে সুফলবাবু বললেন, সত্যিই। প্রতিমার মতো সুন্দরী মিমি।
ভাস্কর বলল, মিমি কি বুঝতে পেরেছে যে, আমি আপনার কলিগ?
–না, না, বুঝবে কী করে? আমি তো গেছিলাম ক্লাসের বইয়ের স্পেসিমেন কপি নিয়ে। বুঝবে কী করে?
–ভীষ্ম ব্যানার্জিকে কি দেখলেন?
–দেখলাম তো। লম্বা। গোলমতো মুখ। চশমা পরে। ভালো নয় দেখতে।
–তাই? সত্যিই ভালো নয় দেখতে?
–নানা একেবারেই ভালো নয়।
–নিশ্চয়ই ভালো পড়ায় তাহলে?
–আমি তো একটু খোঁজখবর নিলুম। তেমন রিপোর্ট তো পেলাম না।
–তাহলে মিমি ওর প্রেমে পড়ল কী করে বলুন তো?
–আরে ভাই, প্রেমে পড়েছে এই কথাটা তোমাকে বলল কে?
–পরিতোষ। ও বলেছে যে, মিমি এখন লিভ-ইন করছে ভীষ্মর সঙ্গে।
–কই? আমি তো পুরোটা দিন ওদের স্কুলে কাটিয়ে এলাম। দেখে তো মনে হলো না আদৌ ওদের কোনো প্রেমের সম্পর্ক আছে বলে। ভীষ্ম তো ওকে সারাক্ষণ ‘দিদি দিদি’ বলছিল দেখলাম।
–বয়স তো ভীষ্মর ওর চেয়ে কম। তাই ও তো ‘দিদি’ বলবেই সবার সামনে। ওরা কি মুখোমুখি ফ্ল্যাটে সত্যিই থাকে?
–এটা তো আমি জানি না। চিন্তা করো না । আমি ঠিক খুঁজে দেখে নেব মিমি কোথায় থাকে।
সজল দত্ত যখন প্রথম সুফলবাবুকে বলেন যে, ভাস্করকে উনি একটু মিমির সম্বন্ধে কয়েকটা মিথ্যে কথা বলতে পারবেন কি না তখন সুফলবাবু বেশ ঘাবড়ে গেছিলেন। উনি বুঝতে পারছিলেন না যে, ওঁর কী করা উচিত। শুভোদয় ওঁকে বলেছিল যে, উনি চেষ্টা করলে কাউন্সেলিং করতেই পারেন ভাস্করের। কিন্তু সুফলবাবু বুঝতে পারছিলেন না যে, একজন সহকর্মীকে মিথ্যে কথা বললে ক-টা মিথ্যেফুল গাছ মারা যাবে। যদি অনেকগুলো মরে যায় তাহলে পৃথিবীর অনেকজন মানুষেরই অনেক ক্ষতি হতে পারে। একজনের জন্য অনেকজনের ক্ষতি করা কি উচিত হবে? সবচেয়ে বড়ো কথা ভাস্করের কেসটা তো এমন নয় যে, একটা মিথ্যে কথা বললেই কাজ হয়ে যাবে। উনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওঁকে দিনের পর দিন মিথ্যে কথা বলে যেতেই হবে। মিমির সম্পর্কে একটা মিথ্যে বললে তো কাজ হবে না। ভাস্করকে পর পর মিথ্যে বলে যেতেই হবে ওঁকে। উনি তাই কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে, ওঁর কী করা উচিত হবে। তবে শেষমেশ উনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ভাস্করকে মিথ্যে বলবেন। কয়েকটা গাছ হয়তো এতে মারা যাবে। যতগুলো গাছ মারা যাবে তার চেয়ে বেশি গাছ উনি তৈরি করে নেবেন মিথ্যে বলে বলেই। পৃথিবীর বড়ো ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না। এখনও পর্যন্ত ওঁর হিসেব মিলে গেছে। এজন্য ওঁকে অনেক বেশি মিথ্যে বলতে হচ্ছে এখন এই কদিন, এই যা। ভাস্করের কাছে তো মিথ্যে বলছেনই উনি। ওঁদের অফিসে যাঁরা আসছেন তাঁদের কাছে, রাস্তাঘাটে দেখা-হওয়া মানুষজনের কাছেও অনর্গল মিথ্যে বলে যাচ্ছেন। এক একদিন এমন হচ্ছে যে, সারাদিনে দশটা সত্যি কথাও বলছেন না সুফলবাবু। কিছু গাছ মরে গেছে। কিছু গাছের চারা জন্মেছে। এরা বড়ো হবে। মিথ্যেফুল ফোটাবেই। অনেক মানুষের কাছে পৃথিবীকে সহনীয় করতে।
যত দিন যাচ্ছে ভাস্করের শরীরটা যেন গুটিয়ে ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অবশ্য ওকে টাটা মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন সজল দত্ত। ওর এখন যা অবস্থা তাতে কেমো দেওয়া যাবে না। রেডিয়েশন থেরাপি শুরু হবে ক-দিন পর থেকে। তারপর কেমো। তবে ততদিন পর্যন্ত ও বেঁচে থাকবে কি না সেটাই একটা বিরাট বড়ো প্রশ্ন। এর মধ্যে অবশ্য ভাস্করকে সত্যি কথাটা বলতেই হয়েছে সজল দত্তকে। উনি ভাস্করকে বলেছেন যে, ওর পাকস্থলিতে ক্যান্সার হয়েছে। এবং ধরাও পড়েছে একেবারেই আর্লি স্টেজে। রেডিয়েশন এবং কেমোর মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাবে। ও এখনও আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। ভাস্করের মাকেও প্রায় এমনই একটা কথা বলেছেন সজল দত্ত। সুফলবাবুর সামনেই।
৯
পাটুলিতে কে. কে. দাস কলেজ আছে জানো? ওদের ফ্ল্যাটগুলো তার পাশে। একটা বড়ো বিল্ডিংয়ের চারতলায় মুখোমুখি ফ্ল্যাটে ওরা দুজন থাকে। বিল্ডিংটার নাম রোশন প্লাজা। ফ্ল্যাটটার উলটো দিকে একটা বড়ো চায়ের দোকানও আছে। যাওয়া খুবই সোজা।
–এটা আপনি বলেই সম্ভব হলো সুফলবাবু। আমি জানতাম যে, আপনি ঠিক আমাকে মিমির ঠিকানা জোগাড় করে দেবেন।
ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম বড়ো মায়া হল সুফলবাবুর। মিমির সম্বন্ধে উনি যা যা বলছেন বেচারি বিশ্বাস করছে। অথচ সত্যিটা হল এই যে, উনি মিমির নতুন ফ্ল্যাট কোথায় একেবারেই জানেন না। ডাঁহা মিথ্যেই বলে চলেছেন টানা।
–এ আর তেমন কী কাজ? সহজেই মিমির ফ্ল্যাটের ঠিকানা জোগাড় করে ফেললাম। একদিন ওর স্কুলে গেলাম। ফিরলাম একসঙ্গে ট্রেনে। তারপর ওকে আর ভীষ্ম ব্যানার্জিকে বুঝতে না-দিয়ে ওদের ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সোজা ব্যাপার তো।
–ভীষ্ম আর মিমি কি একই সঙ্গে যাতায়াত করে?
–হ্যাঁ, করে তো ।
বলেই সুফলবাবু দেখলেন ভাস্করের মুখ কেমন মলিন হয়ে গেল। উনি বললেন, আরে ওদের একটা দল আছে। একজন মিলে একসঙ্গে যায় আর আসে ট্রেনে। তারপর গড়িয়া থেকে অটো।
–একই অটোতে পাশাপাশি বসে মিমি আর ভীষ্ম?
–আমি যেদিন ওদের ফলো করলাম সেদিন তো দেখলাম আলাদা আলাদা অটোতেই উঠল। তবে নামল তো একই স্টপে। একই বিল্ডিংয়ের মুখোমুখি ফ্লাটে থাকে তো।
–তাহলে ওরা তো লিভ ইন করছে না।
–না না। প্রেম-টেম এর ব্যাপারই নেই। শোনো শোনো কী হয়েছে।
–কী হয়েছে?
–আরে আমি তো মিমির ফ্ল্যাট চিনে যাওয়ার পর আরেকদিন সন্ধেবেলা কিছু না বলে-কয়ে সোজা ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির।
–আপনাকে দেখে চমকে যায়নি?
–গিয়েছিল তো।
–ঢুকতে দিল আপনাকে?
–দিল তো। ঢুকলাম তো। কথা বললাম তো।
–কী বলল মিমি?
–আরে আমি তো গিয়েছিলাম একটা প্রস্তাব নিয়ে। বললাম যে, নতুন বছরে আমাদের প্রকাশনা থেকে নাইন-টেন এর বাংলা সহায়িকা প্রকাশ করব, উনি সেই বই লিখতে আগ্রহী কি না।
–কী বলল মিমি?
–এইসব বই লিখতে আদৌ উনি আগ্রহী নন। তবে বই লেখার প্রস্তাব দেওয়া তো আমার একটা ছুতো ছিল। আমি তো আসলে গিয়েছিলাম তোমার বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে।
–ওকে বললেন আমার নাম?
–হ্যাঁ বললাম তো। বললাম যে, তুমি খুবই অসুস্থ।
–কী বলল ও?
–কেমন অসুস্থ, তুমি কতদিন ধরে অসুস্থ – এইসব জানতে চাইল। বললাম সব।
–শুনল?
–শুনল তো। শুনে বেশ মুষড়েই পড়ল বলে তো আমার মনে হল।
–সত্যি?
–দেখো আমি কিন্তু সহকর্মীদের কোনো মিথ্যে কথা বলি না, কারণ সহকর্মীরা তো আমার আত্মীয়ই। তোমাকে কেন শুধু শুধু মিমির বিষয়ে মিথ্যে কথা বলব বলো? আর মিথ্যে বললে তো আমি বলতেই পারতাম যে, ওরা একই বিল্ডিংয়ে থাকে না। সেটা তো বললাম না।
শুনে ভাস্কর খানিকটা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল সুফলবাবুর। জিজ্ঞেস করল, আমি অসুস্থ শুনে কিছুই বলল না মিমি? শুধু একটু মুষড়ে পড়ল? আপনি বলেছেন তো আমার ঠিক কী রোগ হয়েছে?
–সব বলেছি। মুষড়ে পড়েনি শুধু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে চাইছিল তোমার ব্যাপারে।
–সত্যি?
–হ্যাঁ, অবশ্যই সত্যি। এমনকি এটাও বলল যে, তোমার নাকি একটু জ্বর হলেই তুমি মাকে দিয়ে মাথা ধোয়াতে বলতে। এত বড়ো একটা রোগের যন্ত্রণা তুমি সহ্য করছো কী করে?
জ্বর হলে এই মাথা ধোয়ানোর ব্যাপারটা সুফল বাবুকে একদিন ভাস্করের মা নিজেই বলেছেন। কায়দা করে এইখানে সেই তথ্যটাকে সুফলবাবু একটু ব্যবহার করে নিলেন।
শুনে ভাস্করের কুঁকড়ে যাওয়া ছোটো শরীরে, তুবড়ে যাওয়া গালে যেন একটা বিদ্যুৎ হিল্লোল খেলে গেল বলে সুফল বাবুর মনে হল। উনি যা যা বলছেন ভাস্করকে, ছেলেটা সমস্ত কথাই কত সরল মনে বিশ্বাস করছে!
ভাস্কর নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকল, মনে আছে সব। ভোলেনি আমাকে পুরোটা। ভোলেনি তাহলে।
সুফলবাবু বললেন, শোনো, আরও ভালো খবর আছে তোমার জন্য। মিমি আমাকে বলেছে যে, ও একদিন তোমাকে দেখতে আসবে।
–ধুস, হতেই পারে না। এটা আপনি পুরো ঢপ দিচ্ছেন।
–যখন সত্যিই আসবে, তখন মিলিয়ে নিও ঢপ কি না।
ওঁর কথাগুলো শুনে আবারও ভাস্করের শরীরে বিদ্যুৎ হিল্লোল তুলল।
সুফলবাবু জানেন যে, আজও বেশ কয়েকটা মিথ্যেফুল গাছ মারা যাবে। কিন্তু সেটা নিয়ে উনি সত্যিই আর তেমন চিন্তিত নন। ওঁর মিথ্যে বলায় ভাস্কর যে কেবল একটু আনন্দ পাচ্ছে তা নয়। জীবনে প্রথম মিথ্যে বলে সুফলবাবু নিজেও বড্ড আনন্দ পাচ্ছেন। ওঁর মনে হচ্ছে বেঁচে থাকা, মিথ্যে-বলা এতদিনে সত্যি সত্যিই সার্থক।
১০
–মিমি আমাকে দেখতে আসা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব তো সুফলবাবু?
প্রায় দু-মাস ধরে সুফলবাবু প্রতিদিন সন্ধেবেলা ভাস্করকে দেখতে আসছেন। দু-মাস ধরেই উনি ভাস্করকে বলে চলেছেন, মিমি ওকে দেখতে আসবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মিমি ওকে দেখতে আসেনি। তাই এই প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত ভাস্কর করেই ফেলেছে।
গাছের মতো কিছু কিছু মানুষ মারা যায়। সব মানুষের মরে যাওয়ার সঙ্গে গাছের মরে যাওয়ার মিল থাকে না। তিলে তিলে যে-মানুষেরা মারা যান তাঁদের মারা যাওয়াটাই কেবল গাছেদের মারা যাওয়ার মতো। অন্য গাছেদের মতোই মিথ্যেফুল গাছও হঠাৎ করে মারা যায় না। মারা যায় ধীরে ধীরে। কীভাবে একটি মিথ্যেফুল গাছ মারা যায় ধীরে ধীরে সেটা সুফলবাবু দেখেছেন। ওঁর মা যখন ক্যান্সারে মারা যাচ্ছিল তখন ওঁর মনে হচ্ছিল মা নয় একটা মিথ্যেফুল গাছই মারা যাচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, মৃত্যুকে একটি দর্শনীয় বস্তু করে তুলে।
এবারও ভাস্করের মৃত্যুর অভিমুখে যাত্রাকে দেখছেন সুফল বাবু। একইসঙ্গে দেখছেন অনেকগুলো মিথ্যেফুল গাছের মৃত্যুকে। আরও কিছু গাছ মারা যাবে। ভাস্করের মতোই তিলে তিলে এই গাছগুলো মারা যাবে। সুফলবাবু জানেন যে, কিছুতেই উনি এই গাছগুলোকে বাঁচাতে পারবেন না। জানেন যে, ভাস্করকেও উনি বাঁচাতে পারবেন না। কেমো শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে নানা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। তাই বোধহয় আজ ওই প্রশ্নটা ভাস্কর করেছে। ডাক্তাররা অবশ্য ভাস্করকে বলেছেন যে, লড়াই করতে হবে। লড়াই করলে ভাস্কর পারবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে। সজল দত্ত সুফলবাবুকে বলেছেন যে, ভাস্কর যাতে ভেঙে না-পড়ে কেবল সেজন্যই ডাক্তারবাবুরা এমনটা বলেছেন। ভাস্কর আর খুব বেশিদিন এই পৃথিবীতে নেই। সব ক-টা কেমোই হয়তো ও নিয়ে উঠতে পারবে না।
এই কথাটা কি ভাস্করকে তাহলে বলে দেবেন সুফলবাবু? উনি দেখছেন যে, এই প্রথম এমন একটা প্রশ্ন সুফল বাবুকে ভাস্কর করেছে যে-প্রশ্নটার উত্তর উনি খুঁজে পাচ্ছেন না। অনেক প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন উত্তর খুঁজে না পেলে ‘হু’ বা ‘হ্যাঁ’ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় এই প্রশ্নটা ঠিক তেমনও নয়। বলা যাবে না ‘হু’ বা ‘হ্যাঁ’ এই দুটোর কোনোটাই। তবে ভাস্করকে এই প্রশ্নটার মিথ্যে উত্তর দিলে কী হতে পারে সেটা অনেকটা আন্দাজ করতে পারছেন সুফলবাবু। ওঁর মনে আছে মৃত্যু নিয়ে মিথ্যে কথা বলায় একবার কী হয়েছিল ওঁর বাগানটার। সরকারি হাসপাতালে ওঁর ছেলেবেলার এক মহিলা বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলেন সুফলবাবু। সেই বন্ধুর পাশের বেডেই ছিলেন এক বৃদ্ধা। ওঁর বন্ধুর কাছে সুফলবাবু শুনেছিলেন যে, ডাক্তারবাবুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন যে, উনি নাকি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। কেউ ওই বৃদ্ধাকে দেখতেও আসত না। জীবন নিয়ে উনি নিজেই হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তাই যেই সুফলবাবুর বন্ধুকে দেখতে আসত, তাকেই উনি জিজ্ঞেস করতেন, আচ্ছা, আমি ঠিক কখন মরব বলতে পারো? মরলে বাঁচি। সুফলবাবুকেও একই কথা বলেছিলেন বৃদ্ধা। সুফলবাবু ওঁকে বলেছিলেন, এখনও অনেকদিন বাঁচবেন। বাঁচা কত সুন্দর, তাই না? এই কথাগুলো বলার ফল হয়েছিল মারাত্মক। পরের দিন সুফলবাবু দেখেছিলেন ওঁর বাগানের অর্ধেক গাছ মরে গেছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। কেননা উনি তো মিথ্যে বলে জীবনটাকে একটু সহনীয়ই করে তুলতে চেয়েছিলেন একজন গরিব বৃদ্ধার। লাল মিথ্যেফুলগুলোর তো মাথা দোলানোরই কথা ছিল এতে। কিন্তু, হয়েছিল ঠিক উলটো। মরে গিয়েছিল অর্ধেক গাছ। সব রঙেরই। অন্য যে বিষয় নিয়েই আত্মীয় ছাড়া অন্যদের মিথ্যে বলেছেন তিনি সেইসব মিথ্যের জোরে ওঁর বাগানের গাছগুলোর মিথ্যেফুলগুলো ঝলমল করেছে। শুধু মৃত্যু নিয়ে মিথ্যে বলার ফল হয়েছিল উলটো। এই নিয়ম মানলে আত্মীয় বা সহকর্মীদের মৃত্যু নিয়ে মিথ্যে বললে অনেকগুলো মিথ্যেফুল গাছের জন্ম হতে পারে কিন্তু। তাহলে কি ভাস্করকে মিথ্যেই বলবেন সুফলবাবু? এতে দুটো লাভ। মিথ্যে শুনে ভাস্কর শান্তিই পাবে। অপেক্ষা করবে মিমির জন্য। জীবন সহনীয় হবে। আর যে-কটা মিথ্যেফুল গাছ মরে গেছে ওঁর বাগানে তার দ্বিগুণ গাছ জন্মে যেতে পারে। লোভ লাগল সুফলবাবুর। লোভ। উনি শেষমেশ মিথ্যেই বললেন ভাস্করকে। বললেন, সজলবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, ডাক্তাররা ওঁকে বলেছেন, তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে। এত মরবার কথা ভেবো না তো।
১১
তিন-চারটে গাছ মাত্র বেঁচে আছে বাগানটায়। ভয়ংকর অবস্থা। ভাস্করকে মিথ্যে বলার ফল। এইরকম হল কী করে? নিয়ম মানলে তো উলটোটাই হওয়ার কথা। মৃত্যু নিয়ে কি তাহলে কাউকেই মিথ্যে বলা যাবে না? বললে, আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই, ওঁর মিথ্যেফুল গাছগুলো মরে যাবে এভাবেই? মৃত্যুই কি তাহলে জীবনের একমাত্র সত্য যাকে সহজে গ্রহণ করতে হয়? কোনো কিছুর জন্যই যাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না? সব রংয়ের, সব ধর্মের মানুষের জন্য মৃত্যুই তাহলে একমাত্র সত্য? আর কোনো কিছুই নয়?
অফিসে নিজের চেয়ারে ঢুলতে ঢুলতে যখন এসবই ভাবছিলেন সুফলবাবু তখনই গৌরববাবু ওর কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে ওঁদের সবাইকে বললেন, একটা খারাপ খবর আছে। সজল দত্ত এইমাত্র ফোন করেছিলেন। একটু আগে ভাস্কর মারা গেছে। বাড়িতেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি।
শুনে সুফলবাবুর মনে হল যে, ভালোই হয়েছে। ভাস্কর এমন একজনকে পেয়েছে যে ওকে মিমির মতো ছেড়ে যাবে না কোনোদিন।
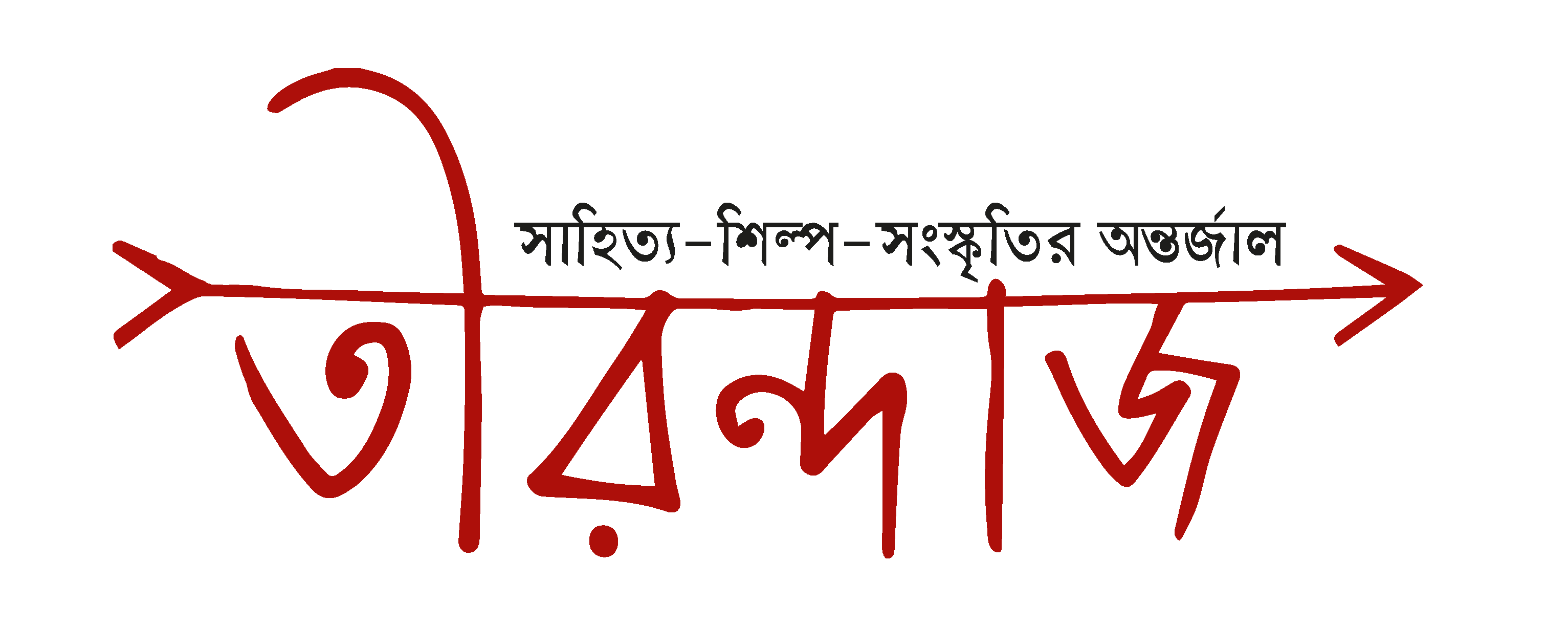

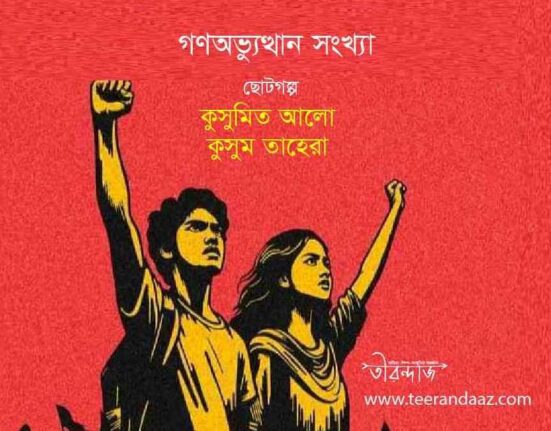


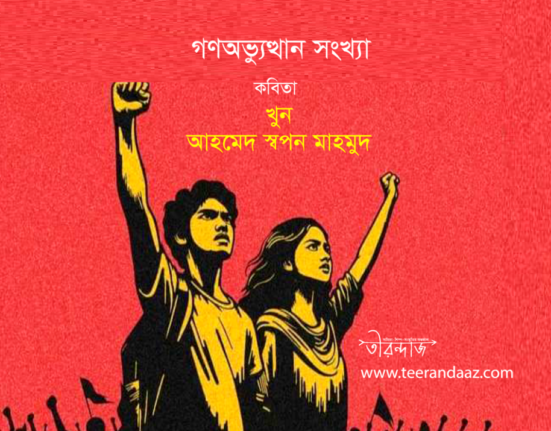
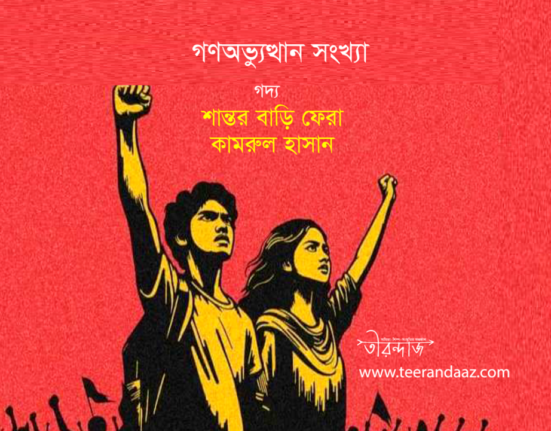
Leave feedback about this