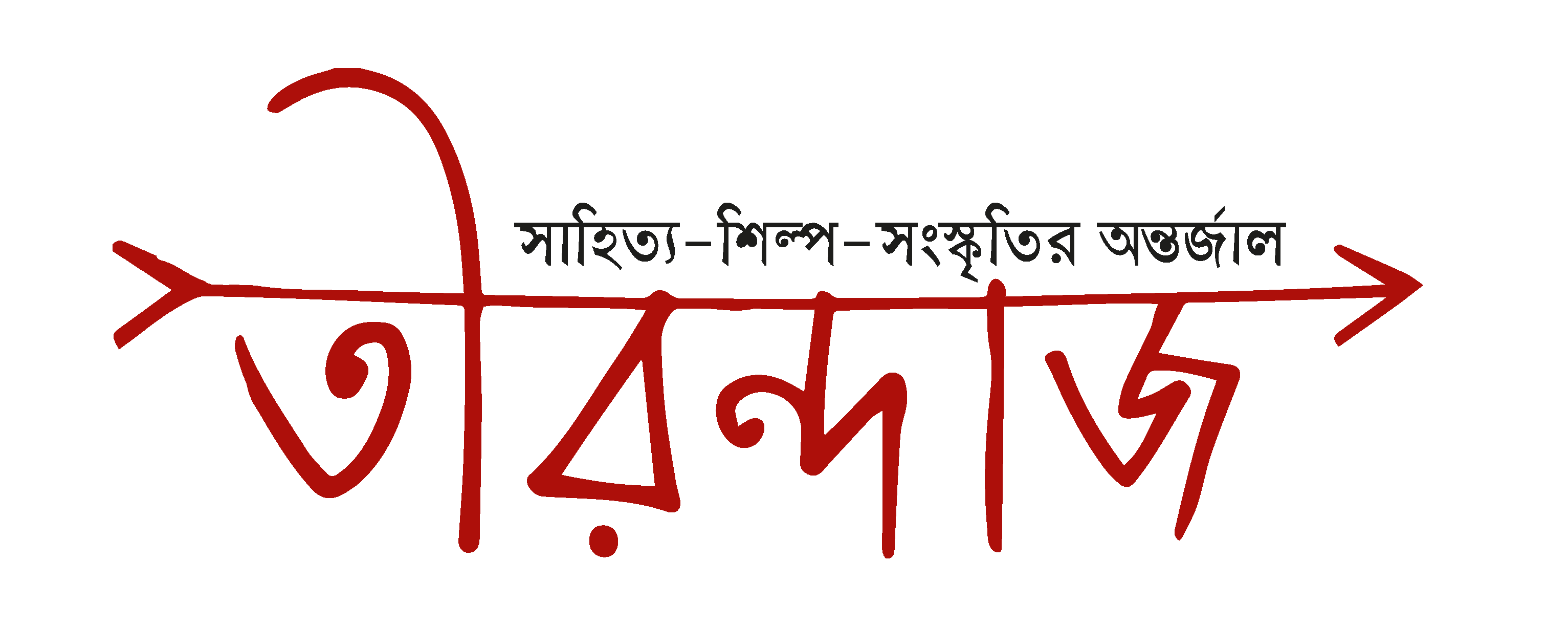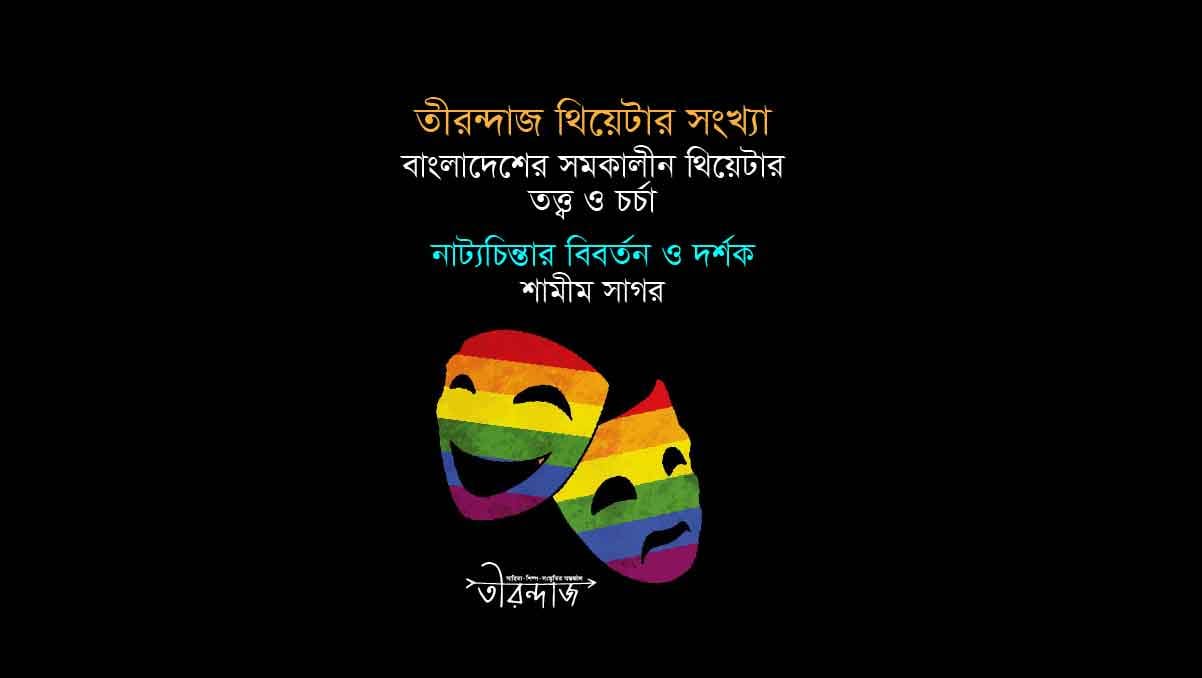বাংলাদেশ থিয়েটার
মানুষ গান-আবৃত্তি শোনে; মুকাভিনয় নৃত্য উপভোগ করে, যাদু-সার্কাস প্রদর্শনীতে যোগ দেয়, সিনেমা দেখে, যাত্রা দেখে, ছবির প্রদর্শনীতে যায়, থিয়েটারে যোগ দেয় – প্রধানত বিনোদনের জন্যে। বিনোদনের এসব উপাদানের মধ্যে থিয়েটার নিশ্চিতভাবেই বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন কৃত্য হতে প্রথমে পারফরমিং আর্ট এবং এ থেকে ধীরে ধীরে থিয়েটারের উদ্ভব; এটি এখন আর অজানা নয়। থিয়েটারের উৎপত্তি লোকমানুষের কৃত্য থেকে, এটা স্বীকার করতেই হবে। কখনো ধর্মীয় কৃত্য আবার কখনো সামাজিক জীবন-কৃষিকেন্দ্রিক কৃত্য থেকে। গ্রিস, মিশরের থিয়েটারের ইতিহাস স্পষ্টভাবেই জানা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে এখনও বিতর্ক চলমান। বঙ্গভূমির থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে বড় বিতর্ক আছে।
বাঙালির থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। প্রথম মত অনুযায়ী এই বঙ্গদেশের নাটকের ইতিহাস কোনভাবেই সাম্প্রতিক নয়, বেশ পুরোনো। মিশরের ধর্মীয় কৃত্যনির্ভর ওসিরিস প্যাশন প্লে, সিরিয়ার তাম্মুস, গ্রিসের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারা ও দিওনুসুসের উৎসব থেকে উৎসারিত গ্রিক ট্রাজেডি, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটক, কৃষিকেন্দ্রিক শিবোৎসবকে ঘিরে রচিত বাংলা নাটক, সবখানেই মানুষের শ্রেণি নির্বিশেষে অংশগ্রহণের প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের শিবোৎসবকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত নাট্যক্রিয়া, বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রভাবিত ধর্মীয় জ্ঞানপ্রচারমূলক নাট্যচর্চা এবং এর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে আখ্যান-পালা পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বাঙালির নাট্যচিন্তা বা নাট্যচর্চার বিষয়টি ভিত্তি পেয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আনন্দ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই নাটক। বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতির পাশাপাশি নিজস্ব নন্দনশাস্ত্রও ছিলো, বঙ্গীয় জনপদের শিল্প নন্দনশাস্ত্র হলো চৈতন্য শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত উজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থ। সংস্কৃত কাব্য কিংবা নাট্যতত্ত্বের ভাবনা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র শিল্পতত্ত্ব ছিল বাংলাদেশে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ পরিবেশনায় এই শিল্পরীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ চর্যাপদের ১১ সংখ্যক পদে নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় এইরকম বর্ণনায় : “নাচন্তি বাজিল, গাওন্তি দেবী/ বুদ্ধনাটক বিষমা হোই…।”
বাংলায় নাট্যাভিনয় করে জীবন ধারণ করতো, এই ধরনের একদল লোকই ছিল, যাদের ‘নট-পেটিকা’ বলা হতো। নাটকের সাজসজ্জা একটি বাক্স/পেটিকায় ভরে নাট্যাভিনয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতো বলে তাদেরকে এই নামে ডাকা হতো বলে ধারণা করা হয়। চর্যাপদের ২০ সংখ্যক পদে কাহ্নপাদ এদের ‘নড়-এড়া’ বলে সম্বোধন করেছেন; যা এই নট-পেটিকা ছাড়া কিছু নয়। চর্যাপদে নাটক ও অভিনেতাদের উল্লেখ থাকার অর্থ হলো এরও আগে থেকে এই বাংলায় নাট্যচর্চা বিরাজমান ছিল। সে হিসেবে বাংলা নাটকের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের কাছাকাছি পুরনো।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, বাংলার নাটকের ইতিহাস কোনভাবেই ২ শ ৩০ বছরের পুরোনো নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী যারা বাংলাতে কর্মরত ছিল, তাদের অবসর সময়টা আনন্দময় করে তোলার জন্যই ১৭৫৩ সালে কলকাতায় ‘ওল্ড প্লে হাউস’-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। উচ্চপদস্থ সকল ইংরেজ এই উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক ছিল। এই ‘ওল্ড প্লে হাউস’-এ মূলত অ্যামেচার অভিনেতারাই অভিনয় করতো। এখানে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার একেবারেই ছিলো না, অভিনেতা কিংবা দর্শক কোনভাবেই না। এর প্রায় চারদশক পর হেরাসিম লেবেডেফ নামের এক রুশ ব্যক্তি বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার চর্চার অবতার হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ডোমতলা এলাকায় ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’ নামে এক নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজি নাটক ‘দ্য ডিজগাইজ’-এর অনুবাদ করেন ‘কাল্পনিক সংবদল’ নামে। বাঙালি অভিনেতারা এই নাটকে অভিনয় করেন এবং দর্শক হিসেবে সাধারণ বাঙালিদের থিয়েটার হলে প্রবেশের বাধা দূর হয়। উল্লেখ্য, সেই সময় ইংরেজদের অনুকরণে নিজেদের জীবনাচার পাল্টে নেয়া, তাদের সংস্কৃতিকে উন্নত সংস্কৃতি মনে করা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সংস্কৃতি-ধর্মকে গ্রহণ করাকে জাতে ওঠা বলে বিবেচনা করা হতো। তখন পাশ্চাত্য ঘরানায় প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চগুলোতে পাশ্চাত্য রীতিতে পরিবেশিত নাটক হয়ে উঠেছিল উচ্চরুচি আর বাঙালির নিজস্ব নাট্যক্রিয়া। যাত্রাগান-পালাগানসহ প্রচলিত সকল লৌকিক নাট্যই হয়ে গেল নিম্নরুচির সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। যা-ই হোক, ১৭৯৫ সাল থেকে বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার-চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুকরণে নতুন এক থিয়েটার চর্চা শুরু হলো। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি নাট্যজন এটা বিশ্বাস করে যে, লেবেদেফের হাত ধরেই বঙ্গদেশে থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই মত অনুযায়ী বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ২ শ ৩০ বছরের পুরনো ধরা হয়ে থাকে।
উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যক্রিয়ার চেহারা আর প্রায়োগিক কৌশল ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব থিয়েটারগুলোরও আলাদা আলাদা ব্যাকরণ থাকা উচিত। সেদিক থেকে পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সংজ্ঞায় বাঙালির থিয়েটারকে মূল্যায়ন করাটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। তবে এখনও আমাদের মানসিকতার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার ভূতটা চেপে বসে আছে। এখনও আমাদের কাছে মূলধারার নাট্যচর্চা হলো প্রসেনিয়ামকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যরীতির নাট্যচর্চা। এই নাট্যচর্চাকে ধরেই নির্দিষ্ট একটা দিকে আলোর ফোকাসটা ধরবার চেষ্টা থাকবে।
বাংলাদেশের নাট্যচর্চা : বিবর্তন
বাংলাদেশ অঞ্চলের প্রসেনিয়ামকেন্দ্রিক থিয়েটার চর্চার ইতিহাস কলকাতাকেন্দ্রিক থিয়েটার চর্চার কাছাকাছি। কলকাতায় যে থিয়েটার চর্চার শুরু ১৭৯৫ সালে, তার ঢেউ পূর্ববঙ্গেও এসে লাগে। বাংলাদেশের একশ বছরেরও বেশি পুরোনো নাট্যমঞ্চগুলো তারই প্রমাণ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্বেও এই ভূখণ্ডে থিয়েটারচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৮৮ থেকে ১৯৭১ সময়কালে বাংলাদেশ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নাট্য সংগঠন গড়ে ওঠা এবং অনিয়মিত হলেও ধারাবাহিকভাবে নাট্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কিন্তু উদ্দীপনার বিষয়। এই সময়কালে গড়ে ওঠা নাট্যদলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইলিশিয়াম থিয়েটার, ঢাকা (১৮৮৮), ক্রাউন থিয়েটার, ঢাকা (১৮৯০), ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার, ঢাকা (১৮৯৭), খুলনা থিয়েটার (১৯০০), করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল (১৯১১), দিনাজপুর নাট্য সমিতি, দিনাজপুর (১৯১৩), নবরূপী, ড্রামা সার্কেল, ঢাকা (১৯৫৬), দিনাজপুর (১৯৬৩), শিখা সংসদ, রংপুর (১৯৬৬), নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা (১৯৬৮), খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার, বরিশাল (১৯৬৯)। এর বাইরেও নিশ্চয়ই আরও কিছু নাট্যদল গঠিত হয়েছিল ওই সময়। শতবর্ষী নাট্যমঞ্চগুলোর মধ্যে লালমনিরহাটের এম টি ইনস্টিটিউট, পাবনার বনমালী ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়ার পরিমল থিয়েটার, বরিশালের অশ্বিনী কুমার টাউন হল, বগুড়ার এডওয়ার্ড ড্রামাটিক মঞ্চ, নীলফামারীর ডোমার নাট্য সমিতি মঞ্চ, কুমিল্লার টাউন হল, মালনীছড়া চা বাগান নাট্যমন্দির, ময়মনসিংহ টাউন হল, রাজশাহীর ললিতমোহন মিত্র নাট্যমঞ্চ, খুলনার নাট্য নিকেতন মঞ্চ অন্যতম। উৎসব-পার্বনে কিংবা বাৎসরিক আয়োজনে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শৌখিন নাট্য সংগঠনে আর পাড়ায় পাড়ায় মঞ্চ নাটক চর্চার ইতিহাস শতবছরেরও পুরোনো (পাশ্চাত্যের অনুকরণে মঞ্চ নাটক চর্চার ক্ষেত্রে)।
১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এই পাশ্চাত্য রীতির থিয়েটারচর্চা কিন্তু থেমে থাকেনি। ভাষার প্রশ্নে ’৪৭ থেকেই বাঙালি সংগ্রাম শুরু করে, ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো এবং বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরো জাগ্রত করে তুলতে কবি-সাহিত্যিকেরা কলমযুদ্ধ শুরু করলেন। এই আন্দোলনের ফলে একঝাঁক নাট্যকারও পেয়ে যাই আমরা সেই সময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে নাট্যর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় ’৪৭-এর পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে। প্রথিতযশা নাট্যকারদের সূতিকাগারও কিন্তু এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রগতিশীল আদর্শে চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে ‘প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ’। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ রচিত ‘এবারের সংগ্রাম’ মঞ্চায়িত হয়। এর পরপরই ২৪ মার্চ চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। যুদ্ধকালের এ দুটি নাটক চট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে পরিবেশিত হয়েছে বলে জানা যায়। আমাদের বিভিন্ন সময়ের সংগ্রাম এবং আন্দোলনে থিয়েটার সব সময়ই তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে, ভূমিকা রেখেছে।
১৯৭১ পরবর্তী সময়ে আমাদের পাশ্চাত্য ঢঙের থিয়েটার চর্চার বিষয়টি স্পষ্ট। একটা বাঁক নিয়েছিল। ‘নাটক-করিয়ে’ কিছু নাট্যজন ১৯৭১ সালে কলকাতায় থাকার সময় গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চা প্রত্যক্ষ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে থিয়েটার নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা, এর প্রভাবে তা আরও পোক্ত হয়ে যায়। তারা দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখবার পাশাপাশি স্বাধীন দেশে নতুন রূপে নতুন উদ্যমে থিয়েটারচর্চা শুরু করবারও স্বপ্ন দেখেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এই নাটক পাগল মানুষগুলো গ্রুপ থিয়েটার চর্চা শুরু করলেন। অবশ্য স্বাধীনতার পূর্বেই বারোয়ারি কিংবা উৎসব পার্বনে বা বাৎসরিক থিয়েটার চর্চার বাইরে যেয়ে ১৯৫৬ সালে পেশাদারত্বের সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার লক্ষ্যে ড্রামা সার্কেল-এর সৃষ্টি হয় এবং ১৯৬৮ সালে গঠিত হয় নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়। তবে নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটার চর্চাটা স্বাধীনতা উত্তর সময়েই শুরু হয়।
স্বাধীনতা পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনী হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শুরু হয় দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনী। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব মিলনায়তনে চট্টগ্রামের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার দল ‘থিয়েটার ৭৩’ জহির রায়হান রচিত এবং অধ্যাপক জিয়া হায়দার নির্দেশিত ‘ম্যাসাকার’ দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চায়ন করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ঢাকাতে দর্শনীর বিনিময়ে নাটকটি মঞ্চায়ন করে। এটি বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ইতিহাসের অনন্য ঘটনা। তবে মনে রাখা জরুরি, আমাদের নিজস্ব নাট্যরীতির যাত্রা কিন্তু বহু পূর্ব থেকেই দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। লোকজ নাটকগুলোর বেশিরভাগই বায়না করে অর্থের বিনিময়ে প্রদর্শিত হতো বিভিন্ন উৎসবে-অনুষ্ঠানে, যা এখনও অব্যাহত আছে।
এটা সত্যি যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একমাত্র নাটকের ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য এসেছে সবচেয়ে বেশি। নাটকের আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে, নির্মাণকৌশলে, মঞ্চায়নে, মঞ্চনির্মাণের ক্ষেত্রে ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের ৫৩ বছরের থিয়েটারের ইতিহাসে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিকেন্দ্রিক একাডেমিক থিয়েটার চর্চা, পরিবেশবাদী থিয়েটার মুভমেন্ট, স্টুডিও থিয়েটার, রেপারটরি থিয়েটার। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।
স্বাধীনতার আগে মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নূরুল মোমেন, সাঈদ আহমদ, আশকার ইবনে শাইখ, কল্যাণ মিত্র, অন্নদামোহন বাগচী, ইবনে শায়ের-এর মতো নাট্যকারেরা এই বঙ্গের নাট্য রচনার ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আর স্বাধীনতা পরে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নাটক রচনার মাধ্যমে নিজের দেশের চেহারা ফুটিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আলী যাকের, মমতাজ উদ্দিন আহমদ, আসাদুজ্জামান নূর, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসনাত আবদুল হাই, আল মনসুর, এস এম সোলায়মান, সৈয়দ মাহিদুল ইসলাম, তারিক আনাম খান-সহ অনেকেই। তেমনি লোকবাংলার শেকড় অনুসন্ধান করে বাংলা নাটককে শেকড়ের সাথে যুক্ত করতেও সচেষ্ট হয়েছেন সেলিম আল দীন। আরও যাদের নাটকে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তারা হলেন- মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক, সামিনা লুৎফা নিত্রা, সাধনা আহমেদ, আনন জামান-সহ অনেকেই।
গত ৫৩ বছর ধরে নাটক রচনা, নির্দেশনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় মঞ্চায়িত ‘বাকি ইতিহাস’ থেকে আজকের ঢাকা থিয়েটারের ‘প্রাচ্য’, সেলিম আল দিনের ‘মুনতাসির ফ্যান্টাসি’ থেকে ‘স্বর্ণবোয়াল’ রচনার ধারাবাহিক যে পরিবর্তন, মামুনুর রশিদের শুরুর দিকের ‘ওরা কদম আলী’ থেকে বর্তমানের ‘রাঢ়াঙ’ পর্যন্ত নাট্য রচনা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে চিন্তনদর্শন-প্রয়োগের যে বাঁকগুলো ঘটে গেছে; তাতে বর্তমানে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের একটি স্পষ্ট চেহারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রবণ ও দর্শনগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের থিয়েটার হিসেবে তা প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমানের থিয়েটার চর্চায় তরুণদের সঙ্গে প্রবীণদের একটি বিভাজন-রেখা সুষ্পষ্ট। তরুণদের চিন্তা-ভাবনা এবং প্রকাশভঙ্গি একবিংশ শতকের শুরু থেকে পাল্টে গেছে। তরুণেরা নানা নিরীক্ষায় ফেলছে নিজেদের কাজকে। ১৯৭১ পরবর্তী নতুনভাবে শুরু হওয়া নাট্যচর্চা যেভাবে এগিয়েছে, ক্রমাগত চর্চার ফলে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তরুণেরা তা থেকে এগিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার চেষ্টা করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বীকারও করছে পুরোনো চর্চাকে। আর সে জন্যই অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, তরুণেরা নাটক রচনা কিংবা নির্দেশনার কথা যেভাবে ভাবছে, প্রবীণেরা বেশিরভাগই সেসব পছন্দ করছেন না। এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই রয়েছে। তরুণদের মধ্যে একদল রয়েছে বুঝেশুনে থিয়েটারটা করবার চেষ্টা করছে। এদের কাজ প্রশংসিতও হচ্ছে, সমালোচিতও হচ্ছে। আবার একদল রয়েছে, না-বুঝেই ভাবাবেগের জায়গা থেকে কিংবা নিজেকে প্রকাশ করবার ইচ্ছে থেকেই থিয়েটার করছে। সেই থিয়েটার দর্শনগত ও পরিবেশনাগত জায়গা থেকে কোন বিশেষ কিছু প্রকাশ করে না। ‘পারাপার’, ‘খনা’, ‘ভগবান পালিয়ে গেছেন’, ‘স্বর্ণবোয়াল’, ‘মানগুলা’, ‘তিনকড়ি’, ‘নিত্যপুরাণ’, ‘আদম সুরত’, ‘চন্দ্রাবতী কথা’, ‘দমের মাদার’, ‘নিশিমন বিসর্জন’ ইত্যাদি প্রযোজনা গত বিশ বছরের মধ্যে নির্মিত এই প্রযোজনাগুলোর নাট্যকার কিংবা নির্দেশক নবীন বা তরুণ। এই প্রযোজনাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এই ধারণা আরও পোক্ত হয়ে উঠবে যে, বর্তমানে নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে চিন্তাগত জায়গায় একটা বড় পরিবর্তন এসেছে।
মহড়ার মাধ্যমে নাট্য-নির্মাণ, নাট্য প্রদর্শনীর উপর নাটকের সফলতা নির্ভর করে না। এখানে আকর্ষণের বিন্দু হিসেবে থাকে দর্শক। দর্শকদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই একটি নাটকের সফলতা নির্ভর করে।
বাংলাদেশের নাট্যদর্শক
যারা নাটক দেখতে মিলনায়তনে প্রবেশ করেন তারাই দর্শক। একটি মৌলিক প্রশ্ন এসে যায়, দর্শক কেন নাটক দেখেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেই কিন্তু একটি নাট্যদল সঠিক নাটকটি বেছে নিয়ে দর্শকনন্দিত নাট্যনির্মাণ করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ দেয়া যাক। কলকাতাতে একই সময় উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক মঞ্চস্থ হতো। বাদল সরকারের নাটক মঞ্চস্থ হতো কার্জন পার্ক, রবীন্দ্র সদনের তিন তলার হল ঘরে; এখানে হাতেগোনা কিছু দর্শক ছাড়া দর্শকদের বড় অংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকেও দর্শকদের অবস্থা প্রায় একই ছিল। কিন্তু উৎপল দত্তের নাটক কোনদিন দর্শক আনুকূল্য হারায়নি। কলকাতার যে থিয়েটার হলে উৎপল দত্তের দল পিএলটির নাটক হয়েছে, হাউজফুল হয়েছে। বহুরূপী নাট্যদলের নাটকও দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। কেন এই পার্থক্য ঘটেছে? মৌলিক নাটক রচনা বা নাটক অনুবাদ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে দর্শকদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করাটা যেমন জরুরি। তেমনি নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেশজ চেহারায় নাটকটির প্রদর্শন জরুরি। এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটলেই সেই নাটক দর্শক গ্রহণ করবে নিশ্চিতভাবে।
থিয়েটারের অপূর্ণ থেকে যায় যদি দর্শকের উপস্থিতি না থাকে। বাংলাদেশে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনী (প্রায় প্রতিদিন) রাজধানী ঢাকাতেই হয়ে থাকে। এই শহরটার জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। নাটক প্রদর্শিত হয় দুটি স্থানে – মহিলা সমিতি এবং শিল্পকলা একাডেমিতে; মঞ্চসংখ্যা চার। দুই কোটি মানুষের শহরে প্রতিদিন গড়ে চারশত টিকেট বিক্রি হয় নাটক দেখবার জন্যে। হিসেব কষলে দেখা যায় সব মিলিয়ে বছরে মাত্র দেড় লাখের কাছাকাছি সংখ্যার টিকেট বিক্রি হয়; ভাবা যায়? এই হিসাবটা এই মুহূর্তের নয়। কিছু দিন আগের। তো দুই কোটি মানুষের শহরে মাত্র দেড় লক্ষ টিকেট বিক্রি হয়; জনসংখ্যার হিসাবে শতকরা এক ভাগেরও কম। কিন্তু মোট দর্শক সংখ্যাও কি টিকেট বিক্রির সমান? না। নাট্যজন সৈয়দ জামিল আহমেদের হিসাবে মাত্র পাঁচ হাজারের মতন দর্শক ঘুরে-ফিরে নাটক দেখতে আসেন। এই সংখ্যাটা কিছুটা এদিক ওদিক হবে। কেননা, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কিছু দর্শক আছে, কিছু পুশিং সেলের মাধ্যমে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজন দু’একবার নাটক দেখতে আসেন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা আট থেকে দশ হাজারের ওপরে যাবেই না। ভয়াবহ অবস্থা। একটি সভ্য শহরের জন্য এটা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। এই অবস্থা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যায়, থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তারা থিয়েটারটারের দর্শক বৃদ্ধি করতে অসমর্থ হয়েছেন কিংবা তারা এমন থিয়েটার নির্মাণ করছেন যেটা দর্শক গ্রহণ করছে না। আরেকটি কারণ হতে পারে। একই মঞ্চে ভালো নাটকের সঙ্গে দর্শকের কাছে অগ্রহণযোগ্য নাটকেরও মঞ্চায়ন হচ্ছে। নতুন দর্শক, কোন একজন যখন একটি মঞ্চ নাটক দেখে খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, যদি তার নাটকটি ভালো না লাগে বা নাটকটি যদি তার কাছে অবোধ্য হয়, তাহলে আবার মঞ্চ নাটক দেখবার ইচ্ছেটা তার মরে যায়।
দর্শকের থিয়েটার দেখতে আসা না-আসার দায়টা নাট্যদলের উপরও বর্তায়। কেননা, থিয়েটারটা শেষ পর্যন্ত দর্শকদের জন্যই মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আরো বেশি দর্শক যেন একটি নাট্যদলের নাটক দেখতে আসে, আরো বেশি মানুষের কাছে যেন থিয়েটারের বার্তা পৌঁছে যায়, সেদিকে লক্ষ রেখে দর্শকনন্দিত হবার মতন থিয়েটার প্রযোজনা নির্মাণের দায়টা নাট্যদলের উপরই থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো কোন দায় নিতে ইচ্ছুক নয়। এটি বাংলাদেশের থিয়েটারের অনেকগুলো ট্রাজেডির অন্যতম।
আমরা আরো দুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারি। এক – আমরা কি নাট্যদর্শক তৈরি করতে পেরেছি? দুই – বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে দর্শক কতটা বিবর্তিত বা সাবালক হয়েছে? তবে, আরো একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। দর্শকদের পছন্দ বদলে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাধারাও কি বিবর্তিত হয়েছে? উত্তরগুলো এমন যে, আমরা হয়তো হাতেগোনা কিছু দর্শক তৈরি করতে পেরেছি। কিন্তু ঢাকা শহরের জনসংখ্যা অনুযায়ী যত দর্শক হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি। তবে আরো একটা দিক রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে কিছু নিয়মিত দর্শক এখনও রয়েছেন, যারা থিয়েটারের শুভাকাঙ্খী হিসেবে রয়ে গেছেন। থিয়েটারকে ভালোবেসে যথাযথ সমালোচনা করেন, থিয়েটারের জন্যেই। থিয়েটার স্থির থাকে না। প্রতিদিনই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যায় থিয়েটার। আর দর্শকও যেহেতু একজন অংশগ্রহণকারী, তাই তারাও থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে থাকেন। তবে নতুন দর্শকদের জন্য বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং। কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে, নবীন দর্শকদের জন্য সহজ কাহিনির প্রয়োজন। কিন্তু একটি সুলিখিত এবং সুনির্মিত নাটক পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নাট্যকর্মীদের দায়িত্ব হলো এমন নাটক তৈরি করা যা একইসঙ্গে বিনোদন ও চিন্তার খোরাক জোগায়। এরকম নাটক আলোচনা এবং সমালোচনামূলক সম্পৃক্তিকে উৎসাহিত করে। দর্শকদের সমালোচনামূলক চিন্তাধারা তৈরি হয় এবং এটি ক্রমে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।
বাংলাদেশের নাট্য দর্শকেরা সাবালক হয়ে উঠেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আমাদের দর্শকদের সাবালকত্ব আসেনি। একটি নাটক দেখবার পর দর্শকেরা বুঝে না-বুঝে থিয়েটার সংশ্লিষ্টদের বিভ্রান্ত করেন অযথা প্রশংসা করে এবং সঠিক সমালোচনা করতে না পেরে। এই দায়ের একটা অংশ থিয়েটার করনেওয়ালাদের উপরও বর্তায়, তারা সমালোচনার চাইতে প্রশংসাই শুনতে চান। তবে এটা সত্য যে, বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের দর্শকরা প্রকৃতপক্ষে বদলাচ্ছেন। তাদের পছন্দ এবং প্রত্যাশা নাট্য প্রযোজনার সীমানাকে আরও বিস্তৃত করছে। যদিও সমালোচনামূলক চিন্তাধারা ধরে রাখাটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, তবু নতুনকে গ্রহণ এবং দর্শকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার ইচ্ছা নাট্যচর্চার ইতিবাচক দিক। বিবর্তনশীল দর্শকদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক শিল্পীসুলভ মতপ্রকাশ এবং সামাজিক মন্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে পারে।
শামীম সাগর : নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা।