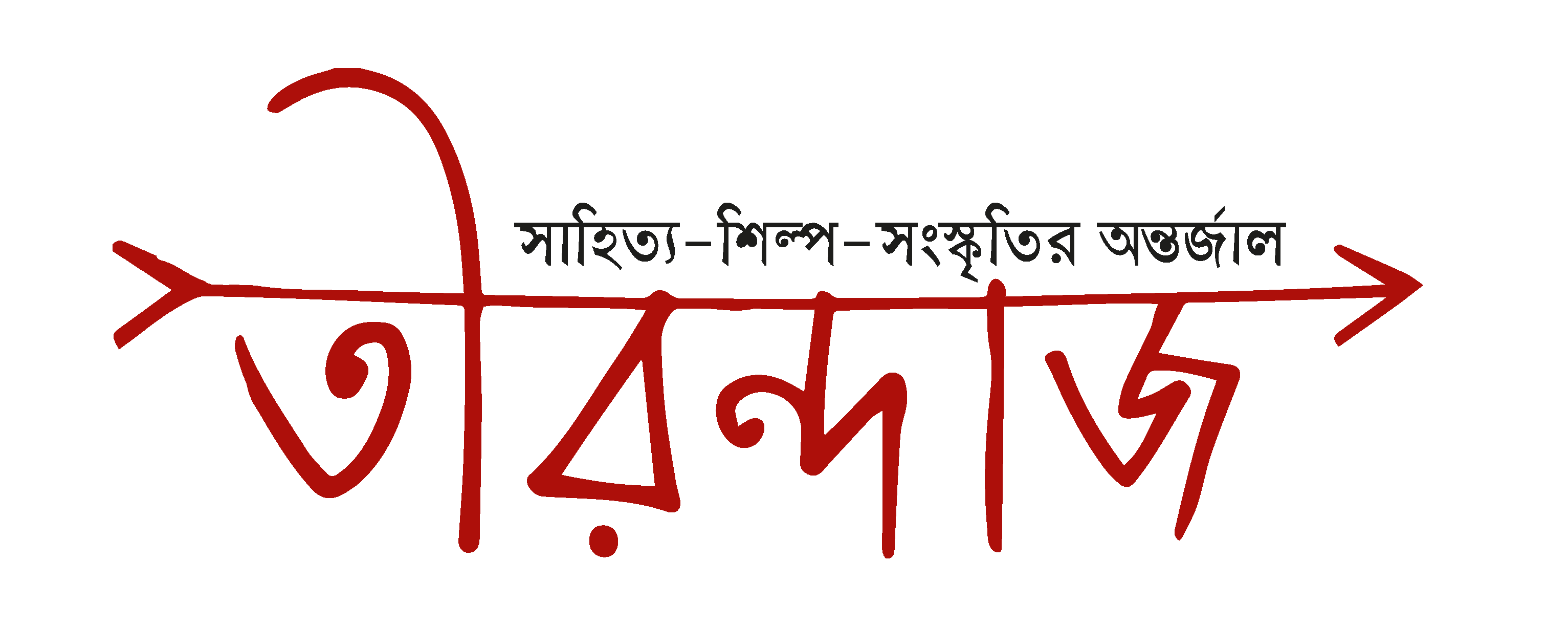‘নিছক বৈঠকী’ শিরোনামে এই জার্নালধর্মী লেখাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে
১. সুবিমল মিশ্র ও ‘প্রথাবিরোধিতা’
পরিণত বয়সে (৮০) বিদায় নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথাবিরোধী লেখক সুবিমল মিশ্র। মাত্র পাঁচমাস আগে (ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৩) তিনি দেহত্যাগ করেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন, ভাষা ও আঙ্গিকের ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য এবং লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম সযত্নে এড়িয়ে দুই বাংলার পাঠক এবং লেখকদের কাছে পৌঁছানোর কৃতিত্বে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের প্রায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। স্রোতের বিপরীতে, প্রথাবিরোধিতায় জীবদ্দশায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তিতুল্য। শুধু ‘প্রথাবিরোধিতা’ নয়, তাঁর নামের আগে ‘প্রতিষ্ঠান বিরোধি’তার তকমাও বেশ জেঁকে বসেছে। ‘প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায়’ তাঁর খুব নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গের আরেকজন শক্তিমান লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (প্রয়াত) একদা তাঁকে ‘লেখকদের লেখক’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারণও ছিল এর নেপথ্যে। দীর্ঘ লেখক জীবনে কলকাতার নামি পত্রিকা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে তিনি সচেতনভাবে পরিহার করেছেন, পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর কাছে ঘেঁষবার সাহস করে নি, এমনকি শেষ জীবনে নামজাদা প্রকাশক হারপার কলিন্স থেকে যখন তাঁর অনুদিত গল্পসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তাতেও তিনি বাদ সেধেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বার্থে লিটল ম্যাগাজিনের ফসল। সাক্ষাৎকারে সোজাসাপটা বলেছেন : ‘কমার্শিয়াল পত্রিকার আমন্ত্রণ আমার লেখকসত্তার অসম্মান ঘটায়।’ কলকাতা বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে নিয়মিত টেবিল পেতে নিজের প্রকাশিত বই সাজিয়ে বসে যেতেন। মেলায় এলে এখানেই গুণগ্রাহীরা তাঁর সাক্ষাৎ পেত। উস্কোখুস্কো চুল, বেখেয়ালে মুখ জুড়ে ছড়িয়ে-পড়া দাড়ি-গোঁফ, কাঁধ থেকে ঝুলছে কাপড়ের ব্যাগ, অবিরাম সিগ্রেট ফুঁকছেন – মোটা দাগে এই ছিলো ‘বিদ্রোহী’ লেখকের প্রতিকৃতি।
১৯৬৯-এর জুনে তাঁর প্রথম গল্প ‘হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি’ প্রকাশের পর পাঠক মহলে তুমুল সাড়া জেগেছিল। সেই গল্প জমজমাট কোন কাহিনি নয়, কতগুলো দৃশ্য মাত্র, মনে হবে তিনি সেগুলোকে একের পর এক জোড়া লাগিয়েছেন শুধু। শুধু কি জোড়া লাগানো, তাতে যে তিনি জাদু ছিটিয়ে দিয়েছেন সেটাই হলো আসল কথা! হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের লাশটি ভেসে যাচ্ছে, সেই লাশের সৎকার কিংবা সদগতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু সেই প্রান্তিক নারীর অপমৃত্যুর আড়ালে লুকানো যে কাহিনি তার নির্যাসটুকু উপজীব্য করে সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় যা লেখা হয়েছিল-তাতে ইঙ্গিতে সে-সময়কার গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই গল্পে বিধবা বৌয়ের সেই লাশ শতগুণে শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছিল বৌটির মৃত্যুর পর। কিছুতেই লুকানো যায়নি সে-লাশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র – পথেঘাটে, বাড়ির উঠোনে; মেয়রের অফিসও বাদ পড়েনি। এমনকি বিদেশ থেকে তৈরি করে আনা সোনার গান্ধীমূর্তিকে বিমানবন্দরে বরণ করে আনতে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর সহচরদের সামনে অলঙ্ঘ্য প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া। বিমান থেকে নামিয়ে আনার পর, বাকশো খুলে সোনার গান্ধীমূর্তি একনজর দেখার জন্য সবাই যখন ঝুঁকে পড়েছেন, তখন কি হলো? লেখকের ভাষায় : “সকলে সমবেত চমকালেন, নাকে রুমাল দিলেন এবং বুঝতে পারলেন হারান মাঝির বৌয়ের মড়া না সরালে সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল পাওয়া যাবে না।’’ লেখকের কলম এখানেই থেমে গেল বটে, কিন্তু তখুনি যেন পাঠকের মনে উঠে এলো নতুন গল্প। আর ভেঙে পড়লো পাঠকের গল্পপাঠের চিরাচরিত অভ্যস্ততাও। সেদিন বাংলা গল্পে এমন একটা নতুন ছাঁচ এনে দিয়েছিলেন সুবিমল মিশ্র যাতে চিরাচরিত স্টোরি-টেলিং অনুপস্থিত, তাতে গল্পের সনাতন কাঠামো খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়। বরং গল্পের নামে তিনি যেন পাঠকের সামনে ঠেলে দেন একটুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, নিজে পোড়েন আবার পাঠককেও পোড়ান। আজীবন সেই অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সুবিমল মিশ্র। ক্ষোভ, উদ্বেগ, প্রতিবাদ ও ঘৃণার তপ্ত লাভা যেন গড়িয়ে নামছে তাঁর রচনার গা বেয়ে। তাঁর রচনা পড়তে গিয়ে শিরদাঁড়া সোজা রাখতে হয়!
কি আছে তাঁর লেখায়? এককথায় চলমান যে সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ শাসন-শোষণ-বৈষম্য-বঞ্চনায় জীবন্মৃতের জীবন যাপন করে চলেছে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিনিয়ন্ত্রিত যে প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের বুকের উপর চেপে বসে নিয়ত মানুষের হাড়-মাংস চুষে নিচ্ছে, প্রতিকার ও প্রতিরোধহীন সেই মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাও আবার আধাআধি কিংবা মেকি নয়, নয় লোকদেখানো-একেবারে সরাসরি ও সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল তাঁর সেই পক্ষাবলম্বন। খুব সহজ নয় সে-কাজ, নিজের লড়াই জারি রাখতে গিয়ে সুবিমল মিশ্র আগে নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন-গোপন ও প্রকাশ্য যতরকম শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে পারেন একজন লেখক তার সবক’টি থেকে নিজেকে মুক্ত করে এনে লড়াইয়ে নেমেছেন। তারই একটি সবধরনের প্রতিষ্ঠান-বর্জন। আমৃত্যু লেখা প্রকাশের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে গেছেন, পরিহার করেছেন প্রচার-প্রচারণা, খ্যাতি ও পুরস্কারের মোহ।
বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত রবীন্দ্রত্তোর যুগে, বঞ্চিত-লাঞ্চিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন-এমন লেখক দুর্লভ নয়। লেখার বিষয়বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রচলিত প্রথা ভেঙে সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত হয়েছেন এমন লেখক আরও আছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথার’ কথা বলা যায়, সমরেশ বসু কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর নামোল্লেখ করা যায়। কিন্তু সুবিমল মিশ্র ছিলেন এর শীর্ষবিন্দু। আজকাল, এমনকি দুই বাংলার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা যখন অনেকখানি ফ্যাশনে রূপ পেয়েছে, সেই কপট কলিকালে তিনি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে তাঁর আজীবনের সাধনায় রূপ দিয়েছিলেন, ক্রমান্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রতীক। এ-ক্ষেত্রে ‘সফলতা’ (!) তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে ভেবে তিনি সং শয় জারি রেখেছেন এই বলে : “আমি যদি সফলতা পাই তার মানে হলো আমি এমন কিছু করছি যা তত নতুন নয়। নতুন কিছু করলে সফলতা সহজে আসে না।” এই সংশয় আজীবন তাঁকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখেছে, একমুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হতে দেয়নি।
তাঁর সম্পর্কে পড়তে গিয়ে যদ্দুর জানতে পেরেছি, এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল তাঁর। দেশি-বিদেশি সাহিত্যে তাঁর বিপুল পঠনপাঠন ছিল, এমনকি ইউরোপীয় ও মার্কিনী সাহিত্যের হালনাগাদ খোঁজখবর রেখেছেন নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমিয়ভুষণ মজুমদার ও কমলকুমার মজুমদারের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে খোঁজ পাওয়া যায়। বিদেশি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিল জেমস জয়েস, প্রাবন্ধিক হিসেবে পছন্দ করতেন মিশেল ফুকোর রচনা। আবার নিরীক্ষাধর্মী ও সমান্তরাল চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্ম নিয়েছিল যৌবনের শুরু থেকেই। ফরাসি নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র আন্দোলনের পুরোধা জাঁ লুক গদারের চলচ্চিত্র দেখে তিনি নাকি পরিচালককে চিঠিও লিখেছিলেন, যার জবাব দিয়েছিলেন গদার। লুই বুনুয়েল, পাসোলিনি, আইজেনস্টাইনের ছবির ডিভিডির বিরাট সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। অতএব, বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক যে তাঁর প্রিয় হয়ে উঠবেন, এতে আর সন্দেহ কি! অনুমান করা অসঙ্গত নয়, তাঁর রচনায় যে রাশি রাশি চিত্র ও চিত্রকল্পের সমাহার আমরা লক্ষ করি, তা গদার প্রমুখের চলচ্চিত্র -বীক্ষণেরই ফল। তাঁর রচনায় মন্তাজ, জাম্প-কাট ও চেতনাপ্রবাহের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ তাঁকে ‘গদার অব লিটারেচার’ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বিপুল তাঁর রচনাসম্ভার, ২০ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর রচনা। নিজের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করার জন্য নিজের রচনাকে তিনি অ্যান্টি-গল্প, অ্যান্টি-উপন্যাস, অ্যান্টি-প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করতেন।
প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে তিনি নিজের অজান্তেই আরেক ধরনের ‘কাল্টে’ রূপ দিয়ে গেলেন কি না ! এ-প্রশ্নও তোলা যায়, তাঁর একগুঁয়েমি ও জেদ কি শেষাবধি একঘেঁয়ে হয়ে উঠছিল পাঠকের কাছে? তিনি কি পাঠকের মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। দিনে দিনে কি দুষ্পাঠ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর লেখা! আরও যে জরুরি প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর রচনার পাঠক কারা, কাদের চেতনায় আঘাত করতে তিনি কলম ধরেছিলেন! তাঁর প্রতিষ্ঠান-বিমুখতার লড়াইয়ের চরিত্র কতটা রাজনৈতিক, কতটা নৈতিক, কতখানি বিমূর্ত! যদ্দুর জানা যায়, তিনি কোন রাজনৈতিক দল, গ্রুপ বা সংগঠনভুক্ত হন নি, যেমনটা ছিলেন মাণিক, সমরেশ অথবা হালের অভিজিৎ সেন। তাঁর প্রতিরোধ একক। তাহলে কি এ প্রশ্নও উঠবে না – বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের এই একক বিদ্রোহ কতটা বাস্তবসম্মত, কতখানি ইউটোপিয়া! তাঁর প্রথা/প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার স্বরূপ অনুসন্ধান করে একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কি একান্ত জরুরি নয়?
অবশ্য একথা আমাদের মানতেই হবে হারানের বিধবা বউয়ের লাশ আজও আমরা সরাতে পারি নি! সুবিমল মিশ্রের বিদ্রোহ তাই আজো জারি আছে!
২. সেকালের পাঠক বনাম একালের লেখক
আমাদের একজন বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরুণ লেখকদের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন রেখেছেন। তাঁদের কাছে তিনি সবিনয়ে জানতে চেয়েছেন : তাঁরা যে দু’হাত ভরে গল্প-উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের বইয়ের রঙিন প্রচ্ছদপট ও নজরকাড়া বিজ্ঞাপনে আজ যে বইয়ের বাজার সয়লাব – এতে তাঁদের প্রস্তুতি কতটুকু, কি তাঁদের পঠনপাঠন ঘটেছে? তরুণ লেখকরা বাংলা ও বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কতটুকু খোঁজ রাখেন, গল্প ও উপন্যাস যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ এ-পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, সেসব কলাকৌশল আয়ত্তে আনতে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের আগ্রহ ও নিষ্ঠা কতখানি! এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করে বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক অতঃপর খোলামেলা ভাষায় তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন এভাবে : “কারো কারো লেখা পড়ে ধারণা করতে পারি, তারা মূলত এইসময়ে বাংলাদেশে যারা গল্প-উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের লেখা পড়ে গল্প-উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন। তাদের পঠনপাঠনের সীমা হয়তো গত ১৫-২০ বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের উপন্যাস ও ছোটগল্প। কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ঔপন্যাসিকদের কিছু লেখা পড়েছেন। কেউ পড়েছেন লাতিন আমেরিকার খ্যাতিমান কয়েকজন ঔপন্যাসিক এবং জাপানি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক মুরাকামি অথবা পাউলো কোহেলোর লেখা। সবই অনুবাদে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বাংলা ভাষায় লেখা চিরায়ত ক্লাসিক উপন্যাসগুলিও হয়তো কেউ কেউ পড়েছেন। কিন্তু সেটা খুব সামান্যই মনে হয়। তবে বিশ্বসাহিত্যের পঠনপাঠন যে অনেকেরই নেই, সেটা তাদের লেখা পড়েই বুঝতে পারি।” যাঁরা সাহিত্যের ধারাবাহিক বিকাশের খোঁজ রাখেন এবং একালের তরুণ লেখকদের গদ্য মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত হবেন। তবে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে, এমনকি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক সাহিত্য আলোচনার (সেমিনার/সাহিত্য আড্ডা) আয়োজন করা সম্ভব। এতে অধ্যাপকের পক্ষ ও তরুণ লেখকদের পক্ষের যুক্তি-তর্ক বিশ্লিষ্ট করা গেলে আমাদের সাহিত্যের জন্য তা লাভজনক হতো বলে আমার ধারণা।
তরুণদের চিরায়ত সাহিত্যের পঠন-পাঠনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে ক’দিন আগে আমার বিশ্বসাহিত্যের ‘বইপড়া কর্মসূচির’ একজন সিনিয়র কর্মীর সাথে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। সায়ীদ স্যারের (অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ) প্রতিষ্ঠিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির মাধ্যমে পরিচালিত দেশব্যাপী ‘বইপড়া কর্মসূচি’ নি:সন্দেহে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এর মাধ্যমে চিরায়ত সাহিত্যের গ্রন্থগুলো পড়ানো ও সেগুলো নিয়ে পাঠচক্রের মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা বহুদিন ধরে চালু আছে। কিন্তু -এই কর্মসূচি যুবমানসের রুচি গঠনে অথবা এমনকি লেখক তৈরিতে কতটা ভূমিকা রাখছে, তা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা দাবি রাখে। সেদিন আমার পরিচিত সেই কর্মী কথাপ্রসঙ্গে তাঁর হতাশা ব্যক্ত করলেন। চিরায়ত সাহিত্যের ঢাউস বইগুলো যে তরুণদের আর নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে না, সেই দুর্দশার কথা তিনি ফিসফিসিয়ে কিন্তু অকপটে আমার কাছে স্বীকার করলেন। আবছা আলোয় তাঁর মুখ বিমর্ষ দেখাল। তিনি আরো বললেন, পাঠচক্রের আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন যে-শিক্ষকরা খোদ তাঁদের আগ্রহেও ঘাটতি পড়েছে। চিরায়ত সাহিত্যের পাঠকরা আজকাল বরং ইন্টারনেটপ্রসূত কনটেন্টে বিভোর। তাঁদের সময়ের একটা বড় অংশ দখলে নিয়েছে মুঠোফোনের চটকদার স্ক্রিন। তলস্তয়ের ‘আন্না ক্যারেনিনা’/ ‘রেজারেকশন’, দস্তইয়েফস্কির ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ কিংবা তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ কী মাণিকের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ পড়বার সময় কোথায় তাঁদের? এক পাঠক তো একবার আমার কাছে অনুযোগের (কিংবা বিরক্তি) সুরেই জানতে চাইলেন-গল্প উপন্যাসে এত খুঁটিনাটি (ডিটেলস) লেখার দরকারটা কি ছিল তাঁদের? তিনি বরং সুপারিশ করলেন, এইসব খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে স্রেফ কাহিনীটুকু রেখে এই উপন্যাসগুলোর বরং একটা করে ‘সংক্ষেপিত’ সংস্করণ ছেপে বাজারে আনতে পারেন প্রকাশকরা। আমি ভাবলাম, এই পাঠকের যুক্তি যদি আমাদের ‘আলোচিত তরুণ লেখকদের’ও (কথার কথা বলছি) প্রভাবিত করে, তাহলে তা আমাদের সাহিত্যের জন্য কতখানি লাভজনক হবে – সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উদ্বেগের, শঙ্কার।
তবে ভাবনার আর একটা দিক আছে। একজন লেখক আমাদের এই উদ্বেগের মুখে নীরব ও নিরুদ্বেগ থাকতে পারেন। তিনি এই নিশ্চিন্তিতে অবগাহন করতে পারেন যে, লেখক মানেই স্রষ্টা, তিনি স্বয়ম্ভূ, স্বাধীন। তিনি কী পড়বেন, কী লিখবেন এবং কী কলাকৌশল প্রয়োগ করবেন তাঁর লেখায়, তা তিনি নিজেই ঠিক করবেন। তিনি প্রকৃতিদত্ত (!) প্রতিভা, সেই কুমোর যাঁর ছাঁচ তাঁর একান্ত নিজস্ব! এ-ব্যাপারে অন্যের মাথাব্যাথা তাঁর সৃজনপ্রক্রিয়ার এখতিয়ারে নাক গলানোর শামিল। সত্যি কি তা’হলে লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে কোন অভিনিবেশ কিংবা অনুশীলনের দরকার নেই? এ-ব্যাপারে আমার কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ আছে।
সম্প্রতি আমি আমার বইয়ের প্রাচীন সংগ্রহশালায় হানা দিয়েছিলাম; এসময় যেন আপনা আপনি দুটি বই হাতে উঠে এলো। ষাট-সত্তর বছর আগে লেখা বাংলা সাহিত্যের দুটি পুরনো উপন্যাস – সমরেশ বসুর ‘বাঘিনী’ ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘প্রেমের চেয়ে বড়ো’। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর (আমার বিবেচনায়) বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখক এই দু’জন : সমরেশ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দুজনই পূর্ববঙ্গের সন্তান, দেশভাগের সূত্রে দেশান্তরী এবং গল্প-উপন্যাস রচনাই ছিল তাঁদের জীবিক। জীবিকার তাগিদে তাঁদের লিখতে হয়েছে অনেক রচনা, সমরেশ বসু তো কালকূট ছদ্মনামেও লিখেছেন অনেক গল্প-উপন্যাস। অনেক লিখতে হয়েছে বলেও হয়তোবা, এঁদের সব রচনাই যে কালোত্তীর্ণ হয়েছে এমন বলা যাবে না। যে দুটো উপন্যাসের কথা বলছি, এগুলো তাঁদের হিসেবে ধরতে গেলে ‘মাঝারি মানের’ রচনা, কেননা দুজনের হাতে রচিত হয়েছে কালজয়ী গ্রন্থ; আর আমারও পড়া হয়েছে যেমন সমরেশ বসুর (কালকূট) গঙ্গা, বি টি রোডের ধারে, শাম্ব, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন, মীরার দুপুর, সূর্যমুখী ইত্যাদি। গঙ্গা ও বারো ঘর এক উঠোন একাধিকবার পড়েছি। উভয়ের গল্পসমগ্রও পড়েছি। তবে অনেক আগের সংগ্রহে রাখা এই বই দুটি আমার আর পড়া হয়নি-বোধ হয় ‘মাঝারি মানের’ ভেবে ফেলে রেখেছিলাম। ‘বাঘিনী’ উপন্যাস অবলম্বনে কলকাতার পরিচালক বিজয় বসু চলচ্চিত্র বানিয়েছিলেন (১৯৬৮) যাতে ‘বাঘিনী’ চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়, সেই ছবিটাই শুধু দেখা ছিল আমার। মাঝখানে গড়িয়ে গেছে কয়েকটি বছর। কিন্তু সেদিন কী মনে হলো বই দুটো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আচমকা পড়তে শুরু করি – প্রথমে ‘বাঘিনী’, পরে ‘প্রেমের চেয়ে বড়ো’। দুটো মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার আয়োজন। কিন্তু নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে সে-পঠন এক বিরল অভিজ্ঞতা বটে। দুই লেখকের ‘মাঝারি মানের’ উপন্যাস হলে হবে কী, গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন, চরিত্রের টানাপোড়েন, প্রকৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার চিত্রায়ণে গল্পে বিশ্বাসযোগ্য ও নাটকীয় আবহ সৃষ্টি, ভাষার কারুকাজ এবং সর্বোপরি পাঠককে ধরে রাখার অসাধারণ দক্ষতায় কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি ও পারঙ্গমতা আমি যেন পুনঃআবিষ্কার করলাম। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উভয় লেখক যে বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, যেমন সমরেশ বসুর শ্রেণীবৈষম্যের পটভূমিতে সামাজিক বিপ্লবের ভাবনা (সমরেশ বসু কম্যুনিস্ট পাটির সদস্য ছিলেন) এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গভীর মনোজগতের অতল অনুসন্ধান; সমরেশ বসুতে যেমন বিস্তার, তেমনি নন্দীতে গভীরতা – দুই লেখকের বলা যায় ‘সিগনেচার’। এই উপন্যাস দুটিতেও তার কিছু কমতি হয়নি। পড়তে পড়তে এও নিশ্চিত হওয়া গেল, কেবল প্রকৃতিপ্রদত্ত সৃজনগুণে নয়, ব্যাপক শ্রম ও অনুশীলনের সুবাদেই তাঁরা এই সিদ্ধি অর্জন করেছেন।
সাহিত্যসিদ্ধি যে খুব সহজ কথা নয়, কেবল এটুকু বলার জন্যই ব্যক্তিগত পাঠ-অভিজ্ঞতার এই বয়ানটুকু টেনে আনতে হলো। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আলোচিত ও আপন ঘেরটোপে তৃপ্ত তরুণ লেখকদেরও মনে করিয়ে দেয়া যে, বাংলা কথাসাহিত্য (দুই বাংলা মিলে) আজ যে শক্ত জমিনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আত্মস্থ করে, জেনে বুঝেই আমাদের এগুতে হবে, অন্যথায় তা হবে উটপাখির বালুতে মুখ গোঁজার সামিল।