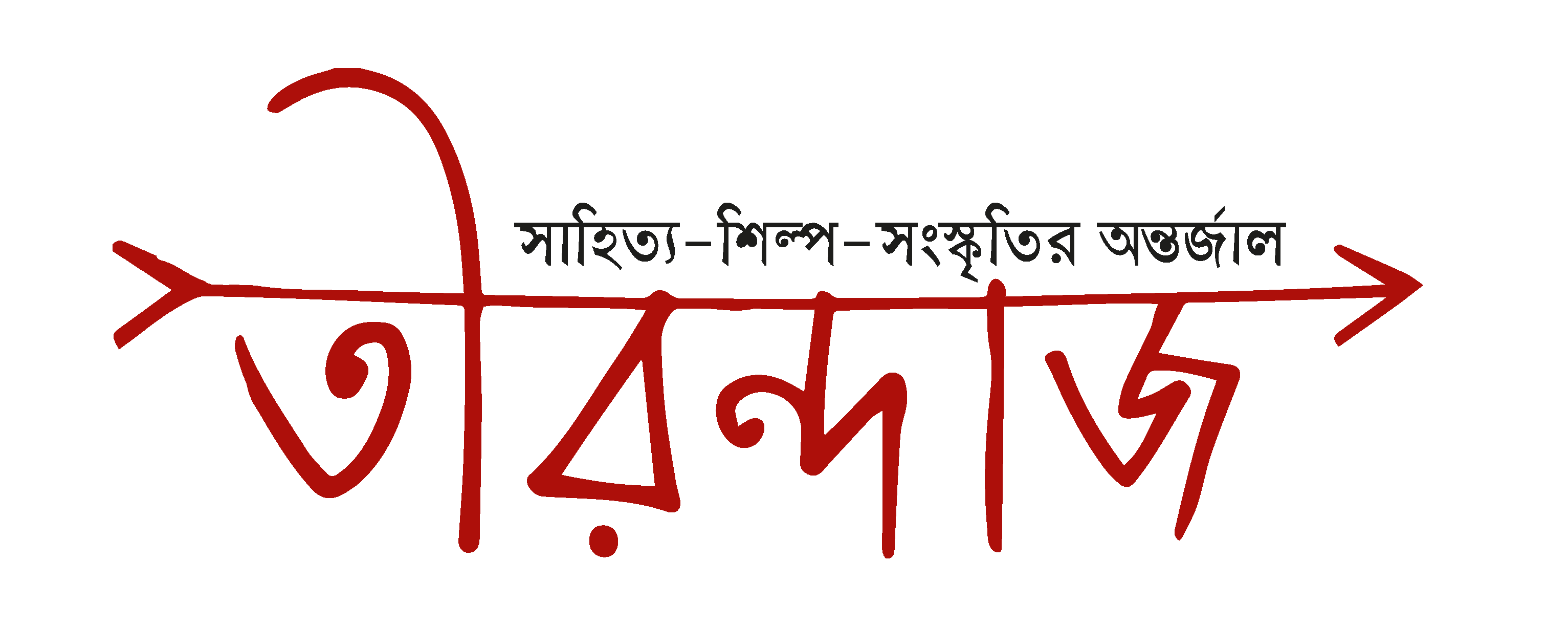বাপের বয়সী বৃদ্ধকে পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করতে দেখে সুরাইয়া বিব্রত হয়ে দ্রুত দূরে সরে যান। লোকটির বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে। চোয়াল-ভাঙা শ্রমক্লান্ত মুখ। কাঁচাপাকা চুলদাড়িতে এলোমলো চেহারা। কতকাল দাড়িতে ক্ষুর, চুলে তেলজল পড়েনি কে জানে।
লোকটি তবু মাটি থেকে মুখ তোলেন না। কান্নামিশ্রিত ভাঙা ভাঙা কণ্ঠ। মেঝের ওপর অশ্রুত কিছু কথা লেখা হতে থাকে। লেখেন সাধু গোমেজ।
মেয়েটি দরজার ফ্রেমেই দাঁড়ানো। ঘরের ভেতরে বা বাইরে কোনোটাই বলা যায় না। সুরাইয়া দেখেন মেয়েটি লম্বা। বেশ লম্বা। এ ঘরের দুজন নারী, সুরাইয়া এবং তার মেয়ে সুরঞ্জিতার চেয়ে লম্বা। গায়ে একটা ফুলস্লিভ টিশার্ট। নিম্নাঙ্গে লেগিনস। মুখটা একটা ওড়না পেঁচিয়ে অর্ধেক ঢাকা। এই মেয়ে ঐ ভাঙাচুরা দেহে গড় করে পড়ে থাকা বৃদ্ধ সাধু গোমেজের কন্যা? মুখ ঢাকা বলে বাপের সাথে চেহারার মিল বা অমিল বোঝার উপায় নেই। তবে সাধু লোকটি লম্বা বটে।
আপনি আমার মেয়েটাকে নিন। আমি ওকে দিলাম। আপনি নিন। কথা দিন, ওর সব দায়িত্ব নেবেন!
বাবা মাথা তুলেছে। তার গাল ভেসে যাচ্ছে পানিতে। মুখে পরিশ্রান্ত মালিন্য। তবে নিশ্চিন্ত একটা কোমলতা।
কী নাম? ভেতরে এসো।
আহ্বান শুনে মেয়েটি সহজ পায়ে সুরাইয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়।
আদুরী। ওড়নার আবরণের ভেতর থেকে জড়ানো আওয়াজ হয়ে বেরোয়।
কী নাম? মুখ খোল। কথা তো বোঝা যাচ্ছে না! সুরাইয়ার ভ্রুতে গিঁট পড়ে।
আদুরী। স্পষ্ট কণ্ঠ। সেই সাথে একটানে ওড়না খুলে হাতের মুঠোয়। ঝাঁকুনি লেগে চূড়ো করে বাঁধা চুলের খোঁপাও খুলে সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হল কালো গাবের মাঞ্জা দেওয়া একটা ঝাঁকি জাল ঝাঁপ দিল জলে।
সুরাইয়া আদুরীর দিকে চেয়ে বোবা হয়ে গেলেন। অপূর্ব রূপসী দীর্ঘাঙ্গী এক পঞ্চদশী গারো কিশোরী তার সামনে সটান দাঁড়িয়ে। মুখের চামড়া চুঁয়ে মাখন গলছে। সুরাইয়া থতমত খেয়ে বলেন, ওকে আমি নেব?
সুরাইয়াকে আদুরীকে নিতে হয়। আদুরীকে ওর বাবা নেবে না, গাঁ নেবে না, পাহাড় নেবে না। নদীও নেবে না। পাহাড়ের উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে আদুরীরা যখন ইশকুলে যায়, নদী পেরিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে বা বাজারে শাকসবজি বেচতে যায়, তখন ওদেরকে কেউ কেউ নিয়ে নেয়। কেউ কারো বাইকের পেছনে বসে উধাও হয়ে যায়, কেউ বা চুরি হয়ে যায়। সেটলার পাড়ার গাজা ফোঁকা যুবক কিংবা হিরঞ্চি গ্রুপের হাতে ওরা বেহাত হয়ে যায়। পরে কোনো উপত্যকায় কলার ঝোপে বা বাঁশবনে দলিতমথিত দেহ পাওয়া যায়। কখনো সেই দেহে প্রাণ থাকে, কখনো থাকে না। কখনো কোনো দেহই পাওয়া যায় না। পাচার হয়ে যায়। আদুরী চোখ ধাঁধানো রূপসী। নবম শ্রেণিতে পড়ছিল। ওকে ইশকুলে যেতে হয়। পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হয়। নদী পেরুতে হয়। বনের পথে আসাযাওয়া করতে হয়। এ পথে ওকে বাঁচানো দায়।
আদুরীকে সুরাইয়া নেন। সুরাইয়ার মেয়ে সুরঞ্জিতা প্রথম মা হয়েছে। তারও ছোট্ট পুতুলের মতো একটা মেয়ে। সুরঞ্জিতার কাছে সার্বক্ষণিক থাকার জন্য একজন লোক দরকার। সুমাইয়া বিউটি পার্লারে তার পরিচিত বিউটিশিয়ান সূচনাকে বলেছিলেন কাজের জন্য ওদের সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে এনে দিতে। গারো মেয়েরা বিশ্বাসী। আদুরী সূচনার কাজিন। সময় ও সুযোগমতো আদুরীকেও সূচনা পার্লারের কাজে লাগিয়ে দেবে। আপাতত থাকুক সুরাইয়ার কাছে। সুরাইয়া কতদিন চুপচাপ থাকে। কঠিন মুখ। বাবার সাথে ফোনে ঝগড়া করে, তর্ক করে, কাঁদে। আদুরী লেখাপড়াটা জারি রাখতে চেয়েছিল। আইন পড়ার ইচ্ছে ছিল তার। বাবা তার ইচ্ছের গোড়ায় কুড়াল মেরেছেন। সুরাইয়া বলেন আমি তোকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়াব। ভাবিস না। আদুরী খানিকটা শান্ত হয়।
আদুরীকে দিয়ে একটু বেশিই সুবিধা হয়। ও পড়ালেখায় ভালো। সুরাইয়ার শ্বশুরকে আদুরী সুন্দর উচ্চারণে ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ে শোনায়। তিনি বলেন, তুই তো নিউজ প্রেজেন্টার হতে পারবি! সুরাইয়ার স্বামী নজরুল ইসলামের বুকশেলফগুলোতে বহুদিনের এলোমেলো বইপুস্তকগুলো বিষয় মিলিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। ক্যাটালগ তৈরি করে। নজরুল বলেন, বাহ তুমি তো লাইব্রেরি সাইন্স পড়তে পারবে! আদুরী কম্পিউটারে বসে ঘরের লোকজনের প্রয়োজনীয় নোটটোট রিপোর্টটিপোর্টও লিখে দিতে থাকে। দোকান, মার্কেট, ব্যাংক, হাসপাতাল সবজায়গায় গিয়ে আদুরীই কাজ সেরে আসে। ওর পড়াটার কথা কেউ মনে রাখে না।
সুরঞ্জিতার বর আরশান আদুরীকে বলে তুমি তো বিউটি কনটেস্ট জিতে আসতে পারবে! জাস্ট এই ভেজামুখ ভেজা চুলের লুকে। আজকাল আদিবাসী মেয়েদের ফিজিক বদলে যাচ্ছে। তারা উঁচু হয়ে উঠছে!
আদুরী ভ্রুকূটি করে। তাই? আমি লেখাপড়ার কনটেস্ট করবো! সুরঞ্জিতা বাচ্চার ভেজা ন্যাপি আর ব্যবহৃত প্যাম্পার্সগুলো নাকমুখ কুঁচকে আদুরীর হাতে দিয়ে বলে, যাও, এগুলো ফেলে দিয়ে এসো।
আচ্ছা, আমি তোমাকে লিংক পাঠাবো। অ্যাপ্লাই করতে পারো। চাইলে যে কোনা হেল্প। আরশান ময়লার ব্যাগ হাতে বেরিয়ে-যাওয়া আদুরীর ছায়াটাকে অনুসরণ করে।
একদিন আদুরী কী কাজে বাইরে গিয়ে আর ফিরে এলো না। ফোন বন্ধ। নজরুল ইসলাম বললেন, আপদ বিদেয় হয়েছে, ভালো হয়েছে। ঐ আগুনের খাপরা মেয়েকে কাজে রাখা যায় নাকি? একটা জিডি করে রাখলেই হবে। দুদিন পরে আরশান বাসায় আসে। তরল গলায় বলে, আরে ঐ মেয়ের নিশ্চয়ই সমস্যা ছিল। কোথায় কার সাথে গেছে কে জানে। জিডিটিডি করে রাখলেই হবে।
সুরঞ্জিতা আরশানের হাতে বাচ্চার বদলানো প্যাম্পার্সগুলো দিয়ে নাকমুখ কুঁচকে বলে, যাও, এগুলো ফেলে দিয়ে এসো।
একদিন গল্পের হাত ধরে রাস্তায় নেমে গিয়েছিলাম
পাঠশালায় শ্লেট-পেন্সিলে লেখার মতো করে আমি প্রথমে মনের শ্লেটে গল্প লিখতাম। লিখে মুছে ফেলতাম। যেসব লেখা মনের শ্লেটে সুন্দর সাদা দাগ হয়ে ফুটে উঠতো সেগুলোর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখতাম। মনে মনে এই গল্প লেখা খেলা চলতো আমার অতি শৈশবে। আমার আম্মা খুব গল্প করতেন। আমাদের পূর্বপুরুষের গল্প, নিজের শৈশব কৈশোর যৌবনের গল্প, আমাদের ভাইবোনদের জন্মের গল্প, অজস্র ঘটনা আর স্মৃতির গল্প। আম্মার কথাগুলো ছিল সব ওরাল গল্প। নিটোল আর নান্দনিক। বিভোর হয়ে শুনতাম আম্মার গল্প বলা। তিনি গল্পকে নতুন করে তৈরি করতেন। নানা ঘটনার খাপছাড়া কথাগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতেন। তাতে একটা শুরু থাকতো তারপর সেই শুরুটা পরিণতির দিকে বয়ে যেতো। ঘটনার ফাঁকফোঁকর, অজানা অংশও আম্মা সব চমৎকার করে ভরে দিতেন। আম্মার কথা বলাই আমাকে গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। গল্পের নির্মাণকৌশলটিও আমি আম্মার কাছেই শিখেছি।
আমার আম্মা অনেক বই পড়তেন। বিস্তর বই ছিল তাঁর ভাণ্ডারে। সংসারের কাজের ফাঁকে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে অথবা দু পা মেলে তার ওপর আমাদের ছোট ভাইবোনকে রেখে দোলা দিতে দিতে আম্মা গুন গুন করে বই পড়তেন। একটু বড় হয়ে আমি আম্মার পড়তে থাকা বই চুরি করে নিজে পড়ে নিয়েছি। পরে ভাণ্ডারের সব বই পড়ে ফেলেছিলাম। কৈশোর না পেরুতেই আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, জরাসন্ধ, বনফুল, ধীরাজ ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের এমনি বিখ্যাত লেখকদের অনেক বই পড়েছি! বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য সুন্দর গম্ভীর সব সমাসবদ্ধ শব্দ, শরৎচন্দ্রের কাহিনির সহজ বর্ণনা, এসব খুব ভালো লাগতো। স্কুলে আমরা বান্ধবীরা কাড়াকাড়ি করে পড়তাম নীহাররঞ্জন গুপ্ত আর নিমাই ভট্টাচার্য। নীহাররঞ্জন গুপ্তের রোমান্টিক কাব্যিক বর্ণনা ঐ বয়সে খুব ভালো লাগতো। কীভাবে নায়িকার মুখের ওপর শেষ বেলার আলো এসে পড়ে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কোঁকড়া চুলের রাশি নেমে আসে, পায়ের পাতার ওপর বিছিয়ে থাকে বঙ্কিম শাড়ির পাড় – এসব বর্ণনা খুব আকর্ষণ করতো। নাইনে থাকতে আমি এই আদলে একটা উপন্যাসও শুরু করেছিলাম। নায়িকার নাম বাসন্তী। মাতৃহীন। অন্যের বাড়িতে যে আশ্রিত ও নিগৃহীত। পুরো নাম ধরে কেউ ডাকে না। বলে বাসি। বাসি মানে পুরোনো। আবেগময় রোমান্টিক ভাষায় কয়েক অধ্যায় লিখেও ছিলাম। পরে সেটি হারিয়ে গেছে। আর আমিও বড় হতে হতে নিজের ভাষা নির্মাণ করে নিয়েছি। তারপরেও আমাদের লেখার শেকড়ে জলসিঞ্চন করেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম মানিক বিভূতি তারাশংকর সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আরও কত জন!
আমি প্রথম লিখতে শুরু করি আমার স্কুল জীবনে। তখন আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। আমার আব্বা রাফ খাতা হিসেবে নীল মলাটে বাঁধানো একটা বড় মোটা খাতা এনে দিয়েছিলেন। আমি সেই খাতাকে বানালাম আমার লেখার খাতা। সেখানে লিখে রাখতাম অনেক ছড়া, কবিতা, গান, গল্প, কাব্যগল্প। সেসব লেখা তো আর কোথাও ছাপা হতো না, তবে সেগুলোর রস আস্বাদন করতাম নিজেরাই। আমার পিঠেপিঠি বোনেরা আমার লেখা গল্প কবিতা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলত। আমার লেখা গানে আমিই সুর দিয়ে গাইতাম। ক্রমশ লেখার পরিমাণ বাড়তে লাগলো, কিন্তু কোথায় কিভাবে লেখা প্রকাশ করতে হয় জানতাম না। সেটি জানলাম বিয়ের পর। ক্লাস টেনে পড়াকালীন ১৯৭৩ সনে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে আমি স্থায়ীভাবে ঢাকা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি মানিকগঞ্জে চলে গেলাম। মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৭৭/৭৮ সাল থেকে আমার লেখা সেখানকার আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। আমার ‘লেখালিখির প্রতিভা’ আবিষ্কার করেছিলেন দেবেন্দ্রে কলেজে আমার শিক্ষক সৈকত আসগর। তিনি আমাকে সবসময় লেখার উৎসাহ দিতেন। আমার কাছ থেকে গল্প কবিতা ছাড়াও নানারকম লেখা চেয়ে নিতেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেসব তিনি পাঠাতেন। এভাবে আমার লেখা ছাপা হতে লাগলো। জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বড় পুরস্কারও পেয়েছিলাম আমার সেই মহান শিক্ষকের সহায়তায়। তিনিই, ১৯৮০ সনে, আমার কাছ থেকে একটি গল্প নিয়ে বাংলাদেশ পরিষদ আয়োজিত একুশের সাহিত্য প্র্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার গল্পটি জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তখন আমাকে কেউ চেনে না। আমি একজন অনামা পল্লীবধূ। থাকি মানিকগঞ্জের একটি গ্রামে, পশ্চিম দাশরায়, আমার শ্বশুর বাড়িতে। আমার ছেলের বয়স তখন সাড়ে চার বছর। আমি ননদ দেবরদের সাথে কলেজে যাই, বাড়ি ফিরে এসে রান্নাবান্না করি, শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী সন্তানের দেখাশোনা করি। সব কাজ শেষ হলে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন আমি হারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে, চিমনিটাকে বই খাতার আড়াল করে লিখতাম।
১৯৮২ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হই। সেসময় থেকে আমার লেখা জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে। তখন দৈনিক বাংলার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন আহসান হাবীব, তাঁর কাছে আমি লেখা পাঠাতাম ডাকে কিংবা লোক মারফত। তিনি আমার লেখা ছাপতেন আমাকে না দেখেই। তিনি মনে করতেন ঝর্না রহমান ছদ্মনামে কোনো পুরুষ লেখক এসব গল্প লেখে। পরে তাঁর সহকারী সম্পাদক নাসির আহমেদ আমাকে চিঠি লেখেন এই বলে যে, আপনি হাবীব ভাইয়ের সাথে দেখা করেন। তারপর আমি একদিন তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করি। আমার লেখক জীবনের অন্যতম প্রেরণা এবং পথপ্রদর্শক হলেন আহসান হাবীব। আশির দশকে দৈনিক বাংলা, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক দেশ, সচিত্র সন্ধানী, সচিত্র স্বদেশ, উত্তরাধিকার, ভারত বিচিত্রাসহ নানা বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় আমার অনেক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে, যা আমাকে উদীয়মান গল্পকার হিসেবে বোদ্ধামহলে পরিচিত করে তোলে।
১৯৮৫ সনে আমার প্র্রথম গল্পের বই ‘কালঠুঁটি চিল’ প্রকাশিত হয় খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি থেকে।