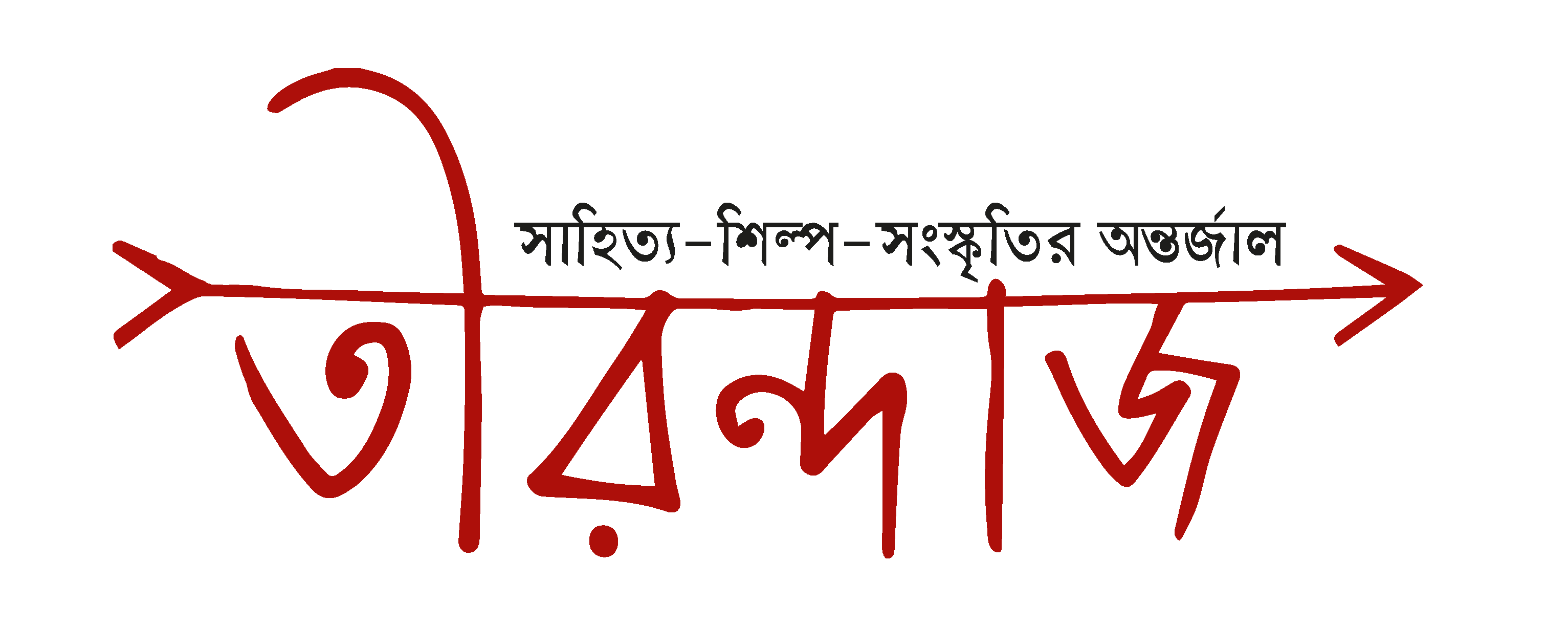যেখানে যাই, যত কাজই থাকুক, সব ফেলে আমি গিলতে থাকি চারপাশের মানুষজন আর ঘটনাপ্রবাহ। কে কী করছে, কী ঘটছে কোথায়, দেখতে থাকি হা করে। ছোটবেলায়ও তা-ই করতাম, বাজারে ঘাটে পথে মাঠে কাজে গিয়ে কাজ ভুলে মেতে থাকতাম এই হা করে চারপাশ গেলার কাজে। মা-চাচিরা তাই আমাকে ‘হা-করা’ বলত। খুব একটা ভালো তকমা এটা না, তবু হা করেই গিলতাম সবকিছু। কোথাও নতুন কিছু ঘটতে দেখা আমার পছন্দের কাজ, নতুন নতুন গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে গানের সুরে ভেসে যেতে। এই কারণেই হয়তো, নিজস্ব একজন গল্পপরি ছিল আমার, ছিল একটা গানের পাখি। আমার দাদি এবং নানি।
ছিলেন পুরোপুরি দুই তরিকার মানুষ, তবে তাদের মিলও ছিল বেশ।
নানি হাওয়া বিবি, মোড়ল বাড়ির বউ, ছোটখাটো মানুষ, বিড়বিড় করে হাঁটেন মেপে মেপে, চিড়বিড়িয়ে কথা বলেন দাঁতচেপে, গাম্ভীর্যের শেষ নেই। দাদি সাহেবজান বেগম, শেখবাড়ির বউ, লম্বা চওড়া মানুষ, দশটা দিকে তরতরিয়ে চলেন, গমগমিয়ে কথা বলেন প্রাণখুলে, কথায় কথায় রস। নানি থাকতেন বাড়িতে, ছেলে, ছেলের বউ এবং পোতা-পুতনিদের নিয়ে, দাদি থাকতেন মেয়ের বাড়ি (মেজোফুপু সরকারি চাকরি করতেন, ঘরসংসার দেখার মতো বিশ্বস্ত কেউ নেই তাই মা’কে নিয়ে রাখতেন কাছে) নাতিদুটো নিয়েই ছিল ব্যস্ততা তার। নানি দেখি মন্ত্রপাঠের নিষ্ঠায় মাসুম জাকির লাকি লাকি করেন; দাদির মুখে সোহাগ শাওন আর শাওন সোহাগ জিকির। দুইখানেই আমি অমুখ্য গৌণ, তাই মন খারাপ হয়। আপসোস হয়, আহা, নানি যদি আমার দাদিজানের মতোই তার নাতিকে নিয়ে মেতে থাকতেন, তাহলে কতই-না ভালো হতো! কতই না সুখের আর মধুর আর আনন্দের হতো দাদিও যদি আমার নানিজানের মতোন তার পোতাছেলেকে নিয়েই কাটিয়ে দিতেন বেলা!
তা তো আর হয় না, দু’জন দুই মেরুর মানুষ, তাদের দেখা-সাক্ষাৎও কমই হয়, তবু তো হয়, একজন কেন আরেকজনকে দেখে শেখে না! শিখলে আর সে-মতো চললেই তো আমি নিত্যদিনের আঁচল পাই প্রশ্রয়ের, আকাশ পাই গল্পের, আর সমুদ্র পাই আদরের। কিন্তু না, তারা তাদের মতোই চলেন। অবরে-সবরে আমি যদি যাই তাদের কাছে, কিংবা তারা যদি ছাড়া পান নাতি-পোতার কাছ থেকে তো আসেন আমাদের দেখতে, তখনই সুযোগ, পুষিয়ে নিতে চাই ঘন দূরত্বের ভার।
পান খেতেন দুজনেই, পানের রসের চেয়েও ঘন আর গভীর স্বাদের গল্প বলতেন।
দাদির কাছে ছিল তার পুরোনো জমিজিরেতের ঢোল, কে কী করত না করত তার ফিরিস্তি, আর দাদার রেখে যাওয়া গানগল্প। গল্প শুনতে চাইলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেসবই বলতেন, তবে আমি শুনতে চাইতাম রূপকথা। বিশেষ করে ভোলা নামের একটা ছেলের যে গল্প তিনি বলেছিলেন, সেটাই কেন জানি না শুনতে ইচ্ছে করে বারবার।
ভীষণ এক ঝড়ের রাতে আমার যখন ভয় করছে খুব, মা-আব্বা গেছেন ডাক্তার দেখাতে, ছোট্ট আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে গল্পটা বলেছিলেন দাদি। ভোলা ছিল আমারই মতো, তবে বুদ্ধি নাকি কম। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কোনো কাজই সে ঠিকমতো করতে পারে না। পড়াশোনায় ফেল মারে বলে মাস্টারের কাছে মার খায় আর মা-বাপের কাছে ঝাড়ি। এই নিয়ে তার দুঃখ ছিল খুব, সেই দুঃখেই একদিন সে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। সেই পথে বহু কষ্ট করে এক মুমূর্ষু দাদুর তৃষ্ণা মেটালো ভোলা। খানিকটা যেন তাতে প্রাণ পেল লোকটা, আর খুশি হয়ে একটা পুরোনো কলম দিলো ভোলাকে। বলল, বাড়ি ফিরে যাও। রাগ না করে কাজ করো, ফল পাবে। বাব্বাহ, লোকটা কী করে জানল যে রাগ করে বাড়ি ছেড়েছে ভোলা? যাহোক, সে ফিরে এলো বাড়ি, আর কলম দিয়ে লিখতে গিয়েই উঠল চমকে। দেখতে পুরোনো হলেও তাতে মুক্তোর মতো সুন্দর হয় হাতের লেখা, আর ভুল লিখলেও ঠিকটাই লেখা হয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা, কালি তার শেষ হয় না কখনো। সেই কলমে লিখে-লিখেই ভোলা হয়ে উঠল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র। শুনি আর প্রার্থনা করি, অমন একটা কলম যেন আমিও পাই, সারাবছর যতই খেলি আর যতই না পড়ি, অমন কোনো কলমের জোরেই যেন ভালো করতে পারি পরীক্ষায়।
তা যেমন হতো না, তেমনই হতো না চাইলেই দাদির কাছে গল্প শোনা। গল্পের চেয়ে দাদির দেখতাম গান শোনানোর আগ্রহ বেশি। গান শুনলেই যে আমার মন গলে যায়, কান ভরে যায়, আর তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তা হয়তো বুঝে ফেলেছিলেন। কোনোমতে একআধটা গল্প শেষ হতেই বলতেন, ‘আচ্চা, বাদ দে দিনি, এইসব পুরোনো দিনির বানানো চুরানো গল্প শুনে কী লাব! তারচে চল তোর দাদার গাওয়া গান শুনোই।’ তখন শুরু হতো সুরেলা সময়।
‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।’
‘সময় গেলে সাধন হবে না।’ ‘জাত গেল জাত গেল বলে।’ ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।’
‘বাড়ির পাশে আরশিনগর, সেথা পড়শি বসত করে।’
বাইরে তখন হয়তো জোছনা আর আঁধারের জড়াপিষ্টি, কিংবা বৃষ্টির রাত জলে-জঙ্গলে সুমসাম দুনিয়া, অথবা জোছনাও না বৃষ্টিও না জোনাকির দল রেশমি আলোর সুঁই দিয়ে সেলাই করে চলেছে রাতের কাপড়, আর ভেতরে আমি ভেসে চলেছি দাদির বয়সী গলায় ঢেউয়ের মতো একটু ওঠা একটু নামা একটু চলা একটু থামা সুরের তালে। সত্যিই একটা দুলুনি দুলুনি ভাব আসে দাদির গান শুনে, আর দুলতে দুলতে আমি ভেসে যাই দূরে যেখানে বাঁওড় বিল আর খালের পানি একাকার, যেখানে মাঠের ওপারে আন্দোলপোঁতা গ্রাম আর গ্রামটার ওপাশেই নেমে এসেছে আকাশ, লুকোচুরি খেলবে বলে। ভাসতে থাকি, আর ভাবতে থাকি দাদির মতো করে কি আর কেউ অমন দরদ দিয়ে আরশিনগরের পড়শি কিংবা অচিন পাখির আসা-যাওয়ার দোলাচলে দোলাতে পারে? কত যে ভাবি ওই পাখির কথা, আটকুঠুরি নয় দরজা আঁটা খাঁচাটাই বা কেমন? সময় গেলে কীসের সাধন হবে না? জিজ্ঞেস করলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে রসিয়ে নাচিয়ে কী সব বুঝিয়ে দেয় দাদি, বুঝি আবার বুঝি না।
এমনই হাবুডুবু অবস্থা আমার হয় নানির বলা সুমিস্যের জবাব খুঁজতে গিয়ে।
কালিদাস একদিন এক নৌকোয় উটে বসলে নদী পার হবে বলে। তা উটে বসে আচে তো বসেই আচে, যাত্রী উটাও শেষ হয় না নৌকাও আর ছাড়ে না মাঝি। বিরক্ত চোখে কালিদাস তাকায় সবার দিকে। এ্যাকজন যাত্রী তার সঙ্গের নোকের কাচে জানতি চাচ্চে যে জমি কিনলি কিরাম জমি কিনা ভালো। আরেকজন বলচে সে গরু কিনতি যাচ্চে তা কিরাম গরু কেনবে বুজতি পারচে না। ওগেরই সাতে আরেকজন ছিল সে বলল ভালো এ্যাটটা মেয়ে পালি বিয়ে করতি পারতাম, তা ভালো মেয়ে যে কনে পাই…। আবার মাঝি নৌকো ছাড়চে না, তারও খানিকটে তাড়া দিয়া লাগে। কালিদাস পন্ডিত তাই এক লাইনি এ্যাটটা জবাব দিয়ে দেলে যার মদ্যি চারটে উত্তরই আছে। জবাবডা কি বলোদিনি, ভাই?
পরীক্ষার আগে বই মুখস্থ করে যাই তবু যেখানে উত্তর করতে পারি না সব, তাতে এই ধাঁধার উত্তর দেব কী করে? ভেবে মরি। আমার দুরবস্থা দেখে নানিই বলে দেন – “উঁচোর চেয়ে নিচু ভালো, কুঁচি ফ্যালে পা/ যার মা ভালো তার ছা ভালো, বা রে মাঝি বা।”
এমন এমন আরো বহু সুমিস্যে জানতেন নানি। তাই সুযোগ পেলেই এই সুমিস্যের আসর বসাতেন আমাদের সামনে।
“নেই বলে খাচ্ছো থাকলে কোথায় পেতে? কালিদাস পণ্ডিত কয় পথে যেতে যেতে।” বলো তো কী?
“জন্মে মুড়ি কর্মে খই, কচি বেলায় সাপ, কালিদাস পণ্ডিত কয় বাপরে বাপ।” কী?
“কালিদাস পণ্ডিতি কইলো এ্যাটটা ধাধা, এ্যাটটা হাজার তেতুল গাচে কয়ডা হাজার পাতা?”
“হাত নেই পা নেই পিট দিয়ে যায়, এ্যাটটা দুডো মানুষ পালি আস্ত গিলে খায়।”
মাথা চুলকাই, একটারও উত্তর দিতে পারি না আমরা। তখন সহজ করে ধরেন তিনি। বলেন, এ্যাটটা লোক তার ছেলেরে চাচার বাড়িত্তে এ্যাটটা জিনুস আনতি পাটায়ে বলচে, “দিলি আনবিনে, না দিলি আনবি।” বলোদিনি কী আনতি বলচে?
ভাগ্য ভালো, এটা আমার জানা ধাঁধা, বলে দিই যে সেটা হলো বাসোই (মই)। শুনে নানি খুশি হয়ে ওঠেন, বাবা, তুমার যে ভালোই বুদ্দি! সেই ভালো বুদ্ধির পরীক্ষায় তারপর আরো প্রশ্ন আসতে থাকে।
“ড্যালা বনে চ্যালা নাচে।” কী জিনুস সেডা? এটার উত্তর মাসুম ভাই দেয় – মই।
“বাগানতে বেরোলো এক হুমো, গা ভরা তার ডুমো ডুমো।” এটার উত্তর বলতে পারি আমি – কাঁঠাল।
“কালো কালো তেতিলে মাথা ক্যান ছেঁচিলে, আমি তো পড়ন্ত ঢিলে, তুমি ক্যান তলায় ছিলে?” শত ভেবেও এর উত্তর আমি বলতে পারি না। উল্টো তখন গল্পের বইয়ে পড়া একটা ধাঁধা ধরি নানিকে আমি।
“আঁখির মধ্যে পাখির বাসা জল কে দিলো মূলে/ চৌপায়ার ওপর নিপায়া উঠিলো দোপায়া তুলিলো ডালে।/ সমুদ্রে বাঘের পাও, ছাগল খাইলো সাতশ নাউ।” বলেন দিনি কিরাম করে হলো এসব? নানি তখন ডাহা কুপোকাৎ। এত এত সুমিস্যে বলতে পারে যে সে আমার মতো ছোট্ট একজনের বলা ধাঁধার উত্তর দিতে পারে না দেখে আহ্লাদে ফেঁপে উঠি যেন! আর বায়না ধরি – সুমিস্যের জবাব দিতে পারেনি যেহেতু, নানি তাহলে গল্প বলুক একটা।
দারুণ দারুণ সব গল্পও বলেন নানি। যত রাত পর্যন্ত হুঁশে থাকি বাচ্চারা, তত রাত পর্যন্ত গল্প চলে। বলতে বলতে ঘুমান তিনি, ঘুমের ভেতর তাঁর জড়িয়ে যায় কথা, গুলিয়ে যায় গল্পের সুতো। তখন হয়তো আমরাও ঘুমের ভেতর, তাই ধরতে পারতাম না যে এক গল্পের গরু ঢুকে পড়েছে অন্যগল্পের খোঁয়াড়ে, কিংবা এক কেচ্ছার বাঘ এসে খেয়ে ফেলছে আরেক কেচ্ছার হরিণ। তাই বাঘে-মহিষে এক ঘাটে খেয়ে ফেলত জল, এর নামে ও আর তার নামে সে হয়ে উঠত গল্পের নায়ক। যদিও মানুষের চেয়ে তার গল্পে অশরীরীদেরই আনাগোনা ছিল বেশি। এত বেশি ভূতপ্রেত আর জ্বীনপরীর সমাবেশ ছিল তাঁর কাছে, এখন মনে হয় তাদের ধরে এনে জড়ো করতে পারলে একটা নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন করা যেত। কিন্তু হায়, তাদের ধরে আনা তো পরের কথা, গল্পগুলোও পুরো মনে নেই এখন আর। মাঝে মাঝে একটুআধটু মনে পড়ে এখান থেকে ওখান থেকে, আর তার আগে পরের ঘটনা জানতে মন চায়, কিন্তু জানানোর মানুষ তো গল্প করতে করতেই গল্প হয়ে গেছেন বহু আগে।
তার আগেই অবশ্য দারুণ একটা স্মৃতি তিনি দিয়ে গেছেন আমাকে।
মামাতো ভাইয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না, তুলনায় আমি ভালো- পড়ি না-পড়ি, স্কুলে ঠিকই যাচ্ছি, আর হুড়মুড়িয়ে পারও হচ্ছি একের পর এক ক্লাস, আমার জন্য তাই গর্বের শেষ নেই নানির। এমন অবস্থায়, ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি তখন, মায়ের কাছে কবে যেন শুনেছেন যে আমার জ্যামিতি বক্স নেই, কিনে দেবে কিনে দেবে করছে আব্বা, কিন্তু দিতে পারছেন না। ততদিনে শয্যাশায়ী নানি, চলতে ফিরতে পারেন না। মাসে মাসে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হয় যশোরে, তবু আরোগ্য নেই, শরীর ভেঙে পড়েছে, পাটের আঁশের মতো মোলায়েম ঢিলাঢালা হয়ে গেছে হাতপায়ের চামড়া তার, কষ্টের ছায়া চোখেমুখে। এর মধ্যেও আমার জন্য ফকফকা হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কত কত বুদ্ধি পরামর্শ দেন, বড় হওয়ার রাস্তা দেখান। সেই বড় হওয়ার পথে একটা জ্যামিতি বক্স বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা সহ্য হলো না নানির। তাঁর একটা মাটির ব্যাংক ছিল, বৈশাখী মেলা থেকে এনে দিয়েছিল ছোট মামা। অভাবের সংসার, বহুবছর ধরে তাতে যখন যেমন তখন তেমন একটাকা দু’টাকা করে জমাতেন বাচ্চাদের মতো। সেই ব্যাংক একদিন তিনি ভেঙে ফেললেন, তারপর আঁজলা ভরে সেই টাকা পাঠিয়ে দিলেন মায়ের কাছে।
আর তার কিছুদিন পরই বুজে ফেললেন চোখদুটো একেবারে। দাদি অবশ্য তারও বহু বছর পর পর্যন্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কর্মক্ষমতা কমে গেলে তিনি চলে এসেছিলেন বাড়ি, ছিলেন মা-বাবার কাছে, ততদিনে আমি শহরে পড়ি, ফুফাতো ভাইও সেই শহরে থাকে, বাড়ি গেলে বা ফোনে দাদির সঙ্গে কথা হলে আগে সোহাগ ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেন, ওর কি শরীর ভালো, খাচ্ছে ঠিকমতো, পড়ছে কি না, কিংবা আসবার সময় তাকে নিয়ে এলাম না কেন। এই নিয়ে খেপাই দাদিকে খুব, “তুমার তো নাতছেলে পুতাছেলে সবই সুহাগ ভাই, আমি আর কিডা! না হলি তো এটটু আধটু আমারও খোজটোজ নিতে।” শোনেন, আর বিব্রত হাসিতে এড়াতে চান। তবু তার হুঁশ হয় না, পরেরবার কথা হতেই আবার সেই সোহাগের খবর আগে! ততদিনে আমি অবশ্য বুঝতে শিখেছি যে, যাকে কোলে-পিঠে করে বড় করল দাদি, তার প্রতি বেশি পক্ষপাত বেশি টান থাকাই স্বাভাবিক।
অস্বাভাবিক যা কিছু তা ঘটল একেবারে শেষ সময়ে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে, মা কল করল, দাদির এখন-তখন অবস্থা, আমি যেন তৎক্ষণাৎ বাড়ির দিকে রওনা দিই। একটা মিডটার্ম পরীক্ষা ছিল বিকেলে, শেষ করেই উঠে বসলাম বাসে। বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম পরের দিন দুপুরের পর। গিয়েই চমকে উঠবার জোগাড় – পাড়ার মানুষ জড়ো হয়েছে, আত্মীয় স্বজনেরও চলে এসেছে অনেকেই, এমনকি গোরখোদকেরা পর্যন্ত বসে আছেন ছোটঘরের বারান্দায়। “এই তো এসে গিয়েচে”, বলে কে যেন আমার হাত ধরে নিয়ে গেল দাদির কাছে, “বাবা, কত টান তুমার পতি, যাও, দ্যাকো, তুমার জন্যিই দমডা যায়নি এ্যাকোনো।”
বড়ঘরের বারান্দায় শুয়ে আছেন দাদি, আমারই খাটে। পাশে গিয়ে বসলাম। বড় আব্বা আমার হাতে একটা গ্লাস আর চা-চামচ ধরিয়ে দিলেন। “ন্যাও, পানি খাওয়াও।” পানি দিলাম দাদির মুখে, বন্ধ ঠোঁটের খাঁজ বেয়ে গড়িয়ে গেল তা। কানে যেন ঢুকে না যায়, সে জন্য তাড়াতাড়ি সেটুকু মুছে নিলাম জামার হাতায়। তারপর বসে থাকলাম সেখানেই, দাদির বাম হাতটা দু’হাতে ধরা। কবজিতে হাত দিয়ে ডাক্তার যেমন রক্তচাপ দেখে, রক্তের আনাগোনা খেয়াল রাখছি তেমন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই হাত আমাকে জানিয়ে দিলো দাদি আর নেই। তবু আমি বসে আছি, অমন অভিজ্ঞতা সেই প্রথম, নিঃসাড় বসে আছি, দাদির হাতটা ছাড়ছি না, যেন হাত না ছাড়লে সে থেকে যাবে, আর রাতেই ঘুমানোর সময় গেয়ে উঠবে, খাঁচার ভেতর অচিনপাখি কেমন আসে যায়…।
তবে পাখি ততক্ষণে চলে গেছে বুঝেই দাদির চোখদুটো একসময় বুজিয়ে দিলো বড়আব্বা। কান্নার রোল উঠল। এ ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল, সে তাকে জড়িয়ে ধরে দিলো সান্ত্বনা। এসবের মধ্যে দিশেহারা লাগে আমার, সোহাগ ভাইয়ের জন্য শাওনের জন্য পাগল আমার দাদি, অথচ আমার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলেন এই শেষ সময়ে!
এখন বুঝি ওটা নিছকই কাকতাল এক, কিন্তু তখনকার সময়ে এ ছিল শিহরণ জাগানিয়া কথা। আহারে, কতভাবেই না মানুষ প্রবোধ দেয় নিজেকে!
তা প্রবোধ হোক বা অন্যকিছু, দাদির কথা মনে উঠলে এই এত বছর পরও ওই মৃতুগন্ধী বিকেলের কথাটাই আমার মনে আসে সবার আগে। আর অবাক হই, মানুষটার মৃত্যুর সেই ঘোর কষ্টের সময়টায় আমিই তাঁর হাত ধরে ছিলাম! নানির বেলায় অবশ্য মনে ভাসে তার দেওয়া সেই জ্যামিতি বক্সের ছবি। দাদির বলা সেই গল্পের মতো কোনো কলম আমি পাইনি ঠিকই, কিন্তু নানির জীবনের শেষ সঞ্চয় দিয়ে কেনা জ্যামিতি বক্সটার জাদু নিশ্চয়ই জোর বাড়িয়েছিল মাথায়, নইলে সারাটা স্কুলজীবন ফাঁকি দিয়ে দিয়ে আমি ক্লাস নাইনে উঠবার পর থেকে হুট করেই ‘ভালো ছাত্র’ হয়ে উঠলাম কী করে!